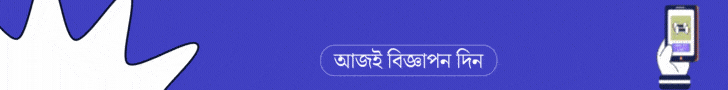এই পদ্মা, এই মেঘনা, এই যমুনা সুরমা নদী তটে
আমার রাখাল মন গান গেয়ে যায়
এ আমার দেশ, এ আমার প্রেম
আনন্দ বেদনায় মিলন বিরহ সংকটে
কত আনন্দ বেদনায় মিলন বিরহ সংকটে
এই মধুমতী ধানসিঁড়ি নদীর তীরে
নিজেকে হারিয়ে যেন পাই ফিরে ফিরে
এক নীল ঢেউ কবিতার প্রচ্ছদপটে
এই পদ্মা এই মেঘনা এই হাজার নদীর অববাহিকায়
এখানে রমণীগুলো নদীর মতো, নদীও নারীর মতো কথা কয়
এই অবারিত সবুজের প্রান্ত ছুয়ে নির্ভয় নীলাকাশ রয়েছে নুয়ে
যেন হৃদয়ের ভালোবাসা হৃদয়ে ফোটে
গানটির গীতিকার আবু জাফর। আবু জাফরের মনস্বী চৈতণ্যে অনেক সুরেলা ও অন্তবিলীন গান রচনা করেছেন, সুর করেছেন আর গাইছেন বিশিষ্ট শিল্পী ফরিদা পারভীন। এই গানের প্রতিটি চরণে চরণে নদী কামনা মদির ওষ্ঠে লেগে থাকা লিপস্টিকের সৌন্দর্য্যেশয্যায় জড়িয়ে আছে, গহীন গাঙ্গের আকুলতায়। ফরিদা পারভীনের গাওয়া এই গানের মধ্যে দিয়ে শ্বাশত বাংলার সকল নদীর গল্প প্রবহমান হয়ে উঠলেও কিন্তু আমি আমার নদীর গল্প লিখবো এই বেলায়।
আমার নদী, কচানদী। নদীর নাম কেনো কচা, জানি না। নানা গল্প বা উপাখ্যান ছড়িয়ে আছে কচা নামের, আমি সেদিকে যাবে না। আমার প্রসঙ্গ আমার নদী, যে নদী আমার কানে কানে কথা কয়, যে নদীর নারীর মতো আমার চেতনার সবুটুক জুড়ে প্রবমহান নিরন্তর! যে নদী আমার সকল প্রেরণার উৎস, যে নদী আমার স্বপ্নসুখের বাসর, যে নদীর স্রােত আমার নিবিড়ে জড়ায় আমারে…।
খুব শৈশবে, ক্লাস থ্রি বা ফোরে পড়ি। কচানদীর পাড়ে খোলা মাঠে আমরা এলাকার ছেলেরা ফুটবল খেলছি। খেলতে খলতে পানির পিপাসা লাগে। পানি পান করতে যাই, আমাদের সঙ্গে খেলছে হানিফ, ওদের বাড়ি। বাড়ি মানে টিনের চৌচালা ঘর, সামনে ছোট বারান্দা। ঘরটা এলোমেলো। উঠোনে ঝাকায় ইলিশ ধরার ছান্দিজাল মেলে দেয়া। একটা গাই গরু ঘরের সামনে বাঁধা। ঘরটার মধ্যে মাছের আঁশটে গন্ধ ভেসে আসছে। হানিফের বাবার কচানদীতে ইলিশ মাছ ধরার পেশা। ঘরের একেবারে বড় একটা নৌকা, লম্বা। নৌকার পাছার কাছে ছোট ছাউনি, পিছনে নৌকার হাল। ছাউনির পর লম্বা খোলা জায়গায় ইলিশ ধরার ছান্দিজাল রাখা। গলুয়ের দিকে তিনটে বা চারটে দাঁড়। দাড়িরা ঘন্টার পর ঘন্টা একটা ছন্দের তালে তালে দাঁড় বেয়ে নৌকা চালায়। তো, হানিফের মা বড় একটা এ্যালুমিনিয়ামের জগ ভরে পানি দেয়, সঙ্গে একটা গ্লাস। আমরা কয়েকজন পেট ভরে পানি খেয়ে আবার খেলতে নেমে যাই। খেলতে খেলতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কচানদীর স্রােতের জলের উপর পশ্চিমের আকাশে হেলে পড়া সূর্যের লালরঙ ছড়িয়ে দিয়েছে। আমরা বাড়ি যে যার বাড়ি ফিরে যাই। কচানদীর তীর থেকে আমাদের বাড়ি সোজা পূর্ব দিকে আধামাইলেরও বেশী।
অনেক রাতে মানুষের জাগর চিৎকার বা কোলাহলে ঘুম থেকে জাগি। বড়রা কোথায় চলে যায়, আমি ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে ঘুম থেকে জেগে মায়ের কাছে শুনি, হানিফদের ঘরবাড়ি নদীতে চলে গেছে। যদিও বয়স আমার কম, একেবারে নদীতীরের মানুষ না হলেও, জন্ম থেকে নদী দেখে আসিছ। দেখছি, আমাদের গ্রামের দুটি খাল, বোথলার খাল আর বায়োনের খালে শত শত মানুষের কচানদীতে ইলিশ মাছ ধরে জীবিকা অর্জনের সংগ্রামী কালাকাল। নদীর তীরে যেতাম ফালগুন মাসে কলাইয়ের শাক তুলতে। নদী তো আকছার ভাঙ্গছে, দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সেই ভাঙ্গনের রূপটা কতো ভয়ংকর, দেখলাম সেই সকালে।
দৌড়ে হানিফদের বাড়ি যাই। হানিফদের বাড়ি একেবারে ছিল নদীর পারে। কারণ, ওদের বাড়ি গত কয়েক বছরে আরও দুইবার ভেঙ্গেছে, নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে সব। ওরা ছিল সব হারিয়ে সর্বহারা। হানিফদের কোথাও যাবার জায়গা ছিল না, তাই একেবারে নদীঘেষে পরিত্যক্ত জমিতে ঘর তুলেছিলো অস্থায়ীভাবে। ওদের ঘর থেকে দুই আড়াইশো গজ দূরে ছিল বেড়িবাঁধ। আমি সেই বেড়িবাঁধের উপর দাঁড়িয়ে দেখি, এক রাত আগে যে ঘর থেকে পানি খেয়েছিলাম, সেই ঘর নেই। সেখানে বইছে ছল ছল কল কল কচানদীর ঘোলা জলের অবিশ্রান্ত স্রােত। হানিফদের ঘরের কোনোয় লম্বা একটা নারকেল গাছ ছিল, সেই গাছটা অর্ধেক গলা ডুবিয়ে প্রবল স্রােতের বিরুদ্ধে টিকে থাকার লড়াই করছে। আর হানিফ গভীর রাতে কচানদীর গ্রাস থেকে বেঁচে যাওয়া দুটি ছাগলের বাচ্চা নিয়ে বেরীবাঁধের উপর খেলছে।
নদী কীভাবে মানুষদের সর্বশান্ত করে, সেই শৈশবে দেখেছি কচানদীর কাছ থেকে। সেই সময়ে জীবনের সর্বগ্রাসী রূপান্তর আমি দেখেছি কিন্তু সেই নদী একদিন আমার জীবনে সৃষ্টির পরম্পরা হয়ে আসবে, ভাবিনি। প্রকৃতপক্ষে জীবন অবাক সাঁতার। সাঁতার কাটতে কাটতে কখন কোথায় জীবন নোঙ্গর করবে, আগে থেকে নিদির্ষ্ট করা মুশকিল।
কচানদীর জন্ম বৃহত্তর বরিশালের পিরোজপুর জেলায়। পিরোজপুরের হুলারহাটের কাছে দুটি নদী-মধুমতী ও সন্ধ্যা নদীর যৌথ প্রবাহে যে নদৗটির জন্ম, সেই নদীটিই কচানদী, আমার কচানদী। বরিশালের সবচয়ে খরস্রােত ও গভীর নদী কচা। নদীর এইপারে দাঁড়িয়ে ওপারে তাকালে চোখে লাগে ধাধা, এতো চওড়া কচা। হুলারহাট হয়ে কচানদী ভানডারিয়া উপজেলার প্রান্ত ছুঁয়ে নদমুল্লা, পাড়েরহাট, ইন্দুরকানি, চরখালি, টগরা, দারুলহুদা, বোথলা, তেলিখালি, বালিপাড়া, জুনিয়া, পাঙ্গাসিয়া হয়ে পড়েছে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হবার আগে বলেশ্বর নদীতে। আরও জানা দরকার, কচানদীটি আর্ন্তজাতিক নদী। এই নদী দিয়ে ভারতে জাহাজে মালামাল চলাচল করে।
আমি যখন সিক্স বা সেভেনে বা অষ্টম শ্রেণীতে পড়তাম, স্কুলের বাঁধাধরা নিয়ম একমদই ভালো লাগতো না। ফলে, নিয়মিত স্কুল পালাতাম। না, কেবল হাই স্কুলে উঠেই নয়, ফোর ফাইভে পড়ার সময়েও স্কুল পালিয়েছি। স্কুল পালিয়ে স্কুলে যাবার পথে নানা বাড়ির কালু মামার গোয়ালঘরে লুকিয়ে থাকতাম। যেই দেখতাম পাশের বাড়ির বন্ধুরা বাড়ি আসছে, আমিও চলে আসতাম। গোয়ালঘরে লুকিয়ে থাকার পর্বটা শেষ হলো, যখন প্রাইমারী স্কুলের বিপরীত দিকে বোথলা হাই স্কুলে ভর্তি হলাম সিক্সে। ওদিকে আর মামা বাড়ি নেই। অগত্য বই খাতা নিয়ে আশ্রয় নিলাম কচানদীর পাড়ে।
বেরীবাঁধ থেকে নেমে কচানদীর পাড়ে ছিল কেয়ার ঝোপ। বোথলার খাল উঠে গেছে কচানদীর শরীর চিড়ে সোচা পূব দিকে। বোথলা খাল আর কচানদীর ত্রিমোহনায় কচাঝোপে বইখাতা নিয়ে বসে যেতাম। আমাকে কেউ দেখতে পেতো না। নদীর জেলেরা দেখতো কিন্ত কিছু বলার ছিল না ওদের। আমি কি দেখতাম? আমি দেখতাম কচানদীর ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ। নদীর বুকে জেলেদের মাছ ধরা। দেখতাম, কচুরীপানাদের ভেসে যাওয়া। অনেক সময় সেই কচুরীপানার সঙ্গে ভেসে যেতে মৃত গরু। মুত গরুর উপর ঝাঁকে ঝাঁকে বসতো কাক। আরও দেখতাম বিচিত্র ধরনের নৌকার চলাচল। টাপুরে নৌকা চলতো তীর ঘেষে। কারণ, ছোট আকারের ওই নৌকায় সওয়ারি বইতো মাঝিরা, এক এলাকা থেকে আর এক এলাকায়। আজ ভাবলে বিস্ময় জাগে, টাপুরে নৌকার মাঝিরা নৌকার পাছায় বসে, ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন এক নাগারে নৌকা বাইতেন। কেমন করে সম্ভব ছিল ধৈর্য আর নিখাত পরিশ্রমের দরিয়া পাড়ি দেয়া? নৌকর সওয়ারী নারী হলে ছইয়ের দুই মাথায় টানিয়ে দেয়া হতো শাড়ির ঝালর, কেউ যাতে দেখতে না পায় নৌকার চড়নধার নারীদের।
আরও ছিল সুন্দরবন থেকে আসা বড় বড় বাওয়ালী নৌকা। সেই নৌকায় বহন করা হতো গোলপাতা। সুন্দরবনের গোলপাতা অনেকটা নারকেল গাছের পাতার মতো। তবে এই পাতা টেকসই হওয়ায় অনেক গৃহস্থ এই পাতা ঘরের ছাওনি হিসেবে ব্যবহার করতো। যেসব নৌকায় গোলপাতা বহন করতো, সেই নৌকা ছিল অনেক বড়, পোয়াতী নারীর মতো বিশাল পেট। সেই পেট জুড়ে গোলপাতা ভরা থাকতো। আমি অবাক হয়ে দেখতাম, নৌকাটা গোলপাতায় এতোটা বোঝাই থাকতো, নদীর পানি ছুই ছুই, মনে হতো এখনই ডুবে যাবে। অবাক ঘটনা, একটা নৌকাও ডুবতে শুনিনি।
ঠিক একই কায়দায় কচানদীর বুক চিড়ে যেতো সুন্দরীকাঠে বোঝাই বিশাল বিশাল নৌকা। আর ওই সব নৌকার বড় সৌন্দর্য ছিল দিকবলয়ের নানা রঙের পাল। বিশাল বিশাল পাল পেটে বাতাস নিয়ে পানির বুকের উপর দিয়ে চলে যেতো ইন্দিরহাট,বানারীপাড়া, স্বরূপকাঠিনর দিকে।
কচানদীর পাড়ে কেয়াঝোপের আড়ালে বসে সবুজ ঘাসের উপর শুয়ে বসে কতোভাবেই না আমি নদীর স্রােত দেখেছি। আমাদের অঞ্চলের নদীর একটা অনন্য বৈশিষ্ট, নদীর জোয়ারভাটা। জোয়ারের সময় কোত্থেতে পানি এসে নদী খাল ভরে যায় আবার ভাটার সময়ে সেই পানি কোথায় যায়, প্রশ্ন আমার অনেক দিনের। প্রকৃতপক্ষে, সমুদ্র সংলগ্ন হওয়ায় এই জোয়ার ভাটার খেলা। কচাপর পারে কেয়ার আড়ালে বসে আমার একটা খেলা ছিল… আমিই দেখবো আগে।
আমি যেখানে বসতাম, সেখান থেকে চরখালীর ঠোডা বা মুখ দেখা যেতো ধু ধু। ওইদিক দিয়ে ঢাকা থেকে বড় বড় লঞ্চ স্টিমার আসে। আমার চোখ থাকতো ঠোডায় যে লঞ্চ আ জাহাজ আসবে, প্রথম দেখবো আমি। অনেক সময় তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা করতো, কোনো লঞ্চ বা জাহাজের দেখা নেই। আবার এমনও হয়েছে, দশ মিনিটে পাঁচটা লঞ্চ বা জাহাজ এসেছে। সেই লঞ্চ বা জাহাজ নদীর গভীরতার নিরিখে চলতো। চরখালির ঠোডা থেকে বের হয়ে জাহাজ সোজা যায় ইন্দুরকানি, কারণ চরখালির মোড়ে চর, সেই চর এগিয়ে ইন্দুরকানি পার হয়ে সোজা কচানদী পার হয়ে চলে আসে দারুলহুদা। দারুলহুদা, বোথলা, তেলিখালি, জুনিয়া পার হয়ে চলে যায় বঙ্গোপসাগরের দিকে, বলেশ্বর নদীতে।
মাঝে মধ্যে মনে হতো কচানদীর ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ আমার সঙ্গে কথা কয়…। বিশ্বাস করুন, কান পাতলে আমিও শুনতে পাই, কচানদীর ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ কথা কয়। আমার সঙ্গে তো বটেই ওদের নিজেদের মধ্যেও। নদীর এই বিচিত্র রূপ দেখতে দেখতে এক সময়ে শুনতে পেতাম বোথলা স্কুলের ছুটির ঘন্টা, টং ঠং টং টং টং….। আমিও বই খাতা হাতে নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটতাম। শৈশব থেকে কচানদী আমার প্রাণের গভীর গোপন বন্ধু।
মেট্রিক পরীক্ষা দিয়েঢাকায় চলে আসি ১৯৮২ সালে। নারিক জীবনের কোলাহলের মিছিলে একটু আশ্রয়, একটু ঠাঁইয়ের লড়াই শেষে দু’বছর পর গ্রামে যাই। বাড়ি পৌঁছেই চলে যাই কচানদীর তীরে। তখন প্রবল ভাটার টান। নদীর জল অনেক খানি নেমে গেছে। আমি নদীর জলে পা ডুবালাম, হাম মুখ ধুইলাম। এবং নদীর জল ও উপরের তীরের মধ্যেবর্তি জায়গা দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম খালি পায়ে। খুব ভালো লাগছিল। হঠাৎ এক জায়গায় চোখ আটকে যায়, দেখতে পেলাম পোড়া মাটির ঘের। চোখ আটকে যায়, নদীর এই তটে পোড়ামাটির ঘের কোত্থেকে এলো? দাঁড়িয়ে ভালোভাবে খেয়াল করলাম। গ্রাম বাংলার মানুষ বলেই খুব সহজেই বুঝলাম, পোড়া মাচির ঘের আসলে চুলোর মাটি।
আমার শরীর মন কেঁপে উঠলো। সেই চুলোর মাটির ঘেরের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ, তাকিয়ে দেখছিলাম কচানদীর প্রবল ভাটার স্রােত। প্রিয় নদী আমার, কতো কতো সংসার ভেঙ্গে চুরমার করে নির্বিকার বয়ে যাচ্ছে নিজের মতো! এই চুলোয় কাদের খাবার রান্না হয়েছিল? সেই সংসার, সেই ঘরের মানুষগুলো কোথায়? আমার বুকের মধ্যে তীব্র বেদনার বাঁশি হাহাকারে বাজলো, এবং এখনও বাজছে…। নদী ভাঙ্গে ভাঙ্গে আর ভাঙ্গে…। গড়েও কি কিছু?
আমাদের বাড়ির আলতাফ চাচা কচানদীতে ইলিশ মাছ ধরতে যেতেন। আমার খুব ইচ্ছে, একদিন চাচার সঙ্গে ইলিশ মাছ ধরতে বা দেখতে যাবো কচানদীতে। মা যেতে দেবেন না। অনেক বলে কয়ে আমি দুইবার গিয়েছিলাম কচানদীতে, ছান্দিজালের নৌকায়। তখন পড়তাম ক্লাস সেভেনে। মানুষ যে কি পরিমান শ্রম দিতে পারে, দেখেছি কচানদীর জলের উপর, ছান্দিজালের নৌকায় বসে।রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে নদীর স্রােতের বিপরীতে দাঁড় বেয়ে শরীরটাকে কালো আলকাতরায় রূপান্তরিত করে জেলেরা যে ইলিশ পায়, সেই ইলিশ বিক্রি করে নৌকার মহাজনকে দিয়ে কতোই আর সংসারে নিতে পারতো?
শৈশবে আমাদের একটা খেলা ছিল কচানদীর পারে, লঞ্চে বা জাহাজের দিকে ঢিল ছুড়ে মারা। খরস্রােতা নদীর প্রায় তীর ঘেষে লঞ্চ বা জাহাজ চলাচল করে, ফলে আমাদের ঢিল মারতে সুবিধা হতো। আবার এতোট্ওা কাছ থেকে নয়, যে ঢিল মারলে গিয়ে পড়বে। কিন্তু সেটা ছিল আমাদের খেলা। ত্রিশ পয়ত্রিশ বছরের স্মৃতির দিনরাত্রি পাড়ি দিয়ে মনে করতে পারছি না, আমাদের কারো ঢিল, কখনো কোনোদিন কোনো লঞ্চের ডেকে বা জাহাজের খোলে পরেছিল কি না!
কচানদীর তীরে ছুঁয়ে আমাদের বোথলা গ্রাম আর সোজা পশ্চিমে তেলিখালি গ্রাম। আমাদের এখানে নদী ভাঙ্গতো বেশুমার। তীব্র সোত। ফলে কখনো গোসল বা সাঁতার কাটার সুযোগ হয়নি বোথলার তীরে। সেই সুযোগটা পেয়েছি তেলিখালি। তেলিখালিতে আমার মেজো খালার বাড়ি। বাড়িটা ছিল নদী থেকে আড়াইশো তিনশো গজ দূরে। আমার খালাতো ভাই আনোয়ার দেলোয়ার নদীর তীরে পৌষ মাঘ মাসের ধান ওঠার ফুট তরমুজ খিরাই কাচামরিচ মিষ্টিআলুর আবাদ করতো। কচানদীর তীর ঘেষে প্রথমে থাকতো বেরীবাঁধ, সেই বাঁদের পরে খোলা জমিনে চাষ…। আমি হালও চষেছি… ভাইজানদের সঙ্গে।
সকালে ক্ষেতের ফুট বা ভাঙ্গরি, তরমুচ, মিষ্টি আলু কৃষকেরা তুলি স্তুপ করতো। নদীতে ছোট ছোট নৌকা নিয়ে ব্যাপারীরা কিনে দূরের কোনো হাটে বা গনজে নিয়ে যেতে। সকালের মিহি বাতাস… ফুট বা ভাঙ্গরি খাচ্ছি আর কচানদীর পারে হাটছি, এ ছিল সেই সময়ে আমার প্রিয় মৌসুম, প্রানান্তকর সুখ। আজ এতাদিন পরে পিছনে ফিরে তাকালে দেখতে পাই, সব শূন্য, কেবলই স্মৃতি। সবাই কালের চক্রে, জীবনের বায় দূরের দেশের সাম্পানে চড়ে ভিন্ন জীবনের স্রােতে ভেসে যায় আর সেই কচানদী পারের পার ভেঙ্গে উজানে নিয়ে গেছে, রেখে দিয়েছে পিয়াসী দীর্ঘশ্বাস।
কচানদীতে গোসল করছে খালাতো ভাইদের তেলিখালি অংশে। ওই অংশে, জুনিয়ার আগে চর পরতে থাকায় স্রােতের বেগ একটু কম ছিল। ফলে শীতের দিনে, দুপুরে কচানদীর পারে ওই এলাকার ছেলে বুড়ো নারী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে গোসল করতে আসতো। গোসলের সময়ে সাঁতার কাটারও সুযোগ ছিল, তবে বেশীদূর যেতাম না। আর মজা ছিল,কচানদীর তীর ঘেষে কোমর পানি সমান জায়গায় গাছের ডালপালা দিয়ে একটা ঝাউ রাখতো। আত আটদিন পরে জালের ঘের দিয়ে সেই ডালপালা তুললে নানা ধরনের মাছ পাওয়া যেতো। আমার খালাতো ভাইদের সেই ঘের ছিল, আমি আনোয়ার ভাইজান আর দেলোয়ার ভাইজানের সঙ্গে সেই ঘেরে মাছ ধরেছি। সলা চিংড়ি, বাইলা, টেংরা, পুটি… আরও কতো মাছ। দুপুরে বা রাতে কচানদীর সেই তাজামাছ দিয়ে ভাত খাওয়ার সুখ আর বিলাসেরন কোনো তুলনা হয়, এই শালার ঢাহা শহরের কোনো পাঁচতারা হোটেলের?
একাত্তরে, সেই অগ্নি উৎসবকালে কচানদীতে অনেক লাশ ভেসে যেতে দেখেছি। অনেক লাশ স্রােতের ঘূর্ণিপাকে একেবারে তীরে এসে লতাগুল্মের সঙ্গে বেঁধে থাকতো। ক্ষত বিক্ষত লাশ ঢেউয়ের দোলায় দুলছে। সেই পোড়াশৈশবকালে একটা ঘটনা জেনিছেলি, কচানদীর পাড়ে, এক মুরুব্বীর মুখে। কিন্তু তিনি কে ছিলেন, আমার মনে নেই। অনেকগুলো লাশ তীরেজলে ঘূর্ণিপাকে ঘুরছিল, আমরা তীরে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। একজন মুরুব্বী লগি দিয়ে ঠেলে ঠেলে লাশগুলো নদীর স্রােতের দিকে ঠেলে দিতেন। তিনি বলছিলেন, দ্যাহো আল্লার কি কুদরত! মাইয়া মাইনষের ইজ্জত আল্লায় রক্ষা করচে। যে লাশগুলান উপুর হইয়া আচে, হেরা মাইয়া মানুষ। মাইয়া মানুষের ইজ্জত উপুর কইরা আল্লায় ঢাইকা রাখচে। তখন খুব বিচলিত হয়েছিলাম, মহান আল্লাপাকের প্রতি এক ধরনের নিবেদন অনুভব করতাম। কিন্তু এখন যদি সেই সময় আসে, সেই মুরব্বীকে পাই, প্রশ্ন করতাম- পাকিস্তানী সৈন্যরা যখন ধর্ষণ করে বাংলার মেয়েদের নারীদের ফালা ফালা করছে, তখন আল্লাহর রহমত কোথায় থাকে? কাম সাইরা শত শত আর্মীর বিভৎস ধর্ষণহুকাংর সহ্য করে মৃতুর মিছিলে আসার পর, ইজ্জত রক্ষা করেছেন! তিনি আরও একটা কাজ করতেন, লাশগুলো কচানদীর স্রােতে ঠেলে দেয়ার আগে মোনাজাত করতেন, দীর্ঘ মোনাজাত।
শৈশবে কচানদদীর কাছে মজার স্মৃতি, মোয়া খাওয়া। শীতকালে আমাদের এলাকার লোকজন পাড়েরহাটে টাপুইরিয়া নৌকায় যেতো। শুরুতেই জানিয়েছি, কচানদীর পারে, কেয়া ঝোপের আড়ালে বসে, আমি যে ঠোডা দেখতাম, সেই ঠোডার কচানদীর প্রবল স্রােত পার হয়ে ওই পারে গেলেই পাড়েরহাট। পাড়েরহাট বিরাট বন্দর এলাকা। পাড়েরহাটের মোহনায় কচানদীতে বিশাল চর। সেই চরের উপর পা থেকে কোমড় পর্যন্ত পানি থাকতো। সেই পানিতে বড় বড় নৌকায় মহাজনেরা ধান কিনতো। শুপারীর দিনে শুপারী কিনতো। কচানদীর তীরবর্তী গ্রামের মানুষেরা ছোট ছোট নৌকায় করে বাড়ির ধান শুপরাী নিয়ে আসতো বিক্রির জন্য। সেটা ছিল পানির উপর নৌকার বাজার। আর এই বেচাবিক্রির মাঝে একদল লোক খুব ছোট নৌকায় টিনের কাতিতে করে মোয়া সাজিয়ে নিয়ে আসতো আর চিৎকার করতো, মোয়া… মোয়া…। এবং চাওয়ার আগেই আব্বা মোয়া কিনে দিতেন। অজস্র নৌকার ভীড়ে ধান শুপারীর বেচাকিনির মধ্যে কচানদীর জলে নৌকায় ভেসে ভেসেসেই মোয়া খাওয়া…
কচানদীর স্মৃতি, ঘটনা কখনো আমার জীবনে ফুরাবে না। আমার সকল লেখার উৎস কচানদীর ঢেউ, স্রােত…। এ পর্যন্ত দুইশত গল্পের মধ্যে তিনটি গল্প কচানদীকে কেন্দ্র করে লিখেছি। প্রথম গল্প, অনেক বছর আগে, প্রায় পনেরো বছর হবে, ‘কচানদীর অট্টহাসি’। দ্বিতীয় গল্প ‘খোয়াজখিজির’। এবং তৃতীয় গল্প ‘ইলিশের মাংস’। ‘ইলিশের মাংস’তো বইয়ের নাম, বইটি দুবছর আগে মাওলা ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত।
স্রােতের সর্বনাশায় কচানদীর পার ভাঙ্গে আর ভাঙ্গে অজস্র মানুষের ভিটা, সংসার…নদীর ভাঙ্গনে মুহুর্তের মধ্যে সব হারিয়ে মানুষ নির্বিকার সর্বহারায় পরিনত হয়। এই ভাঙ্গনের খেলায় খেলে যায় খেয়ালী একরোখা কচা, অবিরাম, নির্দয় ক্রোধে। কচানদী ভাঙ্গে,ভাঙ্গছে সংসার,ঘর বাড়ি, জায়গাজমি, স্কুলঘর, স্বপ্ন, সব সব বরবং সব…। থেকে যায় কেবল মন মাতানো স্মৃতি, বিরহ আর জলের সঙ্গে তরঙ্গের মিহি মৈথুন। মহাকালের তুলনায় ত্রিশ বা চল্লিশ বছর তেম কিছু নয়, বিন্দুর চেয়েও কম সীমানা। কিন্তু সেই ত্রিশ বা চল্লিশ বছরের মধ্যে জীবনের এমন সব রূপান্তর ঘটলো, পিছনে ফিরে বিস্ময় লাগে।
শৈশবে ঢাকা ছিল প্রান্তি প্রান্তের মানুষের কাছে, পরীদের কোকাব শহরের মতো হাজার হাজার মাইল দূরের এক কল্পনারাজ্য। যেখানে গাড়ি চড়ে, ঘোড়া চড়ে, রাজাবাদশারা থাকে। সেই ঢাকা শহরের সঙ্গে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষদের যোগাযোগের প্রথম মাধ্যম ছিল বেতারযন্ত্র, চিঠি আর লঞ্চ। গত শতকের সত্তর-আশি দশকের স্মৃতি জাগানিয়া রূপনারানের কূলের ঘটনা লিখছি, ঢাকা থেকে তিনটি লঞ্চ যেতো কচানদী হয়ে বাগেরহাট। আমার ধারনা, বাংলাদেশের নদীযাত্রায় যাত্রীলঞ্চের এতোবড় রুট আর ছিল না, নেই। ঢাকা থেকে বাগেরহাট যাত্রায় কতো ঘাট যে ধরতো তিনটি লঞ্চ…। লঞ্চ তিনটির নাম নাবিক, পূবালী আর সাতারু। তিনটি লঞ্চ দোতলা। ঢাকা থেকে অনেক অনেক ঘাট ধরে কচানদীতে প্রবেশ করার আগে হুলারহাট হয়ে ভানডারিয়া, চরখালী, দারুলহুদা, তেলিখালি হয়ে বলেশ্বর নদীতে পড়ে চলে যেতো তুষখালী…। আমাদের কাছে তিনটি লঞ্চ ছিল দেবদূতের ঠিকানা। যদিও ঢাকা আসবার কোনো সুযোগ ছিল না, ছিল না সম্ভাবনা, তবুও তেলিখালি স্কুলে পড়ার সময়ে, বা যখন কচার পাড়ে বসে থাকতাম তিনটির যে কোনো একটি লঞ্চ দেখে তাকিয়ে থাকতাম। মনে হতো দোতলা লঞ্চটি স্বপনের সওদাগর। আমাদের অঞ্চলের যাত্রীরা , যারা ঢাকায় আসতো. সকাল এগারটার বারোটা দিকে লঞ্চে উঠে দোতলার পাঠাতনে বিছনা বিছিয়ে বসে যেতো, সারা দিন, সারা রাত পার হয়ে পরের দিন সকালে ঢাকা সদরঘাটে পৌঁছতো। এখন সায়েদাবাদ থেকে সকালে বাসে উঠলে বেলা তিনটায় বাড়ি পৌছনো যায়। লঞ্চ এখনও চলে, শুনেছি সেই নাবিক সাতারু আর পূবালী আর নেই। হায় কচানদী আর স্মৃতির দেরাজ…।
আমি শৈশব থেকে ঝামেলপূর্ণ মানুষ। বোথলা স্কুলে পড়বার সময়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কি একটা ঝামেলা বাঁধে, প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে হাতে লেখা পোস্টার রাস্তায় রাস্তায় সাটাই। ফলে, আমার জন্য বাড়ির কাছের বোথলা হাই স্কুল বন্ধ হয়ে গেলো। বিকল্প হিসেবে আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় চার পাঁচ মাইল দূরের তেলিখালি স্কুলে ভর্তি হলাম অষ্টম শ্রেণীতে। স্কুলটার সঙ্গে বাজার, বাজারের পরই কচানদী, আর লঞ্চঘাট, লঞ্চঘাটের আশেপাশে কয়েকটি চায়ের দোকান। আমরা দলবেঁধে লঞ্চঘাটে আসি, জানি, কোন সময়ে কোন লঞ্চ আসবে। লঞ্চের সিঁড়ি লাগলে বিচিত্র ধরনের, অগনিত আকার ও প্রকারের যাত্রী নামে। সঙ্গে থাকে ব্যাগ, বিছনা। অনেক সময়ে দেখতাম মুরগী, ছাগলও কেউ কেউ কোলে নিয়ে নামছে। আমি ক্লাসে বসতাম জানালার কাছে। কারণ জানালা দিয়ে তাকালেই দেখি কচানদী, নদীর স্রােত, উজান-ভাটা, লঞ্চ, পাল তোলা নৌকা। স্কুলটা পশ্চিম পূর্ব মুখী লম্বা। কোনো অনুষ্ঠান হলে দুটি ক্লাশের মাঝের বেড়া খুলে ফেললেই বিরাট হলঘর। দুই বার বা তিন বার কোনো শিক্ষকের বিদায় অনুষ্ঠান বা অন্যকোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানের কোনো কিছুই মনে নেই। মনে আছে এক শ্যামাঙ্গী হালকা তনুর মেয়েকে। মেয়েটির নামও ভুলে গেছি। সবকিছুর শেষে মেয়েটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতো, আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন, আমার ব্যথার পূজার হয়নি সমাপন…। আমি বসে থাকতাম জানালায়, মেয়েটি গাইছে, আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন… আমি মেয়েটিকে দেখছি না, দেখছি জানালা দিয়ে কচানদীর …। মেয়েটির রচিত সুর, কচানদীর প্রাণ মিলেমিশে আমার পরাণের গহীনে মর্মে পশিয়া যায়। গানের অর্থ জানি না কিন্তু কোমল ক্ষিন তনুর মেয়েটির মোহন সুর আর কচানদীর স্রােত.. মনে হতো আমি স্কুলে নেই আমি মাটিতে নেই আমি অন্য কোথায়, নির্জনের গহীন বালুচরে…। জানি না সেই মেয়েটি কোথায়, তেলিখালি স্কুলটি অনেক আগেই হারিয়ে গেছে কচানদীর অথৈ পেটে. আমি জেগে আছি স্মৃতির বাসনকোসন নিয়ে ঢাকা শহরের নির্মম রাস্তায়।
এই মুহুর্তের বিস্ময়, আমার জীবনস্রােতের প্রধান অবলম্বন কচানদী সর্ম্পকে স্মৃতির বাজনা বাজাতে বাজাতে একটা উপন্যাসের আখ্যান ঘুঙুর পায়ে করোটির জলে নাচতে আরম্ভ করছে। রিভার বাংলা’র কাছে কৃতজ্ঞ, কচানদীর আখ্যান নিয়ে লিখতে লিখতে উপন্যাসের স্রােত বইছে প্রবলবেগে। নাম রেখেছি, ‘কচানদীর জলে ঘুঙুর বাজে’।
আরও পড়তে পারেন….
বুকের ভিতর একটা নদী ।। রাজু বিশ্বাস
আমার শৈশবের তুরাগ এখন অর্ধমৃত! ।। মোহাম্মাদ এজাজ
মহানন্দার ডাকে ।। হামিদ কায়সার
নদী আমায় ডাকে ।। কাইয়ুম চৌধুরী