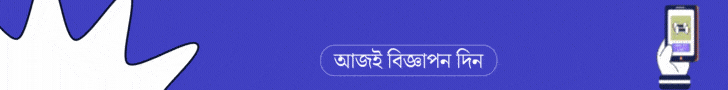মায়ের পরে খুব রাগ হচ্ছে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে কিন্তু ঘুমাতে পারছি না। মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে আছি তবু মনে হচ্ছে নৌকায় শোয়া আর একটা দোলা লাগছে।
মা, আমি ঘুমাতে পারছি না! ঢুল লাগছে।
মা এটাকে উপেক্ষা করছে। এবার চিৎকার করে কান্না জড়ানো সুরে জানালাম। মা তবু হাসছে-
ওরে পাগল, সারাদিন নৌকায় শুয়ে থেকে ঢুল লেগেছে। শুয়ে পড়, একটু পর ঠিক হয়ে যাবে।
টাবুরে করে মামাবাড়ি থেকে বাড়ি এসেছি। বিকালে একটু শুয়েছিলাম। আমাদের বাড়ি মোংলা পোর্ট থেকে পূর্ব দিকে তিন কি.মি. কাইনমারী গ্রামে। মামাবাড়ি একই জেলা বাগেরহাটের রামপাল থানার মালীডাঙ্গা গ্রাম। দূরত্ব ১৪ কি.মি. প্রায়। বাবা কখনও মামাবাড়ির ঘাটে টাবুরের ব্যবস্থা করে, কখনও পায়ে হেঁটে রামপাল এসে সেখান থেকে ওই টাবুরে বা ভাড়ার নৌকা করে বাড়ি আসি। এভাবে আমাদের যাতায়াত চলে। যে খরোস্রােতা দিয়ে দাঁড়-বৈঠার নৌকা বেয়ে আসা-যাওয়া তার নাম মোংলা নদী। নদীর নামেই দেশের দ্বিতীয় সমুদ্র বন্দর। আমার জন্মেরও অনেক আগে থেকে এই নদী আমাকে বয়ে এনেছে। আমি যখন মায়ের পেটে, বেশ কয়েকবার মা এই নদী পথে যাতায়াত করেছে বাড়ি-বাবারবাড়ি। আমার শরীরে রক্তনদীর মধ্যে তাই নিরবধি এর কুলুধ্বণি- কলকল ছলাৎছল।
নদী দেশকে বাসযোগ্য করে সভ্যতা এনেছে। বাণিজ্য বিস্তার করে লক্ষ্মীর শ্রীবৃদ্ধি, উদ্যান ও শস্যভূমির হরিৎছটায় রঙিন করে তুলেছে সুদূরে বিস্তৃত পল্লীর পট। মানুষের জীবনকেও সে রাঙিয়ে তোলে, ভবনার ভাস্কর্য হতে অনুপম অনুষঙ্গ হয়। নদীতে ঝাঁপ দিয়ে যে দূরন্ত শিশুর শৈশব অতিবাহিত হয়েছে, তার জীবনব্যাপী সেই সন্তরণ অনিশেষ। তার দুঃখ-বেদনায়, আনন্দে-গল্পে, স্মৃতিচারণায় মিশে থাকে নদীর কান্না, অশ্রুঝরার নীরব কলতান! সুদীর্ঘ না হলেও মোংলা বাগেরহাটের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদী। দৈর্ঘ্য ১৫ কি.মি. আর গড় প্রস্থ ২৪৫ মি.। বাগেরহাটের পশ্চিম দিক থেকে কয়েকটি খাল দক্ষিণে দুটি প্রধান ধারার সৃষ্টি করে।
বিশেষ করে কুমারখালি ও ফয়লা নদীর ধারা রামপালের পূর্ব দিকে প্রশস্ত হয়ে মোংলা নামে সর্পিল গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। এরপর সামান্য পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণে বাঁক নিয়ে মোংলা বন্দরের উপর দিয়ে পশুর নদীতে মিলিত হয়ে মিশেছে সাগরে। খুলনা-বরিশাল-ঢাকা নৌপথ সহজ করার জন্য মোংলা ও ঘষিয়াখালীর পানগুচি নদীর সংযোগ খাল কাটা হয়। এর ফলে মোংলা নদীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় বহুগুণে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ৭২ নং তালিকায় রয়েছে এই জোয়ার-ভাটার নদীটি। বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের কাছেও এটি প্রথম শ্রেণির নদী। পাহাড়ী নদীর মতো মোংলার কোন বিশেষ সৌন্দর্য নেই।
কিন্তু এক অদৃশ্য মোহ আর কীর্তি দিয়ে আমাকে জাদু করে রাখে ডলফিন বা সোস, কুমির, নদীর জলে মাছের মতো ডুবে থাকা সন্ন্যাসীর কাহিনিগুলো। যে নদীকে ঘিরে আমার পূর্বপুরুষের অসীম সাহসের ইতিহাস, সুন্দরবন কেটে বসতি নির্মাণের প্রবন্ধ জুড়ে আছে তার জন্য আর কী সৌন্দর্য লাগতে পারে! আমার বাবা অঘোরচন্দ্র রায় মজুমদারের ‘স্মৃতি সত্তার আলোয় মোংলা’ গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে মোংলা নদীসংশ্লিষ্ট সেই সব লৌকিক-অলৌকিক কাহিনিসকল। ব্রিটিশ আমলে মোংলা নদী প্রশস্ত ছিল না। পাকিস্তান আমলে সে যৌবন লাভ করে হয়ে ওঠে খরস্রোতা।

সম্ভবত, ১৯৬৬ সাল থেকে মনে পড়ে, অধিকাংশ সময় প্রতিবেশির নৌকায় বহর সাজাতো বাবা। নৌকা চালানোর জন্য হিসনে-দড়া, লগি, দাঁড়-বৈঠার সাথে তৈজসপত্র, গুড়ের কলস, তেলের ঠিলে, বাড়ির তুলোর বালিশ, আরও কত কী আয়োজন! কাইনমারী নৌকা যাবে, ফলে সেখানে আত্মীয়বাড়ি যাওয়ার কয়েকজন সঙ্গী জুটে যেত প্রায়ই। সোনার ভিটের পাশে খালে ছিল মালীডাঙ্গার ঘাট। সেখান থেকে দোয়ানির কূল, টেংরামারীর খাল বেয়ে বর্তমান খুলনা মোংলা রোডের বগুড়া ব্রিজের নিচ দিয়ে বগুড়ার খালে পড়ত নৌকা।
বগুড়ার খাল আসলে ছোট নদীর মতো। ওখান থেকে পূর্বদিকে দেখা যেত থানা রামপাল, মোংলা নদী। আর আমার ছোট্ট বুকের মধ্যে একটা দমধরা ভয় জমা হয়ে উঠত, যতক্ষণ না আবার নদী থেকে মোংলা শহরের খালে ঢুকত আমাদের ছোট নৌকাটি। ভয়টা বেশি হতো বড়দের কথা এবং আচরণে। মোংলা নদীতে পড়ে তারা গঙ্গাদেবীকে স্মরণ করতো, ছোট একটা কলসে জল ভরে নৌকার গুলুইয়ে রেখে দিত সাবধানে। আর আমাদের বার বার বলত, নড়াচড়া করিস না। আমি চুপ করে বসে দেখতাম এখানে সেখানে ভুস করে জলের উপর ভেসে উঠছে ডলফিন। সেগুলোর মুখ আর লেজ দেখা ছিল কঠিন। কেবল পিঠের অংশ দেখা যেত কিছুক্ষণ ধরে। বড়রা বলতো, মাছ তাড়া করেছে সোসগুলো।
‘পাড়ি ধরা’ কথাটা শুনলে ধক করে কেঁপে উঠতো বুকটা। বগুড়ার খাল থেকে মোংলা নদীতে পড়ে একটু পরে পাড়ি ধরতে হতো। নদীর বাঁকগুলোতে একপাশে বিপরীত স্রােত এবং প্রবল ঘূর্ণি তৈরি হয়। ভয়ংকর বেগে জল একটা গোঙানির শব্দে ঘুরপাক খেতে খেতে নিচের দিকে নামে। তার কেন্দ্রে বহুদিন গাছের গুঁড়ি, ডালপালা অনেক কিছু অসহায়ের মতো তলিয়ে যেতে দেখেছি। মনে হতো ওই ঘূর্ণিতে তৈরি হওয়া জলের গর্ত মৃত্যুদূত হয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকতো- এসো, আমার এই অন্ধকার ভয়ংকর রাজ্যে এসে দম বন্ধ হয়ে মরো! ঠিক পাশেই হয়তো উলটো নদীর গভীর তলদেশ থেকে বিশাল জলরাশি ফুলে উঠছে।
এমন স্থানে ছোট নৌকাগুলো জলের তোড়ে কোথায় গভীরে হারিয়ে যায় তা কোনদিন আর খুঁজে পাওয়া যায় না বলে কত গল্প ছড়িয়ে ছিল মানুষের মুখে। বেশি ভয় পেতাম নদীর এই বাঁকগুলোর ঘূর্ণিতে। ওদিকে তাকালে আমার গলা শুকিয়ে আসত। বাবার বইয়ে ছিল, এমন সব বাঁকে কুমির নাক ভাসিয়ে ভাসমান কাঠের মতো জলের স্রােতের সাথে থেকে শিকার ধরতো। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর ১৯৫০ সালে বন্দর স্থাপিত হলে যান্ত্রিক নৌযানের ভিড়ে কুমির সুন্দরবনের ভেতরে চলে গেছে কিন্তু তখনও কিছু ছিল এখানে ওখানে। ভাবতাম, একদিন ঠিকই দেখব, একটা কুমির ঘোলা জলে ভেসে আছে চোখ পাকিয়ে!
রামপাল বায়ে রেখে দক্ষিণে এগিয়ে গেলে পেড়িখালীর পর জয়খার বাঁক। ওখানে মাঝ নদীতে একটা ‘ভেবদি’ জাল পাতা থাকতো ভাটার সময়। তখন নদীতে প্রতি বাঁকে পাতা থাকতো এই জাল। ভয়ংকর স্রােতের মধ্যে কীভাবে সেই জাল পেতে একটা নৌকায় নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকতো জেলেরা তা মনে হয় আজও বুঝে উঠতে পারিনি। জাল বাঁধা থাকতো দুটো ‘পিপেয়’। বড় নোঙর ফেলে বিশাল খালি কালো ড্রামের মুখ বন্ধ করে তাতে বেঁধে রাখা হতো পিপে। বিশেষ করে আমাবস্যা-পূর্ণিমার স্রোত বেশি হলে পিপে ডুবে যেতো জলের টানে। দূর থেকে বোঝাই যেত না। ওটা ছিল আর একটা মরণ ফাঁদ। নৌকা ওই পিপের উপরে উঠলেই কাত হয়ে ডুবে যেত। একবার আমাদের নৌকাও এভাবে দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যায়। সেই থেকে নতুন শঙ্কায় পেয়ে বসল আমাকে। ডুবন্ত বা আধা ডুবন্ত পিপে!

জয়খার বাঁকটা দুঃস্বপ্নে এখনও আসে। মামাবাড়ি থেকে প্রথম ভাটায় যাত্রা করলেও সেখানে পৌঁছাতে দুতিন ঘণ্টা লেগে যেত। আর একটু দেরি করে বের হলে শেষ ভাটার দিকে জল অনেক নিচে নেমে গেলে জয়খা গ্রামের ভাঙন কূলটা মনে হতো পৃথিবীর অন্য কোনো বিচ্ছিন্ন প্রান্ত! রহস্য উপন্যাসে যেমন বিপজ্জনক গা ছমছম করা খাড়ি থাকে, ঠিক সেই রকম। খুব ঘন নারকেল-সুপারির গাছ আর বড় বড় টিনের বাড়ি ভেঙে পড়ছিল সেখানে। নৌকায় বসে মাথা উঁচু করে দেখতাম কিন্তু কিছুই বুঝতে পরতাম না সেসবের বাস্তবতা। কোন মানুষজন চোখে পড়ত না প্রায়শ, কদাচিৎ দুএকজনকে দূরে অস্পষ্ট দেখা গেলেও মনে হতো ছবি। এই বাঁকে এক সন্ন্যাসীকে জলের উপর আসনে বসার মতো দেখতে পেয়েছিল মালীডাঙ্গা গ্রামের চণ্ডী। তখন বসতি শুরু হয়নি এলাকায়। কিছু সাহসী মানুষ নৌকায় যাতায়াত করতো বিশেষ প্রয়োজনে।
‘একদিন চণ্ডী মালীডাঙ্গার বাড়ি থেকে নৌকায় নতুন বাড়ি বর্তমানে মোংলার ইপিজেড এলাকার উত্তরে ঝাউবুনের দিকে আসছে শেষ রাতে। জয়খাঁর বাঁকে এসে দেখতে পেলো, নদীতে জলের উপরে এক সন্ন্যাসী বসা। চণ্ডী জোরে নৌকা বেয়ে কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করতেই সন্ন্যাসী তলিয়ে যাওয়া শুরু করলো। চণ্ডী দূরে থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সন্ন্যাসীর ভাসমান লম্বা চুলের অগ্রভাগ ধরে ফেললো। তারপর সন্ন্যাসীর বাহু ধরে এক হাতে সাঁতরে কূলে নিয়ে গেল। তখন হঠাৎ তার মনে হল সে একটা পঁচাগলা লাশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। প্রচ- দুর্গন্ধ এবং হাতে পঁচা মাংসের ঘিনঘিনে অনুভূতির অবস্থায় চণ্ডী একটা ঘোরের মধ্যে ছেড়ে দিল সন্ন্যাসীকে। ছাড়া পেয়ে সন্ন্যাসী ডুবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানটা চন্দন ও পদ্মগন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। চণ্ডীর যে হাতখানায় সন্ন্যাসীর পচা বাহুর ক্লেদ মাখা বোধ হচ্ছিল সেই হাতখানা সুবাসে ভরপুর হয়ে গেছে। সে তখন হাউ হাউ করে কাঁদছে। তার কান্নায় সন্ন্যাসী কিছু দূরে জলের উপরে আবার ভেসে উঠে বললেন, ‘তুই কানছিস কেন? তোর সঙ্গে আর একদিন দেখা হবে, সেইদিন তোর আশা পূর্ণ করে শিখিয়ে দিয়ে যাব। আজ বাড়ি চলে যা।’ (স্মৃতি সত্তার আলোয় মোংলা)।
চণ্ডীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর আবার দেখা হয়েছিল পশুর নদীতে। জয়খার দক্ষিণ দিকে বাবা প্রতিবার আঙুল দিয়ে দেখাতো, ওখানে একটা কুমির রোদ পোহাচ্ছিল এক সময়। সেই কাহিনিও বাবা গ্রন্থে উল্লেখ করেছে।
‘ফয়লার পূর্ব দিকে সগুনা গ্রাম থেকে একবার দুই পাল মশাই প্রকাণ্ড নৌকা করে শীতকালে দোয়ালি বাসায় যাচ্ছিল ধান কেটে মাড়াই-ঝাড়াই করে আনতে। আনুমানিক ১৯০০ সালের ঘটনা। নৌকায় তিন মাসের দরকারি সব কিছু তুলে ভাটার সময় নৌকা ছেড়েছে ভোরবেলা। কুমির শীতকালে অনেক সময় ডাঙ্গায় উঠে নরম রোদ পোহায়। জয়খাঁ গ্রামের দক্ষিণে নির্জন নদীর পাড়ে পাঁচ-ছয় হাত লম্বা একটা বাচ্চা কুিমর নদীর পাড়ে উঠে রোদ পোহাচ্ছে। পাল মশাইরা কুমিরটাকে বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে চুপি চুপি কুমিরের কাছে এসে নৌকা আড় করে কূলে আটকে রেখে প্রকাণ্ড শব্দ করে ওঠে। কুমিরটা ঝিমুনি ভেঙ্গে নদীতে লাফিয়ে পড়তে গিয়ে কিনারে আটকে রাখা নৌকার মধ্যে পড়লো। তারপর চার পায়ে নৌকার এমাথা ওমাথা ছুটোছুটি করে চেষ্টা করলো নদীতে নামার। কুমিরের পায়ের আঘাতে নৌকার মালপত্র- তিনটে গুড়ের কলস, একটিন কেরোসিন, এক টিন সরিষার তেল, বিছানাপত্র, লেপ-কাঁথা, মাদুর, জ্বালানি, বস্তা বোঝাই চাল, থালা-গ্লাস, হাড়ি-কড়াই, ইত্যাদি সকল জিনিসপত্র ঢেলে, ভেঙ্গেচুরে, ছিঁড়েখুঁড়ে একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে খিচুড়ি তৈরি সারা। এভাবে লঙ্কাকা- করে অবশেষে নৌকা থেকে টপকে নদীতে পড়ে চলে গেল কুমিরটা। পাল মশাইরা নৌকার দুই মুড়িতে বসে মাথায় হাত দিয়ে কান্না জুড়ে দিল।’ (স্মৃতি সত্তার আলোয় মোংলা)।
জয়খার বাঁক পার হতেই দেখা দিত চাড়াখালীর বাঁক। আর নদীতে বাড়তো নৌকার সংখ্যা এবং ক্রমশ যন্ত্রচালিত নৌযান। ব্রিটিশ আমল থেকে পাকিস্তান পর্বেও চাড়াখালী একটা হাট ছিল। পাকিস্তান পর্যন্ত এখানেই ছিল বিশাল এলাকার একমাত্র ডাকঘর। খুলনা-বাগেরহাট, খুলনা-বরিশালগামী লঞ্চগুলোর একটা ঘাট ছিল এখানে। চাড়াখালী পার হলে মোংলা দেখা দিত। মোংলার কুমোরখালী খালের আগে নদীর মাঝখানে একটা পোড়া জাহাজ নোঙর করা ছিল মনে হয় আমার জন্মের ১৯৫৯ সালের আগে থেকে। স্বাধীনতার পর জাহাজটাকে অপসারণ করা হয়েছিল। সেই জাহাজটা ছিল আমার শিশুমনের বিস্ময় জাগানিয়া। সেটার বডি নির্মিত হয়েছিল রড-সিমেন্ট দিয়ে। তার উপরে অনেক কিছুর মধ্যে একটা পেঁপেগাছ জন্মেছিল। কারা যেন গোপনে ঘর বেঁধে বাস করতো সেখানে! কলাগাছও ছিল মনে হয়। জাহাজটার সামনে পেছনে নোঙর থাকায় জোয়ার-ভাটাতে ঘুরে যেত না। আমার কাছে ওটা একটা রহস্যদ্বীপের মতো ছিল। শুনেছিলাম, হিসাব মিলাতে না পেরে নাবিকরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল সেই জাহাজে।
আমরা বেশিভাগ সময় কুমোরখালী খাল দিয়ে, কখনও আরও সামনে মোংলা বন্দর পার হয়ে পশুর নদীতে পড়ে গোগের গোড়া দিয়ে কাইনমারী খালে ঢুকতাম বাড়ির ঘাটে পৌঁছাতে। ভয় পেয়ে জ্বর হওয়ার অভিজ্ঞতাও দিয়েছে এই নদী। একবার, বয়স তখন চার, ছোট নৌকায় মোংলা নদী দিয়ে মায়ের মামাবাড়ি কালেখারবেড় যাচ্ছি জ্ঞানদাদুর বাড়ি। চাড়াখালীর বাঁকে এলে দেখি জোড়া ‘গাধাবোট’ টেনে নিয়ে আসছে ইঞ্জিন বোটে। মাল টানা হয় বলেই হয়তো ওরকম নাম। তাতে পেছনে খুব তুফান আসছে। বাবা হালের কাছে বসা, আমি নৌকার মাঝখানে ‘ঘুরো’র পরে এক মহিলার পাশে। মনে মনে খুব ভয় পেয়ে বললাম, ‘আমি বাবার কাছে যাব।’ বাবা বুঝতে পারেনি! বললো, ওখানে বসে থাকো। তারপর ঢেউ এসে নৌকা যখন ভীষণ দুলে উঠল আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠি। রাতে জ্বর এলো, ১০৪ ডিগ্রি। পরিষ্কার মনে পড়ে, প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছিল কিন্তু চোখ বুজতে পারছিলাম না! চোখ বুজলেই যে কী ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন ঘিরে ধরেছিল তা বলে বোঝানো যাবে না!
একাত্তরের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান পর্বে শেষ নৌকাযাত্রা ছিল আমার এই নদীতে। যথারীতি মামাবাড়ি থেকে মালপত্র বোঝাই করে মোংলার বাড়িতে আসছি। প্রতিবেশিরা রয়েছেন কয়েকজন। নদীটা বেশ ফাঁকা লাগছে। আমরা চাড়াখালী পার হয়ে মাছমারার কাছে আসতেই পাকিস্তানি তিনটি নেভি পিএনএস বাবর, পিএনএস জাহাঙ্গীর এবং আর একটির নাম মনে পড়ছে না, রামপালের দিক থেকে মহড়া দিয়ে তীর বেগে মোংলার দিকে যাচ্ছে। জলপাই রঙের নেভিতে সাদা রঙে বিশাল অক্ষরে সেই নাম লেখা পড়লাম। প্রায় শেষ ভাটার সময়ও পেছনে দেখছি এত বিশাল তুফান যে, নদীর জল সব ডাঙ্গায় উঠে যাচ্ছে। যারা নৌকা চালাচ্ছিল তারা ভয়ে, আর বাবা আমার জন্য কান্নার মতো চিৎকার করে উঠলো। তারপর সবাই নৌকা খুব দ্রুত কূলের দিকে বেয়ে নিল। কিন্তু কূলে গিয়ে নৌকা চরে টেনে তোলার আগেই তুফান এসে ডুবিয়ে দিল আমাদের। মালপত্র ভেসে গেল। সবাই ভিজে চরের মধ্যে নৌকা ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। নেভি চলে গেলে কিছু পরে সন্তর্পণে নৌকার জল ফেলে আবার কীভাবে বাড়ি গিয়েছিলাম ঠিক মনে পড়ে না। আসলে সেদিন নদীতে নৌকা না চালাতে ঘোষণা দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কীভাবে জানব আমরা! তখন তো এত উপায় ছিল না!
বাংলাদেশে প্রথম রামপাল থেকে বাবার সঙ্গে মোংলায় এলাম একটা ইঞ্জিনের বোটে করে। মোংলায় বিদেশি জাহাজে নৌ-কমান্ডোদের মাইন বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত জাহাজের নাবিকদের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করেছিল মুক্তিযোদ্ধা অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং মহানন্দ বিশ্বাস। তাদের সেই বোটটি উপহার দিয়েছিল নাবিকরা। মোংলা নদীকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে নতুন করে যেন অপার বিস্ময়ে দেখছি। বোটে মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন। তারা একজন রাজাকারকে রামপাল থানায় হাজিরা দিতে নিয়ে এসেছিল। মোংলা নদীর মোহনায় পশুর নদীতে বাহাত্তরের এপ্রিলেও কয়েকটি জাহাজে দেখি আগুন জ্বলছে। স্বাধীন দেশে মোংলা নদীতে একটি বিদেশি বোটে একই সাথে মুক্তিযোদ্ধা এবং রাজাকার দর্শন ঘটে আমার! এটা কি প্রতিকী ছিল দেশের জন্যেও?
একাত্তরের পর আমার এই নদীযাত্রা দুঃস্বপ্ন থেকে ক্রমশ স্বপ্নে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। নদীর বিধ্বংসী রূপ কমে আসে; সম্ভবত এজন্য যে, আমার বেড়ে যায় বয়স। তখন বেশি করে শুরু হল গৃহস্থদের নৌকার পরিবর্তে টাবুরে করে যাতায়াত। মোংলা বন্দর থেকে পশুর নদীতে বাজুয়া, চালনা এমনকি খুলনা পর্যন্ত চলে টাবুরে। মোংলা দিয়ে প্রধানত রামপাল। এক সময় মামাবাড়ির কাছে ঝনঝনিয়া থেকে রামপাল পর্যন্ত রিকসা চলাচল শুরু হল। সে ভারি আনন্দময় এক বিস্ময়! রিকসা করে রামপাল এসে টাবুরে করে মোংলা, আয়েশী আর আমাদের জন্য রাজকীয় এক আয়োজন! কারণ হাঁটতে শেখার পর আমরা মোংলার কাইনমারী থেকে রামপালের মালীডাঙ্গা পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে চলেছি বেশিভাগ সময়। রামপাল খেয়াঘাট তখন ভাঙনকূল। খেয়াঘাটের পশ্চিমপাশে একটা বধ্যভূমি ছিল একাত্তরে। ঘাতক বৃদ্ধ আকিজ উদ্দিন কুড়াল দিয়ে কাঠ চেলা করার মতো কুপিয়ে কুপিয়ে মানুষের দেহ ফেড়ে ফেলত। অনেক সময় হাতবাঁধা অবস্থায় বধ্যভূমিতে আকিজ উদ্দিন ব্যঙ্গ করে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতো ‘বাবারে! মেহেরবানী করে তোর ঘাড়টা একটু কাঠখানার উপরে তুলে দে, যাতে এক কোপে কাটতে পারি। আমারও কষ্ট কম হয়।’ খেয়াঘাটে দোকানের বেঞ্চে টাবুরে বা লঞ্চের অপেক্ষায় বসে থেকে সেই বধ্যভূমিটা দেখতাম। কত অসহায় মানুষের দেহ-রক্ত, মৃত্যু-যন্ত্রণা মিশে আছে এই মোংলার জলে!
যাত্রীদের সুবিধার জন্য টাবুরে নৌকায় সুন্দর ছৈ ছিল। একজন মাঝি বা দাঁড়িসহ দুজন টাবুরে বেয়ে নিত একটা ছন্দের মতো। নৌকার গায়ে বৈঠা ঠেকিয়ে আড়ভাবে জল ঠেলে আবার সমান্তরালে জলের উপর না তুলে সামনে নিত বৈঠাখানা। এতে জলকাটার একটা সুন্দর শব্দ হতো। গল্পকরে, মাঝিদের সঙ্গে বৈঠা বেয়ে, ডলফিন দেখে একটা রোমাঞ্চকর সময় কেটে গিয়েছে সে সব যাত্রায়। ১৯৭৭ সালে সম্ভবত শেষ টাবুরেয় উঠেছিলাম। আমার তখন কৈশোর শেষ হচ্ছে। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি। মণিমামা বিয়ে করেছিল পাশের গ্রামে আমার সহপাঠীর দিদিকে। সেই মামিমা সুহাসিনী আমাকে ভীষণ ভালোবাসত। আমাকে বললো, আমি তোমার মামাবাড়ি যাব, আমাকে একটু পৌঁছে দিতে যাবে? স্কুল বাদ দিয়ে টাবুরে করে রামপাল গেলাম। সারাপথ মামিমা আমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল প্রেমিকার মতো। মাঝি সেই চেনা ছন্দে নৌকা বেয়েছিল। একটা ঠাণ্ডা বাতাস ছিল নদীর বুক জুড়ে।
সড়কপথের উন্নয়ন, খুলনা-মোংলা রোড় শুরু হলে ১৯৮০ সালের দিকে টাবুরে বন্ধ হয়ে গেল। আমি তখন খুলনায় কলেজে পড়ি। ভ্যান রিকসায় দিগরাজ হয়ে খুব সহজে মামাবাড়ি ভাগার কাছে মালীডাঙ্গায় যাই। বহু দিন নদীর আর খোঁজ রাখিনি।
মনের মধ্যে নদী তো ছিল! একদিন মাকে বললাম-
মা চলো না নৌকা করে সেই পথে আবার একদিন মামাবাড়ি যাই! দেখে আসি কেমন আছে সেই নদী, তার বাঁকগুলো!
মা খুব খুশি হয়ে ওঠে। বাবারবাড়ির চেনা পথ নারীদের হৃদয়কন্দরে কতটা গভীরে লালিত, কেউ কি তা জানি!
খোকা, খালের পাশে সেই ওড়াফুল, কেওড়া, গাছগুলো আছে?
কীকরে বলি, মাঠ-ঘাট নদীকূল সব শূন্য করে ফেলেছে বৃক্ষদস্যুরা। আমরা যখন খালের মধ্য দিয়ে আসতাম, দুপাশে ঘন বন ছিল ওড়া আর কেওড়া গাছের। জোয়ারের জলে আধাডোবা হয়ে থাকত। মায়ের খুব ইচ্ছে চলতি নৌকায় বসে যত বেশি সম্ভব ফুল সংগ্রহ। বাবা বিরক্ত হতো বিঘ্ন ঘটায়। কিন্তু আমরা দারুণ উৎসাহে ফুল তুলতে গিয়ে ডাল ধরে তাল সামলাতে না পেরে নৌকার মধ্যে পড়ে গিয়েছি। গায়ে আঁচড় লেগেছে ডালের, পাতার জলে ভিজে গেছে শরীর। গাছে আবার টিয়েবোড়া সবুজ সাপ থাকে। সে ভয়ও ছিল। সেই ফুল মা সন্ধ্যাবেলা বৃতি কেঁটে বসিয়ে দিত কাঁসার থালায়। ভোরে উঠে আগে ছুটতাম সেই মধু খেতে। ওড়াফুলের মধুর চেয়ে সুমিষ্ট পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। বৃষ্টি-বাতাসে নদী আরও বিপজ্জনক হলেও বর্ষাকালে অন্য একটা সুন্দরের আকাক্সক্ষা আমাদের খুব টানতো।
কেয়াকাঠাঁল! নদীর পাড়ে ঘন কেয়াবনে খুব কোমল লাল-কমলার পাকা কেয়াকাঁঠাল দেখলে আমাদের মন নেচে উঠত আনন্দে। সেগুলো সংগ্রহ করা যেত না। তবু কেন যে আনন্দ হতো তার কোন ব্যাখ্যা নেই। বৃষ্টির মধ্যে নৌকা চলার সুখানুভূতি আছে। মনটা ময়ূরের মতো সত্যি নাচে। মা ভিজে ভিজে খুব খুঁজতো কেয়াকাঁঠাল আর আমাকে দেখাতো! কিন্তু সেসব দেখতে যাওয়ার নৌকা, মাঝি, দাঁড়-বৈঠা কোথায় এখন! খুলনা-মোংলা রোড হচ্ছে, বগুড়ার খালের পরে সব খালে বাঁধ। সোনার ভিটের পাশে সেই গ্রামের ঘাটও নেই আর! ইচ্ছে হলেই তাই আর কোন দিন পাড়ি দেয়া হবে না সেই স্মরণের নদীরেখা!
স্বাধীনতার কয়েক বছর পরে রাজাকারের উত্থানপর্বে মামাবাড়িটাও বেদখল হয়ে গেল! ফলে যাতায়াত খুবই কম। বাইরে থাকি, বাড়িতেও আসা হয়ে ওঠে না। সম্ভবত ১৯৮৮-র দিকে একদিন খুলনা থেকে বাড়ি যাচ্ছি। মোংলার খেয়াঘাটে পৌঁছে আমি বিস্ময়ে হতবাক! মোংলা নদী ভরাট হয়ে আর খেয়া চলাচলেরও উপযোগী নেই! আমার চিরকালীন প্রমত্ত মোংলার এই মৃত ফুলে ওঠা শবের মতো উঁচু চর দেখে চোখের জল সামলাতে পারিনি! আমার কাছে অবিশ্বাস্য সেই দৃশ্য। ‘নদীভরাট’ শব্দের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল না। আমরা জানতাম, ‘নদীর একূল ভাঙে ওকূল গড়ে।’
এরপর যতবার বাড়ি গিয়েছি নদীর দিকে তাকাতাম না। ভেতরে একটা রক্তক্ষরণ হলেও কাউকে কিছু বলতেও পারিনি। ভাবতাম, দেখব না এই চর। মনের মধ্যে যে নদী সতত বহমান তার স্মৃতিই উজ্জ¦ল হয়ে বেঁচে থাকুক। বাস্তবতা তাকে যেন ম্লাণ করে না দেয়! আমি এখনও পাড় ভাঙার শব্দ শুনি, সেই বাঁকগুলোতে ঘূর্ণির গোঙানি, টাবুরে মাঝির বৈঠায় জলকাটার শব্দশুনি প্রবহমান রক্তের শিরা-উপশিরায়!
আরও পড়তে পারেন….
শঙ্খ নদ : দ্যা রিগ্রাই খিয়াং ।। মুহাম্মদ মনির হোসেন
এই মৃত নদী আমার তিস্তা না ।। শুভময় পাল
আমার নদী…তুই ডাকলেই সাড়া দেয় যারা ।। সুস্মিতা চক্রবর্তী
নদী একটাই ।। রাজেশ ধর