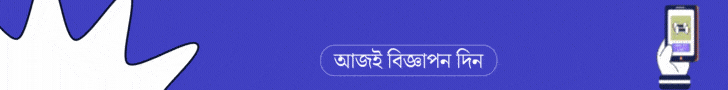ফুলের গন্ধটা তীব্র হয়ে নাকে লাগে। হু হু করে যখন বাতাস বইতে শুরু করল ঠিক তখন ঘুম ভেঙ্গে যায় আমার। কিন্তু এই নৌকায় ফুলের গন্ধটা কোত্থেকে আসবে বুঝতে পারিনা প্রথমে। পরে কারণটা ধরতে পারি ধীরে সুস্থে। আসলে আমি মায়ের কোলে শুয়ে ছিলাম। মায়ের কোলে শুয়ে আশৈশব পেয়েছি এই ফুলের ঘ্রাণ।
বড় হয়ে যখন কারণটা বুঝতে পেরেছি, ততদিনে মা আমাদের মায়া ত্যাগ করে পরপাড়ে পাড়ি জমিয়েছেন। মায়ের পছন্দ ছিল জবাকুসুম তেল, বরাবর বাবা তাই বাড়ি এনে দিয়েছেন, মা সেই তেল মাখতেন চুলে। কিন্তু, কারণ সনাক্ত হবার আগেই সেই যে অবুঝ শিশুর ধমনী জুড়ে ফুলের ঘ্রান ছড়িয়ে পড়েছিল মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে-পড়া স্মৃতির মধ্যে সেই ঘ্রান যায়নি আর! আজো মায়ের কথা মনে পড়লে ঘর জুড়ে সেই ফুলের গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসেছি ততক্ষণে। মা আদুরে ছেলের দরকারের কথা ঠিকই টের পেয়েছেন। বাবাকে ডাকলেন। বাবার আঙুল ধরে ছইয়ের বাইরে এসে চারিদিকে তাকিয়ে প্রস্রাবের বেগ যেন ভুলে গেলাম।
এক অপাথিব চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারিদিক, হাওয়ায় আকুল ডাকাতিয়া নদীর জলরাশি। বড় নৌকার ২ পাশে মোট ৪জন মাঝি,দাঁড় ও বৈঠার মৃদু আওয়াজ হাওয়ায় এক একটি টোকা দিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। ২ জন মাঝি নিচুস্বরে কথা বলছে আর হাত বদল হচ্ছে জ্বলন্ত বিড়িটার। এই তীব্র জ্যোছনায়ও কারুর মুখ ভালো করে দেখা যায় না, শুধু অবয়বটুকু বোঝা যায়। চাঁদের ভেতরের অন্ধকারের প্রভাব হয়তো বা! নৌকার উধমুখী গলুই যেন হাওয়ার বেগে সাঁই সাঁই করে ছুটছে চাঁদের দেশে! ছইয়ের ভেতরে আমরা কটি মাত্র প্রাণী- আমি, আমার বড় বোন, বাবা, মা আর আমার দাদী।
আমরা যাচ্ছি আমার বাবার নানার দেশে, বাবার ছোট মামুজানের বিয়েতে। আমাদের বাড়ির পেছনের বিস্তৃত জলাভূমির গা ঘেঁষে যে একটি সরু খাল আমাদের কয়েক কিলোমিটার দূরের বড় নদীটাকে যোগ করেছে সেটাই নৌ-পথ। এই খাল বেয়ে ডাকাতিয়া নদীর ভাটিতে সারা রাত নাও বেয়ে গেলে সকাল সকাল পৌঁছানো যায় বাবার নানার বাড়ির ঘাট। বছরের ছয় মাস এরকম, শুকনো মওসুমে জলবিরল খটখটে বিরাণ প্রান্তরে মাইলের পর মাইল হাঁটা পথ। পরদিন সকালে পৌঁছে দেখি- চারিদিকে ছড়ানো অগাধ পানির বেড়ে শুধু গ্রামখানি দ্বীপের মত জেগে আছে।
এইসব কতকাল আগের কথা। যেন উঠে এসেছে পুরাণ থেকে। আরো পরে আমরা যখন পরিবারসমেত এক মফস্বল শহরে উঠে এসেছি, তখন স্কুলের গরমের ছুটিতে গাঁয়ের বাড়ি গিয়ে আর খুঁজে পাইনি সেই পৌরাণিক পথ। আমাদের গাঁয়ের পাশের সেই খালটি বুঁজে গেছে ততদিনে- বড় নদীতেও পানির প্রবাহে টান, ওর নিজেরই অভাব, অন্যকে দেবে কি। এদিকটায় পাকা রাস্তা বানানোর সময় কালভার্ট বানানোর প্রয়োজনে অনেক পানির ধারা অপ্রয়োজনীয় বলে অনেকটা জোর করেই মেরে ফেলা হয়েছে। আমাদের বাড়ির পেছনের সেই বিশাল জলাভূমি– যাতে সারা দিন শাপলা ফুল, জল আর নীলাকাশে ভেসে-যাওয়া শাদা মেঘের ভেলা একদা উদাসী করেছিল এক বালকের যাযাবর মন – সেখানে এখন আদিগন্ত সবুজ ধানখেত হয়তোবা অন্য কোন বালকের মনে নতুন আবেগ জন্ম দিচ্ছে, সৃস্টি হচ্ছে আরেক গল্প। মরে গেছে সেই জলাভূমি, সেই খাল আর অকুল জলরাশির ডাকাতিয়া নদী।
সেই মফস্বল শহরে এসে পেলাম আর একটি নদী-আমার হারিয়ে যাওয়া নদীই হয়তো ফিরে এসেছে কিনা ভাবতে বসে দেখলাম- না এ এক পুরোপুরি নতুন নদী। ছোটবেলার সেই অথৈ জলরাশি নেই- বেশ শান্ত, ঘরোয়া এক স্বচ্ছ জলধারা ছোট্ট মফস্বল শহরটিকে কোমল আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেছে। নিত্যদিন, কারণে-অকারণে দেখা হয়ে যাচ্ছে তার সাথে। সেই যখন কিনা শুঁয়োপোকার মত শৈশবের খোলস ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছি কৈশোরের প্রজাপতি বেলায় তখন এই নদীই আমাদের সাথী। এর তীরেই আমরা বড় হয়েছি। দেখতাম হাটবারে কত দূর দূরান্তের নাও এসে ভিড়ছে বড়বাজারের ঘাটে। স্কুলে যাবার পথে, কোন বরষায় রেলওয়ে ব্রিজের কাছে এসে সহপাঠীদের নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যেতাম।
ব্রিজের লোহার থামে বাধা পেয়ে নিচে কী গভীর ঘুর্ণীতোলা স্রােত পাক খাচ্ছে, আর তারই মধ্যে কিনা কি অবলীলায় ঝাঁপ দিচ্ছে আমাদেরই বয়সী এক একটি কিশোর। ভয়ে শিউরে উঠতাম, আবার ভালোও লাগত। কলেজে ঢোকার মুখে কাঠের পুল পেরুতে হতো- তারও নিচে বইছে সেই একই নদী। উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনে ঢাকায় চলে আসার পর যখন মাঝে মধ্যে ফিরে গেছি সেই শহরে, তখন খেয়াল করেছি গুচ্ছের কচুরিপানা এসে চেপে ধরেছে নদীর টুটি- হায়, প্রিয় নদী আর নিশ্বাস নিতে পারছেনা, থেমে গেছে জীবনপ্রবাহ। পুরাতন ব্রম্মপুত্রের সাথে এর সংযোগস্থলে বাঁধ দিয়ে পাকা সড়ক করবার দরকারে এই নদীপ্রবাহ বাগড়া দিয়েছিলো বলে তার এই হাল।
আমাদের কৈশোরের সব গল্প জমা রইলো অই নদীর কাছে, যে নদী মরে গেছে। শিক্ষাজীবন শেষে যৌবনের শুরুতে নতুন কাজে যোগ দেবার পর উত্তরবঙ্গে যাবার সুযোগ হলো। সেই প্রথম যাওয়া উত্তরবঙ্গে। তখনও যমুনা সেতু হয়নি। পাড়ি দিতে হবে যমুনা নদী, মনটা নেচে উঠলো- নদী দেখবো -কত পড়েছি, কত গল্পে শুনেছি যমুনার কথা। বাহাদুরাবাদ ঘাটে এসেছি ট্রেনে চেপে। এবার ফেরি চেপে ওপাড়ে ফুলছড়ি ঘাট। তখন বর্ষাকাল, কালো মেঘে-ছাওয়া আকাশের নিচে ফুঁসছে যমুনা, যেন নদী নয় অকুল দরিয়া। বিশাল ফেরী তীব্র স্রােতে থরথর করে কাঁপছে। সেবার তিনঘন্টার যাত্রায় শেষ হয়েছিলো নদী পারাপার। তারপর আরও বহুবার গেছি উত্তরবঙ্গে। কিন্তু ততদিনে যমুনা সেতু তৈরি হয়েছে। তার ওপর দিয়ে আসা-যাওয়ার পথে বাসে, গাড়িতে অথবা ট্রেনের জানালায় যমুনায় দেখেছি কি বিশাল চড়া পড়েছে- সামান্য পানির ধারাটুকু যেন যমুনা দেবীর অশ্রুজল আমার মত উদাসী পথিকের দীঘশ্বাসে সামান্য সান্তনা। কোথায় সেই অকুল দরিয়া?
মনে পড়ছে, কুষ্টিয়ার শিলাইদহে রবীঠাকুরের কুঠিবাড়ি যখন দেখতে যাই প্রথমবারের মত তখন তো গড়াই নদী রীতিমত নৌকায় পাড়ি দিতে হয়েছিলো। কয়েক বছর বাদে দ্বিতীয়বার গিয়ে দেখি শুকনো খটখটে- আমরা কজন স্রেফ পায়ে হেঁটে পার হলাম। রবীঠাকুর নিজে যে বজরায় পূর্ববঙ্গে জমিদারী দেখার কাজে দিনের পর দিন নদীবক্ষে চষে বেড়িয়েছেন, এসে নামতেন একবারে কুঠিবাড়ির ঘাটে -এখন তার নামনিশানা নাই। কতদূরে সরে গেছে পদ্মা! শিলাইদহ ভ্রমণের সেই দ্বিতীয় যাত্রায় আমরা ট্রেনে ফিরছিলাম। গরমকালের কোন এক দুপুরে। ভেড়ামারা থেকে ট্রেন ছেড়েছে ঈশ্বরদীর পথে। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পেরুবার সময়ে ট্রেনের কামরায় মৃদু গুঞ্জন উঠলো। বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখি বিশাল বিস্তৃত পদ্মা নদী- কিন্তু যদ্দুর চোখ যায়- শুধু ধূ ধূ বালিয়াড়ি।
তারই মধ্যে ব্রীজের নিচে দিব্যি তৈরি হয়েছে পারাপারের পথ- সার বেঁধে চলছে মানুষ, মটর বাইক, অটোরিকশাসহ আরো নানাবিধ যান। আরো দূরে দৃষ্টি প্রসারিত হলে দেখা যায় চৈত্রের উত্তপ্ত হাওয়ার বেগে নদীর শূন্য হৃদয় যেন একেকবার আক্ষেপে বালির ঘুর্ণী তুলে অদৃশ্যে অভিশাপ ছুঁড়ে দিচ্ছে। এদিকে এই কামরায় এক অবাক শিশুর প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারছেন না তার বাবা। ছেলেটি বারবার জানতে চাইছিল – এই এত বড় লোহার পুল এখানে কেন বানানো হলো বাবা । কি দরকার পড়েছিলো বানাবার – সত্যিই তো, আমরা সকলে মুখ চাওয়চাওয়ি করি। ফারাক্কা বাঁধ চিরচঞ্চলা পদ্মা নদীর হাত পা শেকলে বেঁধে ফেলেছে ।
একই অভিজ্ঞতা হয়েছিলো কুড়িগ্রামের চিলমারী বন্দরে দাঁড়িয়ে- সাথে স্থানীয় এক কলেজের শিক্ষক। বিকেলের নরোম আলো এসে পড়েছে দূরে ব্রম্মপুত্রের শীর্ণ ধারায়। এখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এক পরিত্যক্ত নিস্তব্ধ বন্দরে। বালির স্তর দীর্ঘ চড়া ফেলেছে নদী জুড়ে। বন্দর ছেড়ে সরে গেছে নদী। কী মুখর ইতিহাস ছিলো অই বন্দরের। আমরা দুজন কথা বলি না – দীর্ঘ বালিয়াড়ি আর এক বন্দরের চাপা দীর্ঘশ্বাস সামনে নিয়ে মূক হয়ে থাকি। পরিত্যক্ত বন্দরে আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নামে।
যেমন অদ্বৈত মল্ল বর্মণের উপন্যাস পড়ে কিংবা আল মাহমুদের কবিতা পড়ে তেমনি ‘তিতাস একটি নদীর নাম”ছবিটি দেখে উন্মুখ হয়ে থাকি কবে দেখা হবে চাক্ষুস নদীটির সাথে। “তিতাস একটি নদীর নাম’ ছবিটিতে নদীর অকুল জলরাশি যেন প্রেক্ষাগৃহের পর্দা ছাড়িয়ে ভাসিয়ে নেবে তার দর্শকদের। অবশেষে অফিসের কাজে কয়েকবার যাবার সুযোগ ঘটে ব্রাম্মনবাড়িয়ার বাঞ্চারামপুরে, যার বুক চিরে বয়ে গেছে তিতাস। কিন্তু এই কি আমার আজন্মলালিত স্বপ্নের নদী – এ যে দেখছি রীতিমত একটা খাল! কোথাও দেখছি এপার ওপার সাঁতরে পাড়ি দিচ্ছে দুষ্টু কিশোরের দল। এইভাবে আরো আরো গল্প জমে স্বপ্নভঙ্গের ।
এইভাবে আমি বহন করে চলি আমার শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের প্রিয় নদীগুলির মৃত্যুর গল্প, তাদের ঘিরে আমার স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। আমার প্রিয় নদী মানে আমার শৈশবে হারিয়ে ফেলা ফুলের ঘ্রাণে সুরভিত মায়ের কোল, কৈশোরের প্রজাপতি প্রহর আর উদ্দাম যৌবনের যাযাবর দিনগুলি। আমার প্রিয় নদী মানে, ভাংগা খেয়াঘাট, পরিত্যক্ত বন্দর, লোহার শেকল পরানো স্লুইস গেট, চৈত্র নিদাঘে নদীবক্ষের বিক্ষুব্ধ বালিয়াড়ি, নদীপাড়ে ছেঁড়াখোঁড়া জালের ছায়ায় জেলে দম্পতির কষ্টে-সৃষ্টে বেঁচে -থাকা সংসার। আর অনেক রাতে তিস্তার কোন চরে রাতের গভীরে স্মৃতিভারাতুর যদি কেউ গেয়ে ওঠে: “ওরে কুল বাঁকা গাঙ বাঁকা, বাঁকা গাঙের পানিরে, বাঁকা গাঙের পানি। সকল বাঁকায় বাইলাম নৌকা, তবু বাঁকারে না জানিরে — দূরন্ত পরবাসে;” ভাবি হয়তোবা আমারই মনের ভুল।
২. কিন্তু “নদীর মৃত্যু নাই”- এ-কথা আমি ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করি মোহরকে চেনা ও জানার পর। মোহর মানে মোহরালী – আমার দ্বিতীয় গল্পের বই : “কখনো আড়াল”-এ সংকলিত “পরের জমিন”গল্পের মূল চরিত্র। তার যৌবনে সে ছিল নৌকার মাঝি , যখন কিনা নদীরও ছিল যৌবন। তারপর সেই নদী শুকিয়ে যায়- বন্ধ হয়ে যায় তারও রোজগারের পথ। নদীতীরের ছাপড়ায় তার সংসার যায় কষ্টে-সৃষ্টে, পেশা বদলিয়েও তার অচলাবস্থা কাটে না। এই দু:সহ পরিস্থিতিতেও সে নদীকে ছাড়ে না, নদী মানে নদীর স্মৃতি। নদীর যৌবনের স্মৃতি ঘুরেফিরে জীবনের শেষবেলায় এসেও তাকে দোলা দিয়ে যায়। তার স্বপ্ন ও স্মৃতিচারণায় যেভাবে বারবার নদী ধরা দেয় তার খানিকটা এরকম :
“নদীটিও ছিল ছোট, বেশ গেরস্থস্বভাবের: সারাদিন এপারের পানিতে পড়া ছায়া ওপারের ছায়াকে ব্যাকুল আগ্রহে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতো ! আর থাকতো রোদ, রোদে-গলা ইত:স্তত আকাশ, কখনো বা নিজেরই অজান্তে ফেলে-যাওয়া কোন নাইয়রির আধফোটা মুখ কি উড়ে যাওয়া কোন পাখির হঠাৎ-ছায়া। সব মিলে মিশে নদীর ছবিটি কী যে মনোহর ছিল! তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ছবি দেখার ফুরসতই বা ছিলো কোথায়? দূর ভাটির দেশ থেকে পেঁয়াজ, আলু আর ধানের চালান এসে নামতো বাজারে; সকাল থেকেই হাঁকডাক, চেঁচামেচি আর হাটের দিন হলে তো কথাই নেই। সবকিছু শেষ হতে হতে সেই অনেক রাত। ঝুপড়ির ক্লান্ত চালাগুলি চোখের পাতার মত বুঁদে যেতো একে একে, ভাঙা, ছন্নছাড়া হাটের ওপর দিয়ে বয়ে যেতো দূরের বাতাস। শেয়াল বেরুতো একটি দুটি খানিকপর। আর মস্ত শাদা চাঁদটি ভেঙেচুরে ডুবে থাকতো জলে, বৈঠার গা থেকে জোছনাকুচির মত গড়িয়ে গড়িয়ে নামতো পানির ফোঁটা, প্রথমে দ্রুত, তারপর অতি ধীরে — টুপ টাপ-টুপ- টা–প —”
প্রতিদানে নদীও বুঝি তাকে ছাড়ে না। বড় মায়ায় তাকে জড়িয়ে রাখে। যখন মৃত্যু আসে মোহরালীর দরোজায়, যেন নদীই তাকে নিতে আসে, সে-দৃশ্যের খানিকটা এইরকম : “শেষমেষ মোহরালী দেখে শান্ত, অতিচেনা, হারানো নদীটি আবার ফিরে এসেছে। আবার পানিতে ভাসছে মহাজনী নৌকার কোমল-কালো ছায়া, তার পাশে রোদে-আঁকা আকাশ।”
কেবলমাত্র মোহরালীর মৃত্যুর পর আমি বিশ্বাস করতে শুরু করি, নদী কখনো হারায় না। আবিষ্কার করি আমারও আছে নিজস্ব এক নদী। সে এক মায়াময় নদী। মনের গহনে নিরবধি সে বয়ে যায়। আমার বুকের আগুনে সে ঢালে শীতল জল। যদি কখনো থেমে যায় চলা, সে আনে বেগ ও গতি। কখনো ঘুমের অতলে তলিয়ে গেলে তার বুকে স্বপ্নের দাঁড় বেয়ে যেন উড়ে চলে আমার মন পবনের নাও।
১৩ জুন, ২০২০, ঢাকা ।
সৈয়দ কামরুল হাসান : কথাসাহিত্যিক।
আরও পড়তে পারেন….
প্রাণের দোসর কালীগঙ্গা ।। সন্তোষ কুমার শীল
নদীর আঁচল ।। আলিফ আলম
আড়িয়াল খাঁ নদ- স্মৃতি ও বাস্তবতায় ।। হাসান মাহবুব
আমাদের ছোটো নদী ।। গৌতম অধিকারী