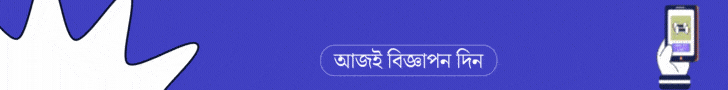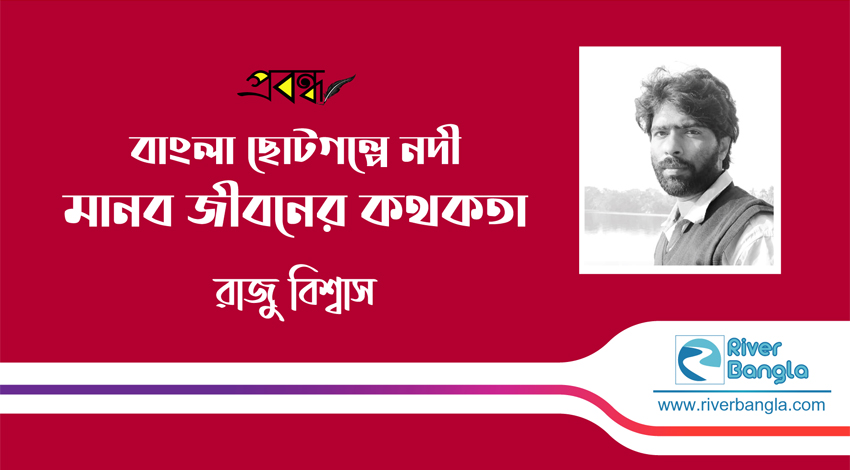নদীমাতৃক এই বাংলা। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে যে বৃহৎ বাংলা– তাকে মায়ের মত আদর স্নেহ ভালবাসা আর শাসন দিয়ে ঘিরে রেখেছে অসংখ্য নদ-নদী। নদীর তীরেই মানুষ সভ্যতার প্রথম সোপান রচনা করে। আমাদের বাণিজ্য যাত্রার ইতিহাস নদীকে কেন্দ্র করেই প্রসারিত হয়েছে। বাংলা মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃত পটভূমিকায় নদীর একটা আলাদা তাৎপর্য আছে। সেই চর্যাপদের সময় থেকেই সাহিত্যে নদনদীর কথা এসেছে গভীরভাবে। মনসা মঙ্গলের বেহুলা এই বাংলার নদী পথেই ভেলায় মৃত লখিন্দরের শবদেহ নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল অমরাবতির দরজায়।
আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে নদী একটা বিস্তৃত জায়গা জুড়ে রয়েছে। সাহিত্য কখনো দেশ কাল নিরপেক্ষ হতে পারে না। নদীকে ঘিরেই বিস্তার লাভ করেছে আমাদের অর্থনীতি ও সামাজিক পরিমণ্ডল। বাংলা গল্পকাররা নদীকেন্দ্রিক গল্পের মধ্য দিয়ে বার বার তুলে ধরেছেন মানব জীবন সংগ্রামের নানা দিক। মানুষের জীবন-জীবিকা, প্রেম, ভাঙা-গড়া, আনন্দ বেদনার সেই সব আশ্চর্য আখ্যান নির্মিত হয়েছে ছোটগল্পে।
দুই.
রবীন্দ্রনাথ জীবনের একটা বিশেষ সময় কাটিয়েছেন বাংলাদেশের পদ্মাপারে। সেই অভিজ্ঞতা ধরা পড়েছে তার বহু ছোটগল্পে। তবে ‘ঘাটের কথা’ গল্পে আছে গঙ্গা নদীর কথা। গঙ্গার একটি সুপ্রাচীন ঘাটকে কেন্দ্র করে এ গল্পের আখ্যান ভাগটি নির্মিত হয়েছে।
সমগ্র গল্পটি বিবৃত হয়েছে ঘাটের জবানীতেই। সমাসোক্তি অলংকারের প্রয়োগে লেখক গঙ্গা নদীর একটি ঘাটকে গল্পে জীবন্ত চরিত্র করে তুলেছেন। অসাধারণ কাব্যিক ভাষায় গল্পকার এখানে গল্পের নায়িকা কুসুমের সঙ্গে নদীর ঘাটকে আত্মীয়তাসূত্রে গেঁথে দিয়েছেন। গল্পে কুসুম বালিকা বয়স থেকেই নদীর সেই ভাঙা ঘাটে জল নিতে আসতো; একদিন তার বিয়ে হয়ে দূর দেশে চলে যায় সে। কিন্তু অনেক দিন পর আবার সে ফিরে আসে। ঘাট চিনে নেয় তাকে। শোনে কুসুমের স্বামী মারা গেছে। কিন্তু সেই নদী পারে যে সন্ন্যাসী আসে নদীর ঘাট জানতে পারে সেই আসলে কুসুমের হারিয়ে যাওয়া স্বামী। নতুন করে পরিচয় হলেও তাদের আর মিলন হয় না। এক অব্যক্ত যন্ত্রণা আর তীব্র অভিমান নিয়ে কুসুম গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। এই সমগ্র ঘটনার সাক্ষী থেকে যায় নদীর সেই ভাঙা ঘাট। তার বৃদ্ধ হৃদয়েও যেন বেঁচে ওঠে কুসুমের নিষ্পাপ হৃদয়ের কান্না :
”আমার কোলে যে খেলা করিত সে আজ তাহার খেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথায় সরিয়া গেল, জানিতে পারিলাম না।”
বস্তুত ‘ঘাটের কথা’ রবীন্দ্রনাথ মানব জীবনের বিচিত্র সুখদুঃখের সঙ্গে নদীর প্রবাহমানতাকে একত্র করে দেখিয়েছেন।
বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসের একটি মাইল ফলক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ‘তারিণী মাঝি’ গল্পটি। নদীকেন্দ্রিক গল্পের মধ্যেও এ গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৪২ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত এ গল্পের কেন্দ্রে আছে উত্তাল ময়ূরাক্ষী নদী। এ গকরতে মানুষের আদিম হিংস্র প্রবৃত্তির এক ভয়ানক করুণ আখ্যান রচিত হয়েছে।
তারিণী ময়ূরাক্ষীর মাঝি। সারাদিন সে খেয়া পারাপার করে যাত্রীদের পৌঁছে দেয় নিরাপদে। কখনো কেউ নদীতে পড়ে গেলে স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে তার জীবন বাঁচায়। স্ত্রী সুখীকে নিয়ে তার সুখের সংসার। কিন্তু যে নদী তার জীবন জীবিকার ঈশ্বর; শেষ পর্যন্ত সেই নদীই তার জীবনের সব আলো মুছে দেয়। তীব্র অনাবৃষ্টির পর গ্রামে যখন বন্যা আসে প্রথমে সকলের মনে তা আশার সঞ্চার করলেও ক্রমেই তা ভয়ানক রূপ ধারণ করে। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত ময়ূরাক্ষী ফুঁসে ওঠে। এক দুর্যোগের রাতে স্ত্রী সুখীকে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছানর জন্য তারিণী নদী সাঁতরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় : ল্পে মানুষের জীবন জীবিকার সঙ্গে নদীর ওতপ্রোত সংযোগ দেখানো হয়েছে; একই সঙ্গে উত্তাল নদীর সঙ্গে লড়াই করতে :
”সুখি দেখিল, ময়ূরাক্ষীর পরিপূর্ণ রূপ। বিস্তৃতি যেন পারাপারহীন। রাঙা জলের মাথায় রাশি রাশি পুঞ্জিত ফেনা ভাসা ফুলের মত দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।”
তারিণী সুখীকে নিয়ে নদীর উত্তাল স্রোতে ভাসতে ভাসতে যখন বোঝে আর এগোনো সম্ভব নয়; তখন প্রাণপ্রিয় স্ত্রী সুখীকে জলের অতলে ঠেলে দিয়ে নিজের জীবন বাঁচায়। মুছে যায় প্রেম; জেগে ওঠে আদিম হিংস্রতা। নদী এ গল্পে জীবন-মৃত্যুর দ্যোতক হয়ে উঠেছে।
তিন.
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃত অর্থেই প্রকৃতির পূজারী। নদী নিয়ে তার বিখ্যাত উপন্যাস ‘ইছামতী’। তবে ছোটগল্পে এতো বিস্তৃতভাবে নদীর কথা আসেনি। তবে গল্পের প্রেক্ষাপট নির্মাণে নদী কোনও কোনও গল্পে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে। তাঁর ‘মাছ চুরি’ গল্পটির কাহিনি নিতান্তই সাধারণ তবে রোমাঞ্চকর। তবে গল্পে নদীর এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। গ্রামের কয়েক জন ডানপিটে সাহসী বন্ধুরা মিলে গভীর রাতে শ্বাপদসঙ্কুল ভুতুড়ে ‘তেঁতুলতলার দোয়া’তে মাছ চুরি করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পরিকল্পনা মত রাতে এক জায়গায় হয়ে টুরু সন্তুরা তেঁতুল তলার দোয়ার গিয়ে সকালে গদাইয়ের বেঁধে রাখা বিশাল মাছটাকে সন্ধান করে। ভাঁটার নদীর স্রোত তীব্র বেগে বয়ে যাচ্ছে। তাতে বন্ধুদের কেউ কেউ বেসামাল হয়ে ভেসে গেলে অন্য বন্ধুরা তাকে আবার ডাঙায় তুলে আনে। কিন্তু সন্তু জলের অনেক নিচে দড়িতে বাঁধা মাছটার সন্ধান পেলেও সমবেত প্রচেষ্টায় এতো বড় মাছ জল থেকে অনেক কষ্টে ডাঙায় সকলে খুব ভয় পেয়ে যায়। দেখে সেটা আদৌ মাছ নয়, ‘প্রকাণ্ড কামট’! কামটের ভয় পায়না এমন কেউ নেই। শেষ পর্যন্ত সেটাকে নদীতে ছেড়ে দিয়ে নিরাপদে বাড়ি চলে আসে তারা। নোনা নদীতে ভরা বর্ষায় কুমীর কামট আসার গল্প আজো শুনতে পাওয়া যায়। বিভূতির এ গল্পে তার এক দারুণ উপভোগ্য কিশোর কাহিনি নির্মিত হয়েছে।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নদীর বিদ্রোহ’ আধুনিক সর্বগ্রাসী সভ্যতার প্রকৃতি-পীড়নের বিরুদ্ধে একটি নদীর প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের গল্প। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে নদীর স্বাভাবিক গতিকে বেঁধেছে। নদীর উপর নির্মাণ করেছে বাঁধ, বিশাল বিশাল ব্রীজ। ফলত পলি জমে গভীরতা হারিয়ে আরও সঙ্কীর্ণ হয়েছে নদী। তাই বর্ষায় জল ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে সে ভাসিয়ে নিয়ে যায় আশপাশের জনপদ; ডেকে আনে প্রবল বন্যা। বিদ্রোহ করে যেন মানব সভ্যতার বিরুদ্ধে। এ গল্পের নায়ক নদেরচাঁদ একজন স্টেশন মাস্টার। চার বছর সে একটা রেল স্টেশনে ডিউটি করছে। নদীর সঙ্গে তার আশ্চর্য প্রেম। ছেলেবেলা কেটেছে গ্রামের ছোট নদীর পারে। নদীর বুকেই তার শৈশব কৈশোর অতিবাহিত। তাই স্টেশন মাস্টারির চাকরিতে এসেও সে ছুটে যায় নদীর কাছে। নদীর উপর যে কংক্রিটের সেতু দিয়ে ট্রেন যায় তার এক পাশে বসে নদী দেখে সে। এক প্রবল বর্ষার মরশুমে সহকর্মীকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে সে হেঁটে চলে যায় রেল ব্রীজের উপর। কিন্তু অন্য দিনের তুলনায় নদীটাকে ভীষণ অচেনা লাগে তার। চেনা নদীটা প্রবল বর্ষায় ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ব্রীজের উপর বসেও সে যেন হাত দিয়ে জল ছুঁতে পারবে। স্ত্রীর উদ্দেশে লেখা একটা চিঠিকে সে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। তার মনে হয় মানুষের এই কংক্রিটের সভ্যতার বিরুদ্ধে নদী এভাবেই বিদ্রোহ করে। কিন্তু মানুষ শেষ পর্যন্ত নদীকে বাঁচতে দেয় না। নদীর জন্য কষ্টে তার বুক ফেটে যায়। রেললাইন ধরে ফিরে আসার পথে ‘৭ নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি’ নদেরচাঁদকে পিষে দিয়ে বেরিয়ে যায়। এক করুণ আবহের মধ্য দিয়ে এ গল্পের পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে লেখক আসলে প্রকৃতির প্রতিশোধের এক ভয়ানক ইঙ্গিত তুলে ধরতে চেয়েছেন।
চার.
জগদীশ গুপ্ত বাংলা ছোটগল্পের জগতের এক ব্যতিক্রমী লেখক। তাঁর ‘দিবসের শেষে’ গল্পটিতে আছে একটি মিথের সত্যি হয়ে ওঠার করুণ ও আশ্চর্য কাহিনি। এ গল্পের প্রেক্ষাপটে আছে কামদা নদী। রতি নাপিত ও নারায়ণীর ছেলে পাঁচ বছরের ছেলে পাঁচু। তাঁর মা নারায়ণী পাঁচুগোপালের মাদুলি ধারণ করে পাঁচুকে গর্ভে ধরেছিল। তার আগে নারায়ণীর তিন ছেলেকে নদী গ্রাস করেছে। তাই এই শেষ সন্তানটিকে সে সর্বদা তাই চোখে চোখে রাখতো। একটা কুসংস্কারের পরিবেশ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।
পাঁচু একদিন ঘুম থেকে উঠে তার মাকে জানায় তাকে আজ কুমিরে নেবে। গল্পকার অসাধারণ সাসপেন্স তৈরি করে বারবার পাঁচুকে কুমিরের মুখ থেকে যেন ফিরিয়ে আনছেন। তাতে মনে হয় পাঁচুর অসংলগ্ন কথাগুলো আসলেই ভিত্তিহীন। কিন্তু দিনের শেষে সে যখন শেষ বারের জন্য বাবা রতির সঙ্গে নদীতে স্নান করতে গেল, ভুলে তার খেলার ঘটটি নদীর ঘাটে ফেলে এলো। রতির কাছে অনুমতি নিয়ে সেই খেলার ঘট আনতে গিয়েই শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই কুমীরে ধরল পাঁচুকে। এক অমোঘ করুন বাস্তবতা যেন গল্পের শেষে পাঠকের হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দেয়। এ গল্পে নদী হয়ে উঠেছে মানুষের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক। তার অমোঘ গ্রাস থেকে নিস্তার নেই কারো।
আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের জগতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর ‘নদী ও নারী’ গল্পটিতে নারী ও নদী যেন সমার্থক হয়ে উঠেছে। দুজনেরই অসীম জীবনীশক্তি। নদী যেমন পার ভেঙে লোকালয় ভাসিয়ে এগিয়ে যায় সামনের দিকে, কোনও বাঁধাই তাকে শেষ পর্যন্ত রুখতে পারে না। নারীও তেমনি নদীর মত এগিয়ে চলে সামনে। মৃত্যু আর সমস্ত স্থবিরতার মুখে ছাই দিয়ে তার যাত্রা এক অনন্ত অসীমের পথে। পদ্মার বুকে অবসর যাপনের উদ্দেশে গিয়ে সুরপতি ও নির্মলা ‘ববড” কাট’ অত্যাধুনিকা নীলিমার সঙ্গে পরিচিত হয়। সে মেয়েটি নদীর মতই খামখেয়ালী আর উদ্ধত। তাকে দেখে একজন হাইপ্রোফাইল বারবণিতা বলে মনে হলেও শেষ পর্যন্ত সুরপতিরা আবিস্কার করে মেয়েটি আসলে তা নয়। ডাক্তারের পরামর্শ মত সে এই তিন বছর ধরে নিজের পঙ্গু অথর্ব স্বামীকে শুশ্রূষা দিয়ে সুস্থ করে তোলার জন্য নদী বক্ষে বাস করছে। তার স্বামী একটা ক্রেন অ্যাকসিডেন্টে নিজের একটা হাত হারিয়েছে। পাটাও হাঁটুর নীচ থেকে কাটা পড়েছে। নার্ভে চাপ পড়ে তার চোখদুটিও নষ্ট হয়ে গেছে। নীলিমাকে দেখে অনিবার্যভাবে আমাদের মনে পড়বে বেহুলার কথা। সেও গাঙুরের জলে মৃত স্বামীকে বাঁচাতে ভেলা ভাসিয়েছিল। কিন্তু নীলিমা আর বেহুলা এক নয়। লেখক বেহুলার মিথটিকে ভেঙেই নীলিমাকে নির্মাণ করেছেন। স্বামীর জন্য তার হৃদয়ে অকৃত্রিম প্রেম আর আত্মত্যাগ থাকলেও মুখে কষ্টের কোনও ছাপ নেই। নদী আর নারী জীবনের দুটি রূপ এ গল্পে যেন ভিন্ন এক আবেদন নিয়ে ধরা দিয়েছে।
পাঁচ.
জীবন নদীতেও জোয়ার আসে; ভাঁটা হয়। মানুষের জীবন-জীবিকা, প্রেম-ভালবাসা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির উপর জীবনের জোয়ার ভাঁটা নির্ভর করে। তা নদীর মত নিয়ম করে আসে না। মানুষের জীবন আসলে ভীষণ অনিশ্চিত। কখনো তার হৃদয়ে ভরে থাকে নীল আকাশের আলো, আবার কখন যে সেই মন মেঘে ঢেকে যায় মানুষ নিজেই তা জানে না।
সমরেশ বসুর ‘জোয়ার ভাঁটা’ গল্পে সমাজের নিম্নবর্গের না খেতে পাওয়া শোষিত পীড়িত দিনমজুরদের জীবনকথা উঠে এসেছে। নদীর সঙ্গে তাদের জীবিকা জড়িয়ে। যেদিন বালি-টালি ইত্যাদি বোঝাই নৌকা আসে, সে দিন ন্যায্য মজুরি না পেলেও খাওয়া জোটে তাদের। তখন শত অভাবের মধ্যেও তাদের মনে রঙ লাগে। আনন্দে তারা মেয়ে-মরদ মিলে গান ধরে কত। কিন্তু নৌকা না এলে তাদের সব গান নিভে যায়। আনন্দের রঙ মুছে দিয়ে পেটে টান পড়ে। তখন তাদের ভিতরের হিংস্র মানুষগুলো বেরিয়ে এসে পরস্পরের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী বিবাদে জড়ায়। আবার একটু আশার আলো দেখলেই একে অপরের হাত ধরাধরি করে বেঁচে থাকতে জানে তারা। আলোচ্য গল্পে কৈলাস ভোলা শ্যামা কামিনীরা নদীর পারে গিয়ে সারাদিন আশায় থাকে মাল বোঝাই নৌকা আসবে। আড়তদারদের খামখেয়ালীপনায় সারাদিন কেটে যায়। পেটের খিদে পেটে চেপে তারা তবু আশায় আশায় থাকে নৌকা আসবে। কিন্তু আসে না। তারা বিবাদে জড়ায়। কিন্তু সব শেষে নৌকা আসে। আবার তাদের জীবন নদী যেন জোয়ারের জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে।
দেবর্ষি সারগী এ কালের একজন ভিন্ন ধারার প্রতিষ্ঠিত গল্পকার। তাঁর অন্যতম সেরা গল্প ‘পদ্মার গ্রাস’ প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে ‘শারদীয় আজকাল’ পত্রিকায়। এ গল্পের প্রেক্ষিতে পদ্মার বন্যা কবলিত একটি বিস্তীর্ণ জনপদের মানুষের সার্বিক যন্ত্রণা- দুর্ভোগের বাস্তব চিত্র উঠে এলেও গল্পের কাহিনি ক্রমশ মোড় নিয়েছে পরাবাস্তবতার দিকে।
উত্তম পুরুষে লেখা এ গল্পের কথক পদ্মার বন্যায় গ্রামের আরও বহু পরিবারের মতই নিজের পরিবারের সঙ্গে তাদের গৃহদেবতার শরণ নেয়। ‘পদ্মাকে তারা একটা শ্বাপদ জন্তুর সঙ্গেই তুলনা করে’। পদ্মার গ্রাস থেকে বাঁচাতে তাদের গৃহদেবতা সত্যি সত্যিই ভয়াল নদীর বুকে এক সুবিশাল নৌকা নিয়ে হাজির হয়। সে নৌকায় চাইলে সকল গ্রামবাসী উঠে পৌঁছে যেতে পারে নিরাপদ আশ্রয়ে। কিন্তু সকলেরই গৃহ দেবতা ভিন্ন ভিন্ন। তাই অন্যের গৃহদেবতার সাহায্য নিলে যদি নিজেদের গৃহদেবতা রুষ্ট হয়-এই ভয়ে তারা কেউ সে নৌকায় ওঠে না। অবশেষে বাড়ির পালন করা সব হাঁস মুরগী বিড়াল ইত্যাদিসহ গল্পের কথক আর তার পরিবার সে নৌকায় গিয়ে ওঠে। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর কথক দেখতে পায় তাদের বাড়ির কুকুরটাকে না নিয়েই তারা চলে আসছে। কুকুরটাকে বাঁচিয়ে নৌকায় আনার জন্য সে পদ্মার বুকে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু সে কিছুতেই স্রোত ঠেলে পারে উঠতে পারে না। জলের অতলে ক্রমশ তলিয়ে যেতে থাকে। জলের নিচে গৃহদেবতা এসে তার হাত ধরলেও শেষে দেবতা তার হাত ছেড়ে নিজেই উপরে উঠে যায়। আর কথক ‘নদীর শান্ত বিছানার দিকে’ তলিয়ে যেতে থাকে। এ গল্পে আসলে এক রহস্যময় যাদু বাস্তবতার জগত নির্মাণ করে নিঃসহায় মানুষের কল্পনার মধ্যে দিয়ে তার স্বপ্নপূরণ এবং একই সঙ্গে বাস্তবের কঠিন আঘাতে সেই স্বপ্নভঙ্গের এক আশ্চর্য আখ্যান নির্মাণ করেছেন লেখক। পদ্মার ভয়াল রূপ এ গল্পে আধুনিক ভাষায় ও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুত নদীকেন্দ্রিক বাংলা ছোটগল্পে একদিকে যেমন উঠে এসেছে জীবনের অসংখ্য অতিবাচক দিক, তেমনি অপর দিকে প্রকাশিত হয়েছে নদীকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবনের গভীর অন্ধকারের প্রসঙ্গ। নদী যেন স্বয়ং নটরাজ। যার এক পায়ের নিচে ধ্বংস; অন্য পায়ে থাকে নব সৃষ্টির বার্তা।
ছয়.
মানব সভ্যতায় নদীর দান অপরিসীম। নদী আমাদের জীবনযাপনের সঙ্গে মিশে রয়েছে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় এই নদীকে আমরা ক্রমাগত অত্যাচার করে চলেছি। বাংলার বেশির ভাগ নদীই বর্তমানে মৃত্যুর মুখে। নদীর বুকে বিশাল বিশাল ব্রিজ বানিয়ে, বাঁধ দিয়ে আমরা নদীর যাত্রাপথে বাঁধার সৃষ্টি করছি। ফলত পলি জমে জমে গভীর নদীগুলিও তাদের নাব্যতা হারিয়ে সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে প্রতি বছর বন্যায় প্রাণ হারাচ্ছে অসংখ্য মানুষ। নদীর বুকে আমরা বজ্য পদার্থ ফেলে দূষিত করে তুলছি নদীর জল। ফলত নদীর মাছও যাচ্ছে মরে। নদীকে ছাড়া আমাদের মানব সভ্যতাও বাঁচতে পারবে না। নদী বাঁচলে আমরাও বাঁচবো। তাই আমাদের উচিত যথাসম্ভব নদী দূষণ বন্ধ করা এবং নদীর বুকে ইতস্তত ব্রীজ ও বাঁধ না হতে দেওয়া। নদীকে বাঁচানোর জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে।
রাজু বিশ্বাস : কবি ও গল্পকার, কলকাতা, ভারত।
আরও পড়তে পারেন….
ফুলেশ্বরীর খোঁজে
সব নদী গাছ ।। হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
আমার নদী মধুমতী ।। রুখসানা কাজল