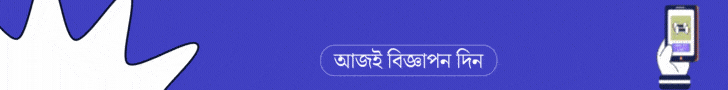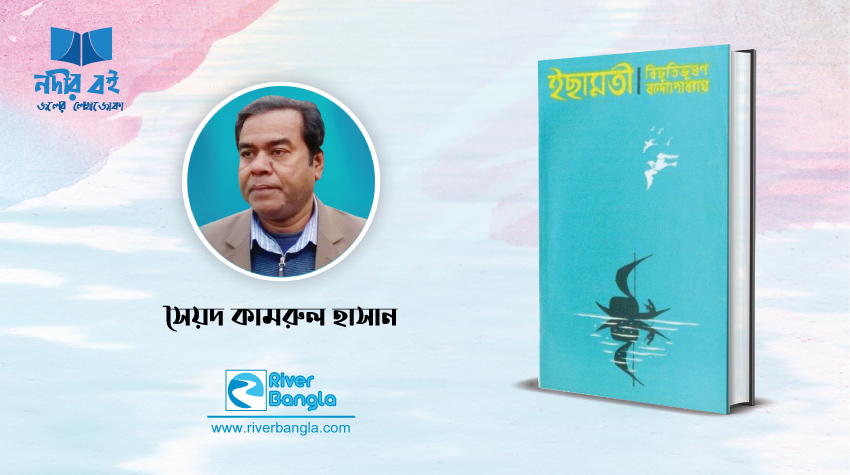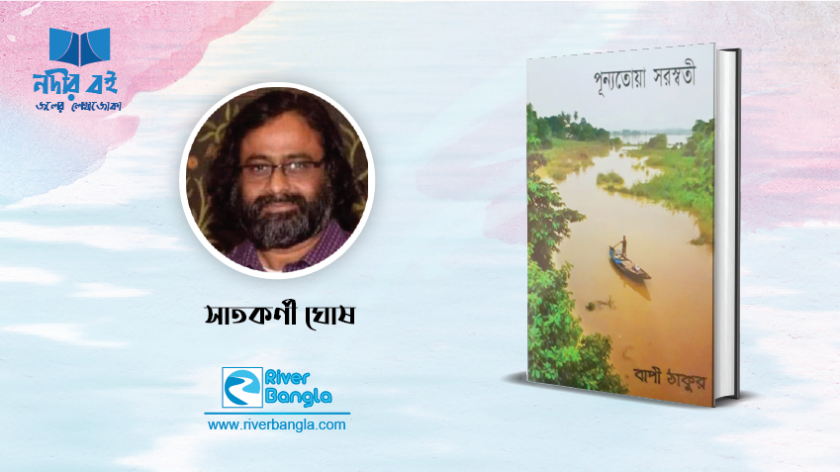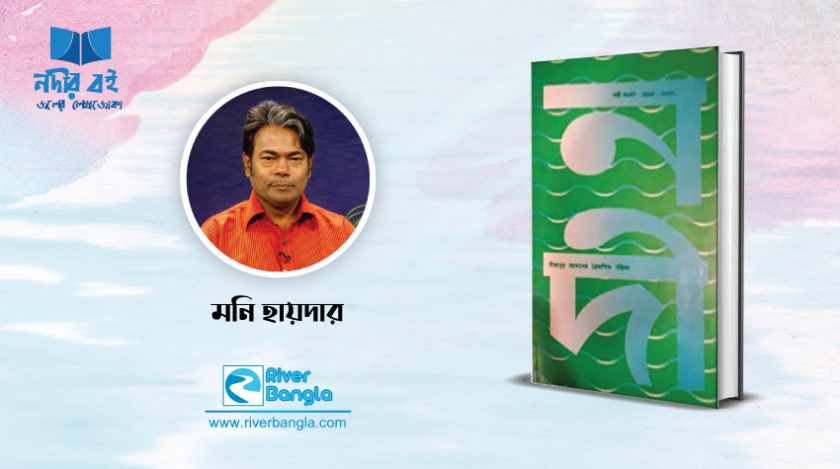১.
১৯৪৭ সালের ১৭ জুলাই ছোটভাই নুটুবিহারী বন্দোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রে বিভূতিভূষণ ‘অভ্যূদয়’ নামে সাময়িকীতে তাঁর ‘ইছামতী’ উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের কথা জানিয়েছিলেন। নিজের গ্রাম বারাকপুর, তৎসন্নিহিত নদী এবং এর আশপাশ, ইংরেজ নীল চাষী, তাদের পরিত্যক্ত স্থাপনা ইত্যাদি নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার আকাঙ্ক্ষা তিনি পোষণ করেছিলেন, যখন তিনি প্রথম উপন্যাস ‘পথের পাঁচালী’ লিখছিলেন তখন থেকেই ।
এ-ব্যাপারে ১৯২৮ সালে তাঁর ডায়রী ‘স্মৃতির রেখায়’ তিনি লিখে রেখেছিলেন তাঁর আগ্রহের কথা। তাঁর ভাষায়: “ঐ আমাদের গ্রামের ইছামতী নদী । আমি একটা ছবি বেশ মনে করতে পারি – ঐ রকম ধূ ধূ বালিয়াড়ী ,পাহাড় নয়, শান্ত, সিগ্ধ দুপাড় ভরে ঝোপে ঝোপে কত বনকুসুম, কত ফুলে ভরা ঘেঁটুবন, গাছপালা, গাঙ শালিকের বাসা, সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট, আকন্দফুল। গত পাঁচশত বছর ধরে কত ফুল ঝরে পড়েছে- কত পাখি কত বনঝোপে আসছে যাচ্ছে, সিগ্ধ পাটা শ্যাওলার গন্ধ বার হয়। জেলেরা জাল ফেলে, ধারে ধারে কত গৃহস্থের বাড়ি। কত হাসিকান্নার খেলা। আজ পাঁচশত বছর ধরে কত গৃহস্থ এল, কত হাসিমুখ শিশু প্রথম মায়ের সঙ্গে নাইতে এল, কত বৎসর পরে বৃদ্ধাবস্থায় তার শ্মশানশয্যা হল ঐ ঠান্ডা জলের কিনারাতেই, ঐ বাঁশ বনের ঘাটের নিচেই। কত কত মা, কত ছেলে, তরুণ তরুণী সময়ের পাষাণবর্ত্ম বেয়ে এসেছে গিয়েছে মহাকালের বীথিপথ বেয়ে। ঐ শান্ত নদীর ধারে ঐ আকন্দ ফুল, ঐ পাটা শ্যাওলা, বনঝোপ, ছাতিম বন। এদের গল্প লিখবো, নাম হবে ইছামতী ।”
বিভূতিভূষণ নিজে ইছামতী পারের মানুষ হবার সুবাদে এর আশপাশের মানুষ ও জনপদের প্রতি ছিল তাঁর অন্তরের টান, হয়তোবা এদের নিয়ে কিছু একটা লেখার জন্য একধরণের দায়বদ্ধতা বোধ করেছেন তিনি। লেখকের ব্যক্তিজীবনের সাথেও জড়িয়ে ছিল এই নদী। তাঁর দৈনন্দিন রুটিন থেকে জানা যায় : “খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন। প্রবল গরম হোক, বা প্রবল শীত, স্নান করতে যেতেন ইছামতীতে। ফিরে লিখতে বসতেন।” ইছামতী নদীতে স্নান করতে গিয়ে পানিতে ডুবে মারা গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণের সহোদরা জাহ্ণবী দেবী ; আকস্মিক সেই শোকে তিনি ভেঙ্গে পড়েছিলেন। অবশেষে সেই নদী নিয়ে তাঁর হাতে রচিত হয়েছিলো -বাংলা সাহিত্যের নদীভিত্তিক উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম সেরা সৃষ্টি – ইছামতী । ৫৬ বছরের আয়ুসীমায় ২৮ বছরের লেখক জীবনে এটি বিভূতিভূষণের নিজেরও শেষ রচনা । বইটি তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী রমা বন্দোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছিলেন । ১৯৫১ সালে ইছামতী উপন্যাসের জন্য বিভূতিভূষণ পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার (মরণোত্তর) লাভ করেন।
কাগজপত্র ঘেঁটে মূল ইছামতী নদীর তিনটি প্রবাহের সন্ধান পাওয়া যায়, যার প্রায় দুই -তৃতীয়াংশ আজ বিলুপ্ত। একসময়ে পশ্চিম ঢাকায় প্রবহমান ছিল এই নদী, যার অবলুপ্ত শেষাংশটুকুর সন্ধান মেলে দিনাজপুরে। ইছামতীর বর্তমানে সচল অংশটুকু পদ্মার শাখানদী মাথাভাঙা থেকে জন্ম নিয়ে ২০৮ কিলোমিটার প্রবাহিত হবার পর ভারতের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার হাসনাবাদের কাছে এবং বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটার কাছে কালিন্দী নদীর সাথে যুক্ত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।
নদীর বর্তমান প্রবাহটি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমারেখা তৈরি করেছে। নদীয়া এবং যশোরের মধ্যে একদা প্রবহমান ছিল যে স্রােতস্বিনী নদী আজ এর ছায়ামাত্রও নেই। প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট নানাবিধ পরিবেশগত দুর্বিপাকে এমনকি নিজ জীবদ্দশায়, বিভূতিভূষণ যখন তাঁর জীবনের শেষদিকে নিজ গ্রাম বারাকপুরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন – ইছামতী তখনই বুড়িয়ে গিয়েছিলো।
স্বভাবত প্রশ্ন জাগে : সেজন্যই কি উপন্যাসের সময়কালকে তিনি তাঁর লেখার সময়কাল থেকে ৮০-৯০ বছর পিছিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন? তিনি লিখতে চেয়েছেন সেই ইছামতীর কথা যখন তা ছিল সেকালের পদ্মা, গঙ্গা বা ব্রম্মপুত্রের মত কোন বিশালকায় নদী নয় বটে, কিন্তু মাঝারি ধরণের এমন এক নদী যার বুকে ছিল স্বচ্ছ জলধারা সতত প্রবহমান, যার তীর জুড়ে বইছিল শান্ত ও নিরুপদ্রব প্রকৃতি ও জনগোষ্ঠীর জীবনধারা; যাতে দৃশ্যমান হয়েছিল প্রকৃতির সজল শ্যামল রূপশ্রী ও তীরবর্তী মানুষের প্রবহমান জীবনধারার স্বাভাবিকতা।
বিভূতিভূষণের শক্তিশালী কলমের আঁচড়ে নদী ও জনপদের সেই রূপশ্রী যেন চিন্ময় বিভূতিতে ধরা দিয়েছে আর আমাদের সাহিত্যে তা হয়ে উঠেছে চিরকালের সম্পদ। ছবি আঁকবার আগে শিল্পী যেমন করে ক্যানভাসে রং চড়ান, তেমনি করে বিভূতিভূষণ উপন্যাসে প্রবেশের আগে, এর উপক্রমণিকায় বর্ণনা দেন নদী ও তীরবর্তী জনপদের, যাতে লেখার বিষয়বস্তু সম্পর্কেও পাঠকের মন ও মগজ প্রস্তুত হবার অবকাশ পায়। দীর্ঘ উপক্রমণিকায় তিনি লিখছেন : “ ইছামতীর যে অংশ নদীয়া ও যশোর জেলার মধ্যে অবস্থিত, সে অংশটুকর রূপ সত্যিই এত চমৎকার, যাঁরা দেখবার সুযোগ পেয়েচেন, তাঁরা জানেন। কিন্তু তাঁরাই সবচেয়ে ভালো করে উপলব্ধি করবেন, যাঁরা অনেকদিন ধরে বাস করচেন এই অঞ্চলে। ভগবানের একটি অপূর্ব শিল্প এর দুই তীর, বনবনানীতে সবুজ,পক্ষী-কাকলিতে মুখর। — সবুজ চরভুমির তৃণক্ষেত্রে যখন সুমুখ জ্যোৎস্নারাত্রির জ্যোৎস্না পড়বে, গ্রীস্ম দিনে সাদা থোকা থোকা আকন্দফুল ফুটে থাকবে, সোঁদালী ফুলের ঝাড় দুলবে নিকটবর্তী বনঝোপ থেকে নদীর মৃদু বাতাসে, তখন নদীপথ-যাত্রীরা দেখতে পাবে নদীর ধারে পুরোনো পোড়ো ভিটের ঈষদুষ্ঞ পোতা, বতমানে হয়ত আকন্দ ঝোপে ঢেকে ফেলেছে তাদের বেশি অংশটা, হয়তো দু-একটা উইয়ের ঢিপি গজিয়েছে কোনো কোনো ভিটের পোতায়। এই সব ভিটে দেখে তুমি স্বপ্ন দেখবে অতীত দিনগুলির, স্বপ্ন দেখবে সেইসব মা ও ছেলের, ভাই ও বোনের, যাদের জীবন ছিল একদিন এইসব বাস্তুভিটের সঙ্গে জড়িয়ে। কত সুখদু:খের অলিখিত ইতিহাস বর্ষাকালে জলধারাঙ্কিত ক্ষীণ রেখার মত আঁকা হয় শতাব্দীতে শতাব্দীতে এদের বুকে। সূর্য আলো দেয়, হেমন্তের আকাশ শিশির বর্ষণ করে, জ্যোৎস্না-পক্ষের চাঁদ জ্যোৎস্না ঢালে এদের বুকে। সেইসব বাণী, সেইসব ইতিহাস আমাদের আসল জাতীয় ইতিহাস। মূক জনগণের ইতিহাস, রাজারাজড়াদের বিজয়কাহিনী নয়।”
স্পষ্টতই লেখক তাঁর রচনা-সময়কালের জলবায়ু-পরিবর্তনে বিপর্যস্ত ইছামতীর গল্প লিখতে চাননি, তিনি ধরতে চেয়েছেন ইছামতীকে এর আদিরূপে, বাস্তবে যার অস্তিত্ব এখন আর নেই। তবে কি একালের পাঠকদের কাছে ইছামতী উপন্যাস শুধু অতীতচারিতা? একালের গবেষকদের কাছে কি শুধুই তা স্মৃতির জাদুঘর (Museum of Memories)? তা যে শুধু অতীতচারিতা নয়, বরং প্রকৃতি ও মানবজীবনের চিরায়ত সম্পর্ক যা নদীর মত মহাসাগর অভিমুখে চির ধাবমান অসীম শক্তিমত্তায় সেই রহস্যময়তার গ্রন্থি উন্মোচন করেছেন বিভূতিভূষণ। জীবনের প্রথম উপন্যাস মাস্টারপিস ‘পথের পাঁচালী’তে তিনি যে অপরিসীম দক্ষতায় অপুকে (পাঠককেও) অতীতচারিতা/নষ্টালজিয়া থেকে মুক্ত করে এনে পথের দেবতার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন, সেই কৌশলে শেষ উপন্যাসেও আশ্চর্য নৈপুন্যে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। সবকিছু ছাপিয়ে চলমানতা ও গতিই সেখানে সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইছামতী হয়ে উঠেছে আবহমান কালের প্রতীক। অথচ তা করতে গিয়ে কোনো ‘জাদুবাস্তবতায়’ সমর্পিত হননি তিনি কিংবা গুরুত্বহীন করে তোলেননি স্থান-কাল-পাত্রের বাস্তবতা! সেই বাস্তবতার কার্যকারণ ও ঐতিহাসিকতা অটুট রেখেই তিনি তা সম্ভব করে তুলেছিলেন। বিভূতিভূষণের পাঠক মাত্রই জানেন বাংলা সাহিত্যের এই কালজয়ী শিল্পী কী অসাধারণ ভারসাম্যে তাঁর এক একটি উপন্যাসে স্বপ্ন ও বাস্তবতার, মীথ ও বিজ্ঞানমনস্কতার সমন্বয় ঘটিয়েছেন।
আর একটি প্রশ্নও জাগে- দূর্ভিক্ষের কাছাকাছি সময়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে জাপানী বিমান হামলার আশংকায় কোলকাতা যখন কম্পমান সেই তখন হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ও অত্যাসন্ন দেশভাগের প্রেক্ষাপটে তিনি কেন একেবারে সম্পূর্ণ পিছু ফিরে উনবিংশ শতকের পটভুমি বেছে নিলেন উপন্যাস রচনার জন্য? তবে কি তিনি এক ভঙ্গুর সময়ের অস্থির চালচিত্র রচনার ভার সমসাময়িক অন্য লেখকদের কাঁধে তুলে দিয়ে, সেই অস্থির নাগরিক জীবনের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে রচনা করতে চেয়েছিলেন এক শান্ত কল্পলোক? তিনি কি বলতে চেয়েছেন এটুকুই আমাদের সবটুকু নয়? বলতে চেয়েছেন জীবনের যাত্রাপথ মহাজীবনের দিকে প্রসারিত যা আসলে এক বহতা নদী আর তাতে আছে ঢেউয়ের দোলাচল, জোয়ার ভাটা, আছে ভাঙ্গা -গড়া, আছে মহাজীবনের ভাঁজে ভাঁজে আরো জীবন? ইছামতী লিখে তাই যেন জানাতে চেয়েছেন লেখক। নদী ও মানবজীবন প্রবাহের শ্বাশ্বত সত্যে একাকার হয়েছে উপন্যাসে। বহমানতাই সত্য। সে-কারণে উপন্যাসের শেষ ও শুরুতে আমরা খুব যেন তফাৎ দেখিনা, জীবন ও নদীর সমান্তরাল বহমানতা একীভূত হওয়ার আকাঙ্খা ও অন্বেষায় অন্তিমেও ফুটে উঠতে দেখি ।
২.
বাংলা ১২৭৩ (ইংরেজি ১৮৬৩) ইছামতী নদী তীরবর্তী পাঁচপোতা নামের এক গ্রামে উপন্যাসের আখ্যান গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে তখন পুরোদমে চলছে নীলচাষ। নীলচাষ, নীলকুঠি ও নীলবিদ্রোহ এই আখ্যানের একটি প্রধান অংশ জুড়ে বিস্তৃত। এখানকার মোল্লাহাটির নীলকুঠিতে আমরা বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানীর প্রজানিপীড়ক মি: শিফটনের দেখা পাই। তাঁর কুঠিতে কাজ করে ধুত দেওয়ান স্থানীয় এক কুলীণ ব্রাম্মণ রাজারাম রায়, আমীন প্রসন্ন চক্কোত্তি ও অন্ত্যজ শ্রেণীর একদল কামলা-কর্মচারী। অন্ত্যজ শ্রেণীর এক নারী গয়ারাণী ওরফে গয়ামেম ‘মিসট্রেস’ বা সায়েবের ছায়াসংগিনী হিসাবে বাংলোয় থাকেন। এদের নিয়ে মি: শিফটন দোর্দন্ডপ্রতাপে তাঁর ব্যবসা ও নীলচাষের বিস্তার ঘটান। আখ্যানের বিস্তারে আমরা লক্ষ করি সমসাময়িককালের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক সততায় উপস্থাপিত। কাহিনীর গ্রন্থিমোচনে ঔপন্যাসিক দেখান কীভাবে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদে রূপ নিয়েছে। এসময়ে নানা স্থানে সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহ ও জার্মানীতে কৃত্রিম নীল উৎপাদনের অভিঘাতে বাংলাদেশ জুড়ে বিস্তৃত নীল চাষ ও ব্যবসায় ধ্বস নামে। উপন্যাসের শেষদিকে রাজারাম দেওয়ান খুন হন, প্রসন্ন আমীন চাকুরী হারান এবং গয়া মেম নীল কুঠির বাংলোর বিলাসী জীবন থেকে ছিটকে পড়েন। এই পরিবর্তনের সুবাদে স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (হকার) নালু পাল বড় মহাজনী ব্যবসায়ীতে রূপান্তরিত হন এবং কুঠিয়াল শিফটনের বাংলো কিনে নেন। কুঠিয়াল শিফটন তাঁর ইংল্যান্ডের গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন না , কুঠিসংলগ্ন গোরস্থানে তিনি সমাধিস্থ হন। আখ্যানে রেফারেন্স হিসাবে আসে আরো অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাও, যেমন- ১৮৫৯-৬১ সালের নীল বিদ্রোহ, ১৮৩১ সালের তিতুমীরের বিদ্রোহ, ১৮৭২ সালে লর্ড মায়োর হত্যাকান্ড, ১৮৮৭ সালে পুরীর কাছে জন লরেন্সের জাহাজডুবি, ১৮৭৮ সালে আফগান যদ্ধে ইংরেজদের বিজয় এবং ১৮৮০ সালে সেন্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ের উদ্বোধন। কোলকাতা বন্দরে পণ্য আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে নব্য ধনী নালু পালের পণ্য পরিবহনে ইছামতী নদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নালু পালের রেলে কোলকাতা যাতায়াতের মধ্য দিয়ে সূদূর কোলকাতা নাগরিক সভ্যতার প্রতীক হয়ে উঠে। এ সবকিছু সত্বেও বিভূতিভূষণ নীল চাষকে ঘিরে সমসাময়িক আর ২/১০টা রচনার মত ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেননি। এই আখ্যানকে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন ইছামতীর বহমানতার সাথে। কিন্তু কীভাবে ? বিভূতিভূষণে -এর সাথে যুক্ত করেন ইছামতী তীরবর্তী প্রবহমান জনগোষ্ঠী ও অবিনশ্বর প্রকৃতিকে। নীল কুঠির কর্মযজ্ঞ ও জীবনপ্রবাহের সমান্তরালে পাঁচপোতার যে অলস-শান্ত-মধুর গ্রামীণ জীবন তাকে তিনি তুলে আনেন – তার মানুষগুলি ও প্রকৃতির বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে।
কুঠির প্রতাপশালী দেওয়ান রাজারামের তিন বোন তিলু, বিলু আর নিলুর বিয়ে হয় গ্রামে ঘুরতে আসা সন্ন্যাসীপ্রতীম ভবানী বাড়–য্যে নামের আরেক কুলীনের সাথে। তিন বোন দিব্যি মিলে মিশে ঘরসংসার করে। মূলত: এঁদের চোখ দিয়েই আমরা ইছামতী তীরের গ্রাম-জীবনধারা ও সেখানকার চরিত্রগুলো দেখি। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় কপমন্ডুকতায় আচ্ছন্ন অলস গ্রামবাসী, বুড়ো ব্রাম্মণদের নিত্য পরচর্চার কথা আর সরল আধ্যাত্মিকতা ও ইছামতী নদীর দুই তীরে লীলায়িত অনিন্দ্যসুন্দর প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে মানুষের প্রাত্যাহিক দিনযাপনের ছবি। তেমন শক্ত গাঁথুনীর কোন গল্প নয়। গ্রামীণ জীবনযাত্রা ইছামতীতে আঁকা হয়েছে মানবিক দিনলিপির ঢংয়ে। প্রচলিত অর্থে নায়ক নায়িকাও এখানে অনুপস্থিত। এখানে কুটিল রাজারাম দেওয়ান যেমন আছে, আছে সুযোগসন্ধানী নালু পাল, হলা ডাকাত, রসিক মল্লিক, জীবন চাটুজ্যে, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়ানো স্বাধীনচেতা যুবতী নারী নিস্তারিনী কিংবা কুঠিয়ালের অবৈধ সঙ্গিনী গয়া মেম, আবার আছে ভবানী বাড়–য্যে ও রামকানাই কবিরাজের মত বিষয়বিমুখ, ঈশ্বর ও প্রকৃতি অভিভূত নির্লোভ, সরল প্রাণ মানুষেরা । কিন্তু একজন প্রখর জীবনবোধসম্পন্ন শিল্পী হিসেবে বিভূতিভূষণের বর্ণনায় বাদ পড়ে না, স্থবির গ্রামসমাজে নারীর অবদমন, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মীয় কুসংস্কার ও জাতপাতের দ্বন্দ্ব। ইতিহাসের অভিঘাতে গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তনশীলতার সাথে সাথে সমাজ জীবনের আরো নানান ভাঙচুর তিনি তুলে আনেন। উপন্যাসের শেষ দিকে এসে আমরা দেখি গ্রামের রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে তিলু -নীলুদের সাহস বাড়ছে, নিস্তারিনী আরো সাহসী হয়ে উঠছে, রেল চালু হলে কোলকাতার সঙ্গে যোগাযোগের যে নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে – গ্রামের যুবকরা তা কাজে লাগাচ্ছে এবং এমনকি ঈশ্বরপ্রেমী ভবানী তার শিশুপুত্রকে টোলে পড়িয়ে সংস্কৃত পন্ডিত বানানোর স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে তাকে ইংরেজি স্কুলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
কিন্তু এখানেই উপন্যাস লেখার চরিতার্থতা খুঁজে পেয়ে বিদায় নেন না তিনি । অর্থ্যাৎ কেবল বর্তমানের কাছে পাঠককে সঁপে দিয়ে বিদায় নেন না লেখক। বরং (আগেই বলেছি ) ঘটনাপ্রবাহকে তিনি দেখেন নদীর সাথে মিলিয়ে – এ যেনো সময়ের মঞ্চে বয়ে যাওয়া ঢেউ, উঠছে ও নামছে, নিতুই পালা বদল ঘটছে তার জোয়ার ভাটায়। তাই বিভুতিভ’ষণ দৃষ্টি মেলে দেন আরো দূরে, শ্বাশ্বতের দিকে,শ্বাশ্বত প্রবহমানতার দিকে – উপন্যাসে যার মেটাফোর হিসেবে তিনি হাজির করেন ইছামতী নদী – সে যেনো পরিবর্তমান ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষ্য নিয়ে গভীর উদাসীনতায় বয়ে যায়। হয়তোবা সেকারণেই উপন্যাসে ভালোয়-মন্দে মোটা দাগের কোন ভেদরেখা টানেন না লেখক। বিভূতিভূষণের অন্যান্য উপন্যাসের মতই মন্দ চরিত্রগুলিও তিনি গভীর মমতায় আঁকেন। বিভূতিভূষণ যেন বলতে চান – ভালো ও মন্দ, গুণ ও দোষ, জোয়ার ও ভাটা – এ জীবনপ্রবাহেরই অংশ। শুধু অংশ নয় – এ যেন রহস্যময়ী প্রকৃতির কোলে সদা-লীলায়িত বিশ্বব্রম্মান্ডব্যাপী আবহমান কালের কোন শ্বাশ্বত সুরের ঐক্যেও বাঁধা। গল্পের একটি প্রধান চরিত্র [কেন্দ্রীয় চরিত্রও বলা যায়] ভবানী বাড়–য্যে এক বিকেলে ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে তাঁর একমাত্র শিশুপুত্রটির দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। তখন তাঁর মনে এক গভীর ভাবনার উদয় হয়: “কোথায় ছিল এ শিশু এতদিন ? বহুদূরেরও কোন অতীতের মোহ তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করে? যে পৃথিবী অতি পরিচিত, প্রতিদিন দৃষ্ট – যেখানে বসে ফনি চক্কতি সুদ করেন, চন্দ্র চাটুজ্যের ছেলে জীবন চাটুজ্যে সমাজপতিত্ত্ব পাবার জন্য দলাদলি করে – অজস্র পাপ, ক্ষুদ্রতা ও লোভে যে পৃথিবী ক্লেদাক্ত – এ যেন সে পৃথিবী নয় । অত্যন্ত পরিচিত মনে হলেও এ অত্যন্ত অপরিচিত, গভীর রহস্যময়। বিরাট বিশ্বযন্ত্রের লয় সঙ্গতির একটা মনোমুগ্ধকর তান। পিছনকার বাতাস আকন্দ ফুলের গন্ধে ভরপূর। স্তব্ধ , নীল শূন্য যেন অনন্তের ধ্যানে মগ্ন ।” (পৃষ্ঠা -২৬৫)।
এইভাবে বিভূতিভূষণের হাতের ছোঁওয়ায় নিত্য দিনের উর্ধে উঠে যায় পাঁচপোতার জীবনধারা । তিনি পরম সত্য অনুসন্ধান করেন চলমান বাস্তবতা ও ইতিহাসের মধ্য থেকে নয় । কোলকাতার দৈনিক আনন্দবাজারে প্রকাশিত (২৮ নভেম্বর, ২০১৫) এক আলোচনায় যমুনা বন্দোপাধ্যায় তাঁর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন তিনি : “জীবনকে শুধু বস্তুপৃথিবীর গন্ডীতে দেখতেন না ”।
আমাদের ধীমান কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক বলছেন : “ তুচ্ছের মধ্যে অমৃতের সন্ধান করে গেছেন বিভূতিভূষণ। কীভাবে তা মিলতে পারে অমৃতের স্বাদ নিতে নিতেই আমাদের তা জানিয়ে গেছেন।” ইছামতী উপন্যাসে ভবানী বাড়–য্যের মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ যেন স্বয়ং প্রকাশিত হন । তিনি লিখছেন : “ চৈত্র মাস যায় যায়। মাঠ বন ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছে। নির্জন মাঠের উঁচু ডাঙায় ফুলে-ভরা ঘেঁটু বন ফুরফুরে দক্ষিণে বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে । স্তব্ধ, নীল শূন্য যেন অনন্তের ধ্যানমগ্ন-ভবানীর মনে হোল দিক হারা, দিকচক্রবালের পিছনে যে অজানা দেশ, যে অজ্ঞাত জীবন, তারই বার্তা যেন এই সুন্দর, নির্জন সন্ধ্যাটিতে ভেসে আসছে।” (পৃষ্ঠা-২৬৮) প্রকৃতিকে ধর্মগ্রন্থ হিসাবে দেখেছেন বিভূতিভূষণ, এই ভাবে দেখতে গিয়ে তিনি এমনকি সনাতন হিন্দু সমাজের প্রচলিত গন্ডী ভেঙেছেন অবলীলায়। তাঁর রচনায় সনাতন ধর্মগ্রন্থ ও প্রতিষ্ঠান ভেঙেচুরে একাকার হয়ে আর একটা নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে, হয়ে উঠেছে আরো সজীব ও সবাক। প্রকৃতিকে তিনি নতুন ভাষা দিয়েছেন,তাঁর কলমে প্রকৃতি হয়ে উঠেছে মহাজীবনের প্রতীক। ইছামতীতেও আছে সেই প্রমাণ, এই স্তবক কি সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে না ?
“ প্রাচীন শাস্ত্র বেদ, যে বেদ প্রকৃতির গায়ে লেখা আছে। আমার মনে হয় ফুল-নদী, আকাশ, তারা, শিশু এরা বড় বড় ধর্মগ্রন্থ। এদের মধ্য দিয়ে তাঁর লীলা বিভূতি দর্শন বেশি করে। পাথরে গড়া মন্দিরে কী হবে, যার ভেতর তিনি নিজে থাকেন সেটাই তাঁর মন্দির। এই চড়পাড়ার বিলে আসবার সময় দেখলাম কুমুদ ফুল ফুটে আছে, ওটাই তাঁর মন্দির।” (পৃষ্ঠা -৩২৭) এ-কারণেই সমকালীন, পূর্ব কিংবা উত্তর প্রজন্মের লেখককূলে গোটা বাংলা সাহিত্যে তিনি মৌলিক ও অনন্য । কথাটা ঘুরিয়ে এভাবেও বলা যায় -বস্তুতান্ত্রিকতার প্রচলিত গন্ডীর বাইরে এনে তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন প্রকৃতিকে নতুন করে দেখার একটা দৃষ্টি। আমাদের সাহিত্যে এটুকু তাঁর অবদান।
৩.
ধারণা করা অসংগত হবে না যে, এই গল্প/প্লট কালজয়ী অপর দুই কথাসাহিত্যিক তারাশংকর ও মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের হাতে পড়লে কিভাবে রূপায়িত হত! তাঁদের সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতা থেকে এমত অনুমান করা চলে – মাণিক ব্যানার্জীর কলমে তিন সহোদরা তিলু, বিলু আর নিলুর এক ছাদের নিচে এক স্বামীর ঘর অইরকম নিবিড় প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিক আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে করা সম্ভব হতো কীনা তা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ করা চলে। বরং অই প্রকৃতি-বন্দনা (পূজা) ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে মানিকের চরিত্ররা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খুঁজে নিত সন্দেহের চোরকাঁটা । আশপাশের অন্যরাও ওদের এই কূটকচালে জড়িয়ে ফেলত কিনা যেমন সেই গ্রামবুড়োর দল – তারাইবা কী ভূমিকা নিত। ধারণা করি, মাণিক ব্যানার্জীর রচনায় এই আখ্যান হয়ে উঠতো শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সতত দ্বন্দ্বমুখর এক নতুন সৃষ্টি। অন্যদিকে তারাশংকর তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে এই আখ্যান হয়তো আরো ছড়িয়ে দিতেন, হয়তো দেখাতেন তিনি পরিবর্তনের চাপে জীর্ণ হয়ে আসছে দরিদ্র কৃষিজীবী সমাজের আধ্যাত্মিক প্রশান্তির পরিসর ; তা তাদের পাশ দিয়ে যতই বয়ে যাক না কেন ইছামতীর জীয়ন্ত ধারা ! হয়তো নদীতীরবর্তী জনপদে তিনি খুঁজে নিতেন উনবিংশ শতকের নদীয়া-যশোর এলাকার ভাবান্দোলনের প্রতীক কোন বাউল/বোষ্টম সম্প্রদায় যাদের গলার মরমী সুর খুঁজে ফিরতো একদা সমৃদ্ধ জনপদের অতীত গৌরব। উপন্যাসের চরিত্র নির্বাচনে নদীতীরবর্তী সমাজের জনমিতিতে দাপুটে কোন মুসলিম চরিত্র এনে তিনি হয়তো সমাজের সম্পূর্ণ চেহারা হাজির করতেন। সে যাহোক, নিম্নবর্গের জীবনের বিশ্বস্ত চিত্রায়ন ও তাদের প্রতি মমতায় এই তিন শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যের অনেক মিল থাকা সত্বেও আমরা আগেই কতকটা বলার চেষ্টা করেছি- বিভূতিভূষণ ছিলেন কোথায় স্বতন্ত্র !
ইছামতীর অন্য একটি স্বাতন্ত্র্য এবার উল্লেখ করা যাক। বাংলা সাহিত্যের বহুল আলোচিত নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলির মধ্যেও বৈশিষ্ট্যে ও চরিত্রে ইছামতী ব্যতিক্রম। বহুল আলোচিত, পঠিত, পাঠকনন্দিত ও সেরা চলচ্চিত্রকারদের হাতে সেলুলয়েডে চিত্রায়িত ‘পদ্মানদীর মাঝি’ (মাণিক বন্দোপাধ্যায়), ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (অদ্বৈত মল্ল বর্মণ) ও গঙ্গা (সমরেশ বসু) সম্পূর্ণভাবে জেলেদের পেশা, মাছধরা ও একান্তভাবে তাদের জীবনের উথথান-পতন নিয়ে আবর্তিত। সবকটি উপন্যাসেই নদী তাদের জীবনের নিয়ন্ত্রক ও নিয়ামক হয়ে উঠেছে । কিন্তু মৎস্যজীবীদের জীবনের বয়ান ইছামতীর মুখ্য উপজীব্য নয় । এদিক থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘কাঁদো নদী কাঁদো’র কথাও উল্লেখ করা যায়। উভয়টিই নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস হওয়া সত্বেও ঠিক সেগুলি জেলেজীবনের গল্পে কেন্দ্রীভূত নয়। যদিও আবার উভয়ের ক্ষেত্রেই নদীকে আনা হয়েছে জীবনের বহমানতার প্রতিরূপ হিসাবে। ইছামতীতে একটি নদী তার তীরবর্তী জনপদ ও সমাজের বহমানতা পুরোটাই অস্তিত্বে ধারণ করে মহাসাগরের দিকে ধাবমান, অন্যদিকে সেই প্রবাহমানতা রূদ্ধ হলে ব্যক্তি ও সমাজের স্থবিরতা ও মৃত্যু যে অনিবার্য নিয়তি হিসাবে আবির্ভূত অর্থ হয় তাই ফুটে উঠে ‘কাঁদো নদী কাঁদো’র গল্পে। আমার ধারণা, বিষয়টি আরো বিস্তৃত গবেষণার দাবি রাখে।
৪.
উপন্যাসের শেষ দিকে এসে আমরা দেখি গয়া মেম এসেছে ভগ্ন ও বিধ্বস্ত কুঠির গোরস্তানে শিফটন সাহেবের সমাধিতে কিছু সন্ধ্যামালতী আর বকফুল ছড়িয়ে দিতে। তখন “ পঞ্চমীর কাটা চাঁদ কুমড়ার ফালির মত উঠেছে পশ্চিমের দিকে।” কেউই মনে রাখেনি আজ সায়েবের ‘মরার তারিখ, ’ গয়া মনে রেখেছে। নাটকীয়ভাবে (পথ ভুলে), সেখানে ঘোড়া চালিয়ে এসে হাজির হন গয়ার প্রতি অনুরক্ত বৃদ্ধ আমীন প্রসন্ন চক্রবতী, একদিন এই কুঠির আমীন হিসেবে তারও ছিল ঝলমলে দিন। অস্পষ্ট জ্যোছনায় গয়ার চোখে জল চিকচিক করে উঠতে দেখেন তিনি। গয়ার অনুরোধে তিনিও কিছু ফুল ছড়িয়ে দেন সায়েবের সমাধিগাত্রে । তারপর উঠে পড়েন প্রসন্ন আমীন, ঘোড়ায় চেপে মিলিয়ে যেতে থাকেন। লেখক গল্পের শেষ স্তবকটি লিখেছেন : “ষষ্ঠীর চাঁদ জুনিপার গাছের আড়াল থেকে হেলে পড়েছে মড়িঘাটার বাঁওড়ের দিকে। ঝিঁ ঝিঁ পোকারা ডাকচে পুরনো নীলকুঠির পুরনো বিস্মৃত সাহেব-সুবোদের ভগ্ন সমাধিক্ষেত্রের বনে জঙ্গলে ঝোপঝাড়ের অন্ধকারে !…. ”
কিন্তু উপন্যাসের প্রচলিত আখ্যানটুকু এখানে শেষ হলেও, ইছামতীর পথ চলা যে শেষ হয় নি ! জীবন ও ইতিহাসের সীমা পেরিয়ে সে বয়ে চলে আরো দূর কোন লক্ষে বুঝি বা বয়ে চলে আরো প্রসারিত করে দিতে জীবন ও ইতিহাসের নতুন সীমানা। লেখক বিভূতিভূষণও তাই এগিয়ে যান; গল্পের শেষে জুড়ে দেন নতুন আরেক অধ্যায় আর পাঠকও সেই যাত্রায় সাথী হতে চিরকালের জন্য বাঁধা পড়েন। ইছামতীর শেষ বাক্য ক’টি পড়ুন: “বর্ষার দিনে এই ইছামতীর কূলে কূলে ভরা ঢল ঢল রূপে সেই অজানা মহাসমুদ্রের তীরহীন অসীমতার ছবি দেখতে পায় কেউ কেউ। কত যাওয়া-আসার অতীত ইতিহাসমাখানো ঐসব মাঠ, ঐ সব নির্জন ভিটের ঢিপি- কত লুপ্ত হয়ে যাওয়া মুখের হাসি ওতে অদৃশ্য রেখায় আঁকা। আকাশের প্রথম তারাটি তার খবর রাখে হয়তো। ওদের সকলের সামনে দিয়ে ইছামতীর জলধারা চঞ্চল বেগে বয়ে চলেছে লোনা গাঙের দিকে, সেখান থেকে মোহনা পেরিয়ে, রায়মঙ্গল পেরিয়ে, গঙ্গাসাগর পেরিয়ে মহাসমুদ্রের দিকে।”
৫.
পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানতে পেরেছি –ইছামতী নদী আজ নাকি দখলে-দূষণে মৃতপ্রায় দুই বাংলায়। ইছামতী উপন্যাসে বিভূতিভূষণ যে ছবি এঁকে গেছেন তা কোন নির্দিষ্ট সময়ে বয়ে-চলা নির্দিষ্টকোন নদীর নয়, তা গোটা মানবজীবনের প্রতিরূপ । তা কোন ‘স্মৃতির জাদুঘর’ নয়, এক প্রাণবান জীবন্ত সত্তার প্রতীক, যা বেঁচে থাকার এক সম্প্রসারিত অর্থ। তা বহমানতার রূপক এক মহামিলনের মোহনার দিকে । এ-কারণেই বিভূতিভূষণের ইছামতী কেবল একটি নদী তীরবতী জনপদের গল্প নয়, তা মহাজীবনের মেটাফোর। চরিত্রে ও বৈশিষ্ট্যে এই রচনা মহাকাব্যিক। অবশেষে ইছামতী পাঠের অভিজ্ঞতায় আমরা নতুন এক অভিজ্ঞান লাভ করি: – নদীকে হত্যা করা মানে আমাদের প্রাচীন, লোকায়ত ঐতিহ্যের এক প্রাণবান সত্তাকে হত্যা করা-ইছামতী যেন বিভূতিভূষণ সতর্ক তর্জনী ।
২৫-০৬-২০২১
ঢাকা
তথ্য ও আলোচনা সূত্র:
শ্রী অশ্বিনী কুমার দাস : আলীগড় সন্দভ ,২০০৯: বাংলা উপন্যাসে ও ছোটগল্পে অন্ত্যজ জীবন
The River as a Metaphor of history -A study of Bibhutibhuson Bandopadhaye’s ICHAMOTI
স্মৃতির রেখা : বিভূতিভূষণের ডায়রী
দৈনিক আনন্দবাজার : ২৮ নভেম্বর,২০১৫
দৈনিক আনন্দবাজার : ১৯ নভেম্বর,২০১৬
ইরাবতী /অনলাইন সাহিত্যপত্র ১২ সেপ্টেম্বর,২০১৯ : ইছামতীর ধারে, বিভূতিভূষণকে নিয়ে : ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়
এই সিরিজের আরও লেখা পড়ুন…
‘পদ্মা নদীর মাঝি’ আমাকে পদ্মায় নিয়ে ফেলে
অদ্বৈত মল্লবর্মণ: তিতাস একটি নদীর নাম
‘মহানদী’, এক সাধারণ পাঠকের অনুভব
‘মহানদী’, এক সাধারণ পাঠকের অনুভব

সৈয়দ কামরুল হাসান, কথাশিল্পী। প্রধানত গল্পকার। বসবাস করেন ঢাকায়। পেশাগতভাবে একটি বেসরকারি সংস্থার প্রধান হিসেবে দায়িত্বপালন করছেন। নদী তাঁর ভীষণ প্রিয়। প্রকাশিত বই দুটোই গল্পের।