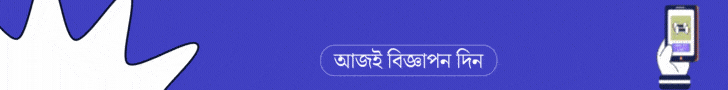‘মানবজীবন সে তো/ গঙ্গায় ভাসন্ত বাছাড়ির নাও।/ ফুটো থাকলেই টানতে থাকে তলানিতে/ আবার—/ মানবজীবন সে তো/ বর্ষার জোয়ার ভাটা/ জলেঙ্গার জল।/ দু দণ্ড জোয়ার তো চার দণ্ড ভাটা/ চার দণ্ড সুখ তো আট দণ্ড দুঃখ।/ তবে অবাক হবার কিছু নেই।’ মানবজীবন ও নদীর সাদৃশ্য এভাবে উত্থান-পতন, ভাঙা-গড়ার রূপকে চিরকাল চিত্রিত হয়েছে। আর এভাবেই বিশ্বের সব ভাষায় লিখিত সাহিত্যের রূপকল্পে নদীর বহুমাত্রিক চিত্র আত্মপ্রকাশ করেছে। আদি মহাকাব্য মহাভারত-রামায়ণ কিংবা হোমারের ইলিয়াড-ওডিসি’র কাহিনি ব্যাপ্ত হয়েছে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ে। আর মর্ত্যের নদী সেখানে বিশাল অংশ দখল করে আছে। ধ্রুপদী সাহিত্যে তা ভারতীয় কালিদাস কিংবা মধ্যযুগের শাহনামা’য় নদী মানবজীবনের সঙ্গে একীভূত। প্রাচীন সভ্যতাগুলো যেমন নদীকেন্দ্রিক ছিল তেমনি সাহিত্যের আদি নিদর্শনে নদী তার গতিময়তায় কবিতা-গানে প্রাণ দান করেছে। বাংলা শিল্প-সাহিত্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য, নগর-জনপদ গড়ে উঠতে নদী বড় ভূমিকা রেখেছে। তাই সংগতভাবেই প্রত্যেক সাহিত্যিকের লেখনীতেও কোনো না কোনোভাবে এসেছে নদীকথন। সাহিত্য-বুননে ধৃত হয়েছে নদীর উপমা, প্রতীক আর চিত্রকল্পের পর চিত্রকল্প। আদি মহাকাব্য রচনার সময় থেকে নদীর দেবতা অথবা দেবী কল্পনার শুরু এবং তাঁদের বন্দনা সাহিত্যে স্থান পেতে থাকে। আবার একক কোনো নদীস্তোত্রও রচিত হয়েছে। কোথাও নদী জননীস্বরূপা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায় কপোতাক্ষের প্রশস্তি গেয়েছেন, ‘দুগ্ধ-স্রোতরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে।’ বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদেও এসেছে নদী; নির্বাণের রূপকে। তবে কবিতার চেয়ে বিস্তৃত পরিসরে উপন্যাসে নদী ও জীবনকে রূপায়িত হতে দেখা গেছে বেশি। শলোকভের ‘প্রশান্ত দন’ রাশিয়ার বৈপ্লবিক জীবনের মহাকাব্য। দন নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবনের সংগ্রাম ও সংরাগ ব্যক্ত হয়েছে এর কাহিনিতে।
রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিস্তৃত অঞ্চল দখল করে আছে নদী। ‘আমাদের ছোট নদী’র মতো শিশুতোষ রচনা কেবল নয় বাংলাদেশের পদ্মা নদী এবং শান্তিনিকেতনের কোল ঘেঁষে বয়ে যাওয়া কোপাই অথবা কলকাতার গঙ্গা আর বিশ্বের অনেক জানা-অজানা নদীর সঙ্গে বিশাল ব্যাপ্ত শিল্পজগত্ গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের। বাংলাদেশে থাকার সময় শিলাইদহের উত্তরে প্রবাহিত পদ্মা বা পশ্চিমে প্রবাহিত গড়াই নদী বা শিলাইদহের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিকে মোহিত করেছিল। এক্ষেত্রে পদ্মা ছিল তাঁর শিল্পসাধনসঙ্গী। কারণ পদ্মাকে যে দেখেনি বাংলাদেশকে দেখেনি সে, পদ্মাকে যে জানে না বাংলাদেশকে জানে না সে, পদ্মাকে যে বোঝেনি, বাংলাদেশকে বোঝেনি সে; যা কিছু দেখা জানা বোঝা সমস্ত সংহত এই নদীটির মধ্যে। এই পদ্মাতীরে বসে কবি তাঁর অন্তর্নিহিত কবিধর্মকে যেমন আবিষ্কার করেছেন, তেমনি পদ্মার কলধ্বনিতে শুনেছেন বাংলার জনজীবনের কোলাহল। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতৃস্মৃতি গ্রন্থে লিখেছেন, ‘…বাবার গদ্য ও পদ্য দুরকম লেখারই উত্স যেমন খুলে গিয়েছিল শিলাইদহে, এমন আর কোথাও হয়নি। এই সময় তিনি অনর্গল কবিতা প্রবন্ধ ও গল্প লিখে গেছেন — একদিনের জন্যও কলম বন্ধ হয়নি। শিলাইদহের যে রূপবৈচিত্র্য, তার মধ্যে পেয়েছিলেন তিনি লেখার অনুকূল পরিবেশ।’ নদীকে কেন্দ্র করে বিপুল সৃষ্টির উপকরণ অর্জিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে। প্রমথনাথ বিশী ‘ছিন্নপত্র’কে ‘পদ্মার মহাকাব্য’ বলে অভিহিত করেছেন। কবিমনে পদ্মা ধীরে-ধীরে বাস্তব প্রকৃতিকে ম্লান করে মানস প্রকৃতির ভাব গ্রহণ করেছে। সে পরিণত হয়েছে এক মানবীয় সত্তায়, ভরা বর্ষায় দুকূলপ্লাবিনী পদ্মার কাছে রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছেন জীবনের আশ্বাস, এগিয়ে চলার মন্ত্র। সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালীর মতো কাব্য গড়ে উঠছে এ-সময়। চিত্রাঙ্গদা, বিদায়-অভিশাপ লিখিত হওয়ার সময়ও এটি। গড়ে উঠেছে অজস্র গান। ‘ছুটি’ গল্পের ফটিক, ‘সুভা’ গল্পের সুভা বা ‘সমাপ্তি’ গল্পের ‘মৃন্ময়ী’কে তিনি পেয়েছেন নদীর তীরেই। ‘পোস্টমাস্টার’, ‘মেঘ ও রৌদ্র’ বা ‘ক্ষুধিত পাষাণ’-এর মতো গল্পের সৃষ্টিও পদ্মার পারেই। ‘দেনাপাওনা’, ‘শাস্তি’, ‘স্বর্ণমৃগ’ গল্পের সৃষ্টির পেছনে রয়েছে পদ্মাপাড়ের জনজীবন। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের একটি উপন্যাসের নাম ‘নৌকাডুবি’। নদীতে নৌকাডুবির ফলে সৃষ্ট জটিলতায় আখ্যান এগিয়েছে এখানে।
পূর্বেই বলা হয়েছে উপন্যাসে সবচেয়ে বেশি নদীকেন্দ্রিক জীবন চিত্রিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—কাজী আবদুল ওদুদের ‘নদীবক্ষে’ (১৯১৯); মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ (১৯৩৬); তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কালিন্দী’ (১৯৪০); হুমায়ূন কবিরের ‘নদী ও নারী’ (১৯৪৫); বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ইছামতী’ (১৯৫০) কাজী আফসার উদিদন আহমদের ‘চর-ভাঙা চর’ (১৯৫১); অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৯৫৬); অমরেন্দ্র ঘোষের ‘চর কাশেম’ (১৯৫৬); সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’ (১৯৫৭); অমিয়ভূষণ মজুমদারের ‘গড় শ্রীখণ্ড’ (১৯৫৭); কমল কুমার মজুমদারের ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ (১৯৬২); সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ (১৯৬৮); সত্যেন সেনের ‘এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে’ (১৯৭১); সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘গহীন গাঙ’ (১৯৮০); আবু ইসহাকের ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’ (১৯৮৬); দেবেশ রায়ের ‘তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্ত’ (১৯৮৮)। এছাড়া ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেনের ‘পোকামাকড়ের ঘরবসতি’ (১৯৮৬) উপন্যাসে নদী, জল ও জীবন পরস্পরের রঙে মিশে একাকার হয়েছে। রাহুল সাংকৃত্যায়নের ‘ভলগা থেকে গঙ্গা’ অনেকের বিবেচনায় উপন্যাসোপম মহাগ্রন্থ। এতে বর্ণিত হয়েছে একটি ভূখণ্ডের সভ্যতা গড়ে ওঠার বিশদ বর্ণনা।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসে রয়েছে জেলেজীবনের অসামান্য অভিব্যক্তি। লেখক নদীতীরবর্তী গ্রাম্য নিম্নবর্গ জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ক্রমশ বিলুপ্ত প্রায় ‘মালো’ সমপ্রদায়ের জীবনচিত্রণ মূলত নদীকেন্দ্রিক। লেখক ধীবর সমাজের জীবনসংগ্রামের সাধারণ কাহিনিকে দিয়েছেন অবিনশ্বর ও অসাধারণ রূপাবয়ব। উপন্যাসটির ভূমিকাংশে তিনি লিখেছেন, ‘তিতাস একটি নদীর নাম। তার কূলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস। স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়। ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙ্গে, দিনের সূর্য তাকে তাতায়; রাতে চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়া ঘুম পাড়াইতে বসে, কিন্তু পারে না।’ তিতাস নদী ও তার দু’কূলের মানুষের জীবনযাত্রাকে ঘিরে রচিত ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য একটি রচনা।
এছাড়া বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ইছামতী’ নদীপাড়ের জীবনকেন্দ্রিক একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য। এখানে তত্কালীন সময়ের নদী আর নদীপাড়ের জীবন একাকার। তবে ‘গঙ্গা’র আখ্যান যাদের জীবন নিয়ে নির্মিত, তা ফাঁকফোকরহীন। এত নিখুঁত, নিটোল আর জলের সঙ্গে মানুষের এমন গভীর সংগ্রাম অন্যকোনো নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসে দেখা যায় না। এখানে জলের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম, মধুর প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিত্র পাওয়া যায় যা অন্য কোনো নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসে এমনি করে উপস্থাপন করা হয়নি। তিতাসকে অবলম্বন করেও মানুষ হিসেবে হয়তো বেঁচে ওঠা যায় অন্তত তার প্রমাণ এই উপন্যাস। কিন্তু সেই কল্পবীজ এ উপন্যাসে শাখায়িত হতে পারেনি। হোসেন মিয়া ময়নামতীর দ্বীপে পদ্মার প্রতিস্পর্ধী এক জনবসতি গড়ে তুলতে চেয়েছে, কিন্তু তার সে প্রয়াসও রহস্যময় থেকে গিয়েছে। কিন্তু গঙ্গার বুকে মালো পরিবারের মাছমারা ছেলে সমুদ্রের স্বপ্ন এমনভাবে লালন করেছে মনের মধ্যে, প্রতিহত করা যায়নি তাকে। গঙ্গাকে এভাবে পেরিয়ে যেতে পারে বলেই গঙ্গা এই জাতীয় উপন্যাসগুলির মধ্যে স্বতন্ত্র। ‘গঙ্গা’তে রয়েছে নদী-জীবনের রূঢ় বাস্তবতার নিখুঁত রূপময়তা। ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ ও ‘গঙ্গা’র পটভূমি এক হলেও চরিত্র-চিত্রণ, ভাষা, কথোপকথন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা মোটকথা সবকিছু উপস্থাপনার গুণে উপন্যাস দুটির অবস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে যোজন যোজন দূরে। গঙ্গা উপন্যাসের সার্থকতা এখানেই। কারণ ‘গঙ্গা চলে দুর্বোধ্য হেসে, কুলুকুলু করে।’ এখানে জেলেদের কান্না যেন কান্না নয়, উপোসী চিলের চিত্কার। এই উপন্যাসে সমরেশ বসু আমাদেরও জেলেপাড়ার বাসিন্দা করে তুলেছেন। জেলেপাড়ার ভাষা, বিশেষ শব্দ, এমনকি উচ্চারণেও বিরক্তি নেই আমাদের। পুরো উপন্যাস রচিত হয়েছে মূলত এক মৌসুমের মাছমারার ঘটনা প্রবাহ নিয়ে। যদিও এর আগের মৌসুমের কথা আছে ভিন্নভাবে, যে-মৌসুমে নিবারণ সাইদর মরেছিল সমুদ্রে। তারপরেও গঙ্গার ঘটনা, কাহিনি, চরিত্র সব মিলিয়ে এর ব্যাপকতা অনেক বেশি। জাল, জল আর জেলে নিয়ে এ কাহিনি অনন্য।
কেবল পদ্মা-গঙ্গা-ইছামতী নয়, বাংলা সাহিত্যে হুগলি-অজয়-ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ-নদীর প্রভাব রয়েছে। অজয় নদ ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের একটি বন্যাসঙ্কুল নদী যা গঙ্গার অন্যতম প্রধান শাখা ভাগীরথী হুগলির উপনদী। কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও আরো অনেক কবি অজয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন :
‘বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অজয় নদীর বাঁকে,/ জল যেখানে সোহাগ ভরে স্থলকে ঘিরে রাখে।’ ‘অজয়ের ভাঙনেতে করে বাড়ি ভঙ্গ,/ তবু নিতি নিতি হেরি নব নব রঙ্গ।’ হুগলি নদী বা ভাগীরথী-হুগলি পশ্চিমবঙ্গে নদীর একটি শাখানদী। পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে প্রবাহিত এই নদীটির দৈর্ঘ্য প্রায় ২৬০ কিলোমিটার। মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা বাঁধ থেকে একটি খালের আকারে নদীটি উত্সারিত হয়েছে। বাংলার প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ও লেখমালায় সর্বত্রই ভাগীরথীকে গঙ্গা বলা হয়েছে। ‘পবনদূত’ গ্রন্থে ত্রিবেণী-সঙ্গমের ভাগীরথীকেই বলা হয়েছে গঙ্গা। লক্ষণসেনের গোবিন্দপুর পট্টোলীতে বেতড়ে পূর্ববাহিনী নদীটি জাহ্নবী নামে অভিহিত। বল্লালসেনের নৈহাটি লিপিতে ভাগীরথীকে ‘সুরসরিত্’ অর্থাত্ স্বর্গীয় নদী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেও ভাগীরথীর উদার প্রশস্তি করা হয়েছে। পদ্মাপুরাণ, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, এমনকি মুসলমান কবিদের রচনাতেও গঙ্গার স্তুতি দেখা যায়। ১৪৯৪ সালে রচিত বিপ্রদাস পিপলাই-এর মনসামঙ্গল কাব্যে অজয় নদ থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ভাগীরথী-হুগলির প্রবাহপথের এক মনোজ্ঞ বর্ণনা পাওয়া যায়, যার সঙ্গে ১৬৬০ সালে দেওয়া ফান ডেন ব্রোকের তথ্যের বেশ মিল লক্ষিত হয়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সুজন-সখী’র ‘সব সখীরে পার করিতে নেব আনা আনা, তোমার বেলা নেব সখী’—প্রেমের গানটি ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’-এ বর্ণিত যমুনা তীরের রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অর্থাত্ সংগীতজগতে ‘নদী’ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে ঠাঁই পেয়েছে। মান্নাদে’র ‘এ নদী এমন নদী’; জগজিত্ সিংয়ের ‘নদীতে তুফান এলে বুক ভেঙ্গে যায়’ কিংবা আরতী মুখোপাধ্যায়ের ‘নদীর যেমন ঝরনা আছে, ঝরনারও নদী আছে’ ইত্যাদি অমর সংগীত হিসেবে টিকে থাকবে। এছাড়াও, ‘মোহনায় এসে নদী পিছনের পথটা কি ভুলতে পারে’—গানটিও জনপ্রিয়।
মূলত শিল্প-সাহিত্যে নদীময়তার কথা বলে শেষ করতে হলে দীর্ঘ পরিসর দরকার। কারণ মানবজীবন ও তার সভ্যতার বয়স যেমন হাজার বছরের তেমনি নদীর সঙ্গে সাহিত্যের যোগাযোগও দীর্ঘদিনের। তবে এখনো নদীকেন্দ্রিক সাহিত্য রচিত হচ্ছে। নিম্নবর্গের জেলে সম্প্রদায় থেকে শিক্ষিত হয়ে সেই জনগোষ্ঠীর কথাও কেউ কেউ লিখছেন। যেমন—হরিশঙ্কর জলদাস। তাঁর ‘জলপুত্র’ একটি বাস্তব জীবনের নদী ও সমুদ্রকেন্দ্রিক জীবনের আখ্যান। আশা করা যায় এপথে অনেকেই এগিয়ে আসবেন অদূর ভবিষ্যতে।
নোট: লেখাটি দৈনিক ইত্তেফাক থেকে নেয়া হয়েছে।