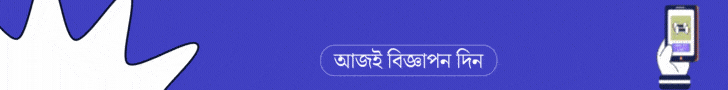কোন্ নদীর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল, কোন্ নদী ছিল আমার প্রথম প্রেমিকা? আমি খুঁজি, স্মৃতি হাতড়ে ফিরি, বিভ্রম তৈরি হয়, একবার যদি বুড়িগঙ্গার শেষ বিকেলের জল চলকে উঠে তো, আরেকবার চিরিক মেরে উঠে দুপুরের ঝলমলানো তুরাগ। বুড়িগঙ্গা আমার নানাবাড়ির আর তুরাগ দাদাবাড়ির। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই এতোবার নানাবাড়ি আর দাদাবাড়ি করেছি যে, আমি আসলে প্রথম কাকে দেখেছিলাম, তুরাগ না বুড়িগঙ্গাকে, সাব্যস্ত করা সত্যি কঠিন হয়ে উঠে। শেষে দ্বারস্থ হই মায়ের, মা চোখ বন্ধ করে বলে দেন, বুড়িগঙ্গা!
হ্যাঁ, বুড়িগঙ্গাই হবে। মায়ের এভাবে গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলার কারণটা হলো, ঢাকা থেকে আমি নাকি প্রথম নানাবাড়ি গিয়েছিলাম। ঢাকা থেকে কেন, ঢাকাতেই যে আমার জন্ম হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের নভেম্বরে লালবাগের বিষ্ণুচরণ স্ট্রিটের এক ভাড়াবাড়িতে। ১৯৬৬ সাল থেকেই আমার নানা লন্ডন চলে যাওয়ার পর নানি তার সন্তানদের নিয়ে ঢাকাতেই থাকতেন-কখনো লালবাগ কখনো শাহজাহানপুর কখনো আবার কমলাপুর। আমার মায়ের বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও তিনিও থাকতেন ঢাকায় নানির সঙ্গে। নয় বছর পর নানা দেশে ফেরেন। তখন আবার ব্যাক টু দ্যা প্যাভিলিয়ন, নানারা চলে যান বুড়িগঙ্গার ওপার কেরানিগঞ্জের রাজাবাড়ি নিজেদের বাড়ি আর আমার মা আমাকেসমেত স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন তুরাগ পার্শ্ববর্তী গাজীপুরের জরুন গ্রামে।
তো, ওই যে ঢাকাতে বসবাসের সময়ই আমি, যখন খুব পিচ্চি, ঢাকা থেকে প্রথম গিয়েছিলাম নানাবাড়িতে! আর নানাবাড়ি যেতে হলে তো অনিবার্যভাবেই পেরোতে হয় বুড়িগঙ্গা। তখন তো আর বুড়িগঙ্গার বুকে তিন-তিনটি ব্রিজ ছিলো না, এতো হতশ্রী রূপও ছিলো না। কৃশকায়ও ছিলো না মোটেও। নদীর এপার থেকে ওপার প্রায় দেখাই যেতো না। ভরা টালমাটাল জলের টইটুম্বুর বুড়িগঙ্গা পার হতে হতো ছোট ছোট রিকশা নাওয়ে। কিছু নাও বড়ও ছিলো, সেসব ঘাটের পারানি। তখন ভটভটানি মেশিনওয়ালা নৌকার কথা কেউ কল্পনাও করেনি। ছলাৎ ছল ছল ছলাৎ বুড়িগঙ্গার জল নৌকায় এসে মাঝেমধ্যেই ভিজিয়ে দিতো। আমাকেও কি প্রথম দর্শনেই ভিজিয়ে দিয়েছিল? প্রথম দর্শনেই কি আমার প্রেমে পড়েছিল? তা নইলে ও কেন আমাকে এতো ডাকতো! এতো টানতো বারবার গভীরভাবে! পরে আমরা যখন নয় বছর ঢাকা কাটানোর পর স্থায়ীভাবে দাদাবাড়ি গাজীপুরের জরুন গ্রামে থিতু হই, তার পর থেকেও, এতোবার আমার নানাবাড়ি যেতাম যে, বুড়িগঙ্গার সঙ্গে বছরে কমসেকম তিনচার বার, আসা-যাওয়া মিলিয়ে অন্তত সাত-আটবার তো দেখা হতোই- কোনো কোনোবার তারও বেশি।
কতবার যে বেড়িয়েছি বুড়িগঙ্গার ওপর দিয়ে- কতভাবে কত ঋতুদিনে, বলে শেষ করা যাবে না। দাদাবাড়ি থেকে নানাবাড়ি আসা-যাওয়ার মাঝখানে পড়তো শহর ঢাকা। ফলে ঢাকার ক্রমবিকাশের ধারাটাও লক্ষ্যগোচর হয়েছে। কীভাবে বদলে গেল এর ল্যান্ডস্কেপ, কবে কোন মাঠটার মৃত্যু ঘটল, জলের কোন ধারা গেল থেমে, চেনা-অচেনা গাছগুলো হারিয়ে গেল কোথায়, নির্জন স্বচ্ছ সুন্দর পথ ফুটপাত ভরে উঠল অজস্র মানুষ- বুড়িগঙ্গা কীভাবে কীভাবে ধর্ষিতা হলো- সব যেন ধারাবাহিক এক দৃশ্যপট! অবশ্য পুরো ঢাকার নয়, যেটুকু আমার চোখের আয়তসীমার মধ্যে ছিল, যেতে-আসতে দৃশ্যমান হতো। জরুন গ্রাম থেকে কোনাবাড়ি বাসস্টেশন, কোনাবাড়ি থেকে ঢাকার গুলিস্তান-ফুলবাড়িয়া, সেখান থেকে সোয়ারিঘাট, সোয়ারিঘাট থেকে বুড়িগঙ্গা-জিনজিরা হয়ে রাজাবাড়ি- এই যাত্রাপথের দুধার, দুধার ছাপিয়ে হয়তো আরো দূর-দিগন্ত, যত দূর চোখ যায় সেই প্রান্তবর্তী সীমানা! তবে মুক্তিযুদ্ধের আগের কোনো স্মৃতিই মনে নেই, তখন আমার বয়স ছিল মাত্র তিন।
গুলিস্তান থেকে কখনো রিকশা কখনোবা বেবিতে সোয়ারিঘাট পৌঁছালেই দূর থেকে চিতল মাছের প্রসারিত পেটের মতো ভেসে উঠতো বুড়িগঙ্গা- স্ফুরিত, সবাক, প্রীতিময়, স্পন্দিত- দেখলেই মনে বয়ে যেত শীতল সুবাতাস। লাল-নীল কত রঙের পালতোলা নৌকা এদিক-ওদিক ছোটে চলেছে। যতো এগোই ভেসে উঠে জলের কল্লোল, কল্লোলতা ছাপিয়ে লঞ্চ-স্টিমার বা জাহাজের ভটভটানি। কুলিদের শোরগোল, মাঝিদের হাকাহাকি। জীবনের যেন একটা চলন্ত গতিচ্ছবি দোলা দিয়ে যেত!
বুড়িগঙ্গার পানি তখন ছিল টলটলা পরিষ্কার আর ভরা। নদীর মধ্যে নানান রঙের মাছরাঙার দেখা মিলতো। তবে ভয়ে থাকতাম, কখন না আবার বড় স্টিমার বা জাহাজ চলে আসে! তার ঢেউজল আছড়াতে আছড়াতে যে আমাদের ছোট্ট নৌকাটাকেও বেসামাল করে দেয়! ভয়ে গুটিসুটি মেরে বসে থাকতাম। সময়টা যদি হতো উন্নার। তাহলে এই বুড়িগঙ্গা-পর্বটা অল্পই হতো, ওপারের জিনজিরার কোনো ঘাটলায় নেমে চারআনা কি আটানা অক্টো ঘাটলায় দিয়ে শুরু হতো আমাদের হাঁটা। তারপরের যাত্রাটা ছিল দুর্বিষহ। কত গ্রাম কত দীঘল পথ যে হাঁটতে হতো আমাদের। জিনজিরা থেকে মনু ব্যাপারীর ঢাল হয়ে বাঁকা চরাইল, মুক্তিরবাগ, করদিঘির পার, কাঠুরিয়া, কাজিরগাঁও, ধীতপুর, নামারহাঁটি হয়ে তবেই রাজাবাড়ি! প্রায় সাত-আট মাইলের সুদীর্ঘ এক পথ।

তবে বর্ষা হলে কথা নেই, প্রলম্বিত হতো আমাদের বুড়িগঙ্গা-পর্ব। পানিতে পানিতে সয়লাব বর্ষায় সোয়ারিঘাটেই মিলে যেত রাজাবাড়ির নাও। শশ সারিবাঁধা নৌকা থেকে মাঝিরা পাল্লা দিয়ে শুরু করতো ডাকাডাকি। এর ভেতরেই রাজাবাড়ির নৌকাকে ভালোভাবে শনাক্ত করা যেতো। মাকে দেখেই এগিয়ে আসতো গ্রামের চেনা কোনো মাঝি। ব্যাগট্যাগ নিজের হাতে নিয়ে নৌকায় রাখতো। এরই ফাঁকে আব্বা আামাদেরকে নৌকায় বসিয়ে রেখে মাংস-পরোটা নিয়ে আসতেন। অতুলনীয় স্বাদের সেই পরোটা-মাংস খেতে খেতে পৌঁছে যেতাম মাঝনদী। তারপর সারিবাঁধা নৌকার ভিড় থেকে এ-নৌকাকে ঠেলে ও-নৌকাকে ধাক্কিয়ে, কারো মাথা অন্য নৌকার গলুইয়ে লাগলো কিনা গা বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসতো খোলা নদীতে। সেখানে এসেই মাঝি যেন নতুন করে একটা দম নিতো। তারপর সজোরে চালাতে শুরু করতো বৈঠা। কখনো কখনো অল্পবয়সী সাগরেদ সামনের গলুইয়ে বসে উল্টো দিক থেকে বৈঠা বাইতো। আমরাও যেন নতুন আনন্দে উজ্জীবিত হতাম। জলে বেজে উঠতো ছলাৎ ছলছল ছলাৎ ছলছল এক নেশা ধরানো শব্দ। দুলতে দুলতে নৌকা মাঝনদীর দিকে এগোতো। ধীরে ধীরে চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যেত হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরি, সোয়ারিঘাট, শহরের সব কোলাহল চিৎকার আর নৌকার দঙ্গল।
কখনো ফাগ-মাখানো রোদ কখনো বা মেঘের ছায়ায় ছায়ায় নৌকাটা কোনাকোনি ছুটে যেতো তিরতির করে। মাঝির উদ্দেশ্য নদীর ও-পারের দিকে থাকা। সেটা যে ভালো হতো আজ বেশ উপলব্ধি করি, যতই ওপারের দিকে এগোতো নৌকা সৌম্য নীরবতার বুক ফুঁড়ে বেজে উঠতো পাখির কলকাকলির মূর্ছনা। একসময় ঢাকার বিল্ডিংগুলো হয়ে উঠতো সব চৌকোনা বাক্স। একটার ওপর আরেকটা বাক্স ঠাসাঠাসি করে রাখা। তারপর সেই বাক্সগুলোও একসময় দৃশ্যপট থেকে ক্রমশ অন্তর্হিত হতো। নৌকাটা তখন ঢুকে পড়েছে অফুরান সবুজের এক রাজ্যে! ডানে-বাঁয়ে যেদিকেই তাকাও গাছগাছালি, তারই মাঝে টলটলে বুড়িগঙ্গার জল, মাছরাঙার ওড়াওড়ি। তবে হঠাৎ হঠাৎই চিরে যেত এই সৌম্যতা। কোথা থেকে সিনেমার ভিলেনের মতো বিকট শব্দ তুলে হাজির হতো বড় কোনো স্টিমার বা লঞ্চ। আর সবকিছুকে চাপা দিতে দিতে এক সময় ওটা মিলিয়ে যেতো আমাদের সামনে থেকে। শুধু কি শব্দ! সেই স্টিমারের ঢেউয়ের ধাক্কায় আমাদের ছোট্ট নৌকাটাও আলোড়িত হতো- প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠতো, নাচতো কাঁপতো, এমনকি ডুবে যাওয়ার ভয়ও দেখাতো।
বুড়িগঙ্গার সঙ্গে এইসব নানান খুনসুটি শেষে একসময় আমাদের ছোট নৌকাটা বরিসুর দিয়ে ঢুকে যেত সরু খালে। খাল তো নয়, যেন এক সুড়ঙ্গপথ। দুপাশে ঘিঞ্জি ঘনবসতি। লতাগুল্মের জঙ্গল। জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে-মধ্যে টংয়ের পায়খানা। জঙ্গলে তেলাকুচা পেকে লাল হয়ে আছে। গণ্ডায় গণ্ডায় পিটকেল ভাসছে পানিতে। মাঝে-মধ্যেই কাঠের সাঁকো মাথার ওপর। সে-সাঁকোয় দাঁড়িয়ে গল্প করছে পাড়ার ছেলেরা। তবে দৃশ্যপটে আছে বৈচিত্র্যেরও বাহার। কোথাও বা লতাগুল্মের বদলে খালের কিনার ঘেঁষে এলোমেলো মাথা নুয়ে শুয়ে আছে আখগাছ। আখের পাতার ধার এসে শরীরেও লাগতো। কী যে নৈঃশব্দের এক অপূর্ব গান বাজতো তখন। বৈঠার একঘেয়ে শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। মাঝে-মধ্যে কোথা থেকে ভেসে আসতো কাকের ক্লান্ত স্বর।
কোথাও বা দুই বাড়ির দুই জোয়ান বউ কী একটা ব্যাপার নিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। আচ্ছা, কী নিয়ে হাসাহাসি করছিল ওরা? কোথাও বা এক স্কুল-বালিকা ক্লাস ফেলে খালপাড়ে বিষণ্না আনমনা। এইভাবে কত দৃশ্যপট ছাড়িয়ে সুড়ঙ্গ টাইপের খালটা একসময় আমাদেরকে একটা অশত্থ গাছের কাছে ছেড়ে দিত। তারপরই নৌকাটা সামান্য বাঁক নিয়ে একটা ব্রিজের নিচ দিয়ে হঠাৎই উপস্থিত হতো অসীম এক আকাশতলে, যেখানে ডানে বামে সামনে পেছনে কোনো ঘরবাড়ি নেই লোকালয় নেই। দিগন্তের পর দিগন্ত শুধু জলঢাকা খোলা প্রান্তর। সেই প্রান্তরের মাঝে পানির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে ওঠা আমন ধানক্ষেত সবুজতা শুধু বিলিয়েই চলেছে। আর মাথার ওপর শুধু আকাশ আর আকাশ আর সুদূরের আহ্বান আর অসীমের ব্যপ্তি! অনেকদূরে দিগন্ত-রেখায় গ্রামগুলো কখনো গাঢ় কখনো বা ধুসর সবুজ, কখনো বা একেবারেই ঝাপসা। আমন ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে নারীর চুলের সিঁথির মতো চলে গেছে যে সরু পথ, সেখান দিয়েই নৌকা তির তির করে এগিয়ে যেতো অবশক্লান্ত গান শুনিয়ে।
কোথা থেকে যে আসতো বর্ষার এত পানি! সেই সোয়ারিঘাট থেকে দু-পাড় উপচেপড়া বুড়িগঙ্গার পানির মধ্য দিয়ে শুরু হতো আমাদের যাত্রা। চারপাঁচ ঘণ্টা ধরে এই বিপুল অসীম স্রােতবাহী পানিপথেই যেতে হতো নানাবাড়ি! পুরো পথটিই সমুদ্রের মতো পানির অসীম পুঞ্জ ধারণ করে রাখতো। পরে জেনেছি, আমাদের নানাবাড়ি ছিল পদ্মাবিধৌত অঞ্চল। পদ্মা-উপচানো পানি এসে পুরো বিক্রমপুর, কেরানিগঞ্জ ওদিকে মানিকগঞ্জের বিস্তীর্ণ নিম্নাঞ্চল প্লাবিত করে দিত।
গাজীপুরে আমাদের দাদাবাড়ির নামায়ও বর্ষার পানি আসতো। কোপাকান্দির বিল ভরে গিয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত তুরাগ নদের সঙ্গে। তবে ঘরের পাশে গাবতলা বা একটু দূরের কদমতলা- কোথায়ও নৌকা থাকতো না। গ্রামের মানুষের কারোর নৌকায় চলাফেরার চল ছিল না, দরকারই হতো না নৌকার। সবাই টানে থাকতেই পছন্দ করত। সেজন্যই বুঝি আমার দাদাবাড়ির মানুষকে নানাবাড়ির লোকজন ঠাট্টা করে বলতো টেঙ্গুইরা। আর, আমার দাদাবাড়ির লোকজনও ছাড়তো না, নানাবাড়ির লোকজনকে সম্বোধন করতো ভউরা বলে। যা হোক, নৌকা যে একেবারে থাকতো না, তাও নয়। নৌকা থাকতো জেলেপাড়ায়, কোপাকান্দি বিলের ওপার। বর্ষায় সেই জেলেপাড়ারই এক-দুটা নৌকা পারাপারের জন্য কদমতলায় বাঁধা থাকতো। সে-নৌকায় না ছিল ছই না ছিল বসার মতো পাটাতন। কীভাবে থাকবে, সেসব নাও ব্যবহার হতো শুধু মাছ মারার কাজে। ছইঅলা প্যাসেঞ্জার-নৌকা ভাড়া করে আনতে হতো কাশিমপুর বাজার থেকে। কাশিমপুর আর কড্ডার মধ্যে তখন নিয়মিত তুরাগ নদীতে ভাড়া নৌকার চল ছিল। বাজার-সওদা করার ব্যাপার তো ছিলই, কাশিমপুর অঞ্চলের মানুষ ঢাকাসহ গাজীপুর যাওয়ার জন্য ব্যবহার করতো তুরাগের এই নৌপথ।
বর্ষা সিজনে এ-নদীকে অবলম্বন করেই অনেকের রোজগারের পথ খুলে যেতো। বর্ষার পানি টইটুম্বুর হলেই ছোট ছোট ছইঅলা নৌকা নিয়ে কদমতলায় হাজির হতো বেদের দল। তারা কেউ দেখাতো সাপের খেলা, কেউ ম্যাজিক, কেউ বা আবার মন্ত্র ঝেড়ে শরীর থেকে বদরস বের করে সারাতো বাতবেদনা, ফেলতো দাঁতের পোকা! আমরা সাপের খেলাটা নিয়মিত দেখতাম, ম্যাজিকও মিস করতাম না। এখনো কানে বাজে কোনো কোনো বেদেনির মন্ত্র, এক দুই তিন, চলে যা ময়মনসিং! মাটির জিনিসপত্রের সম্ভার নিয়ে হাজির হতো কুমারবাড়ির মানুষ। যাদের আখড়া ছিল কাশিমপুর। তুরাগ নদী থেকে এটেল মাটি উঠিয়ে এরা কাশিমপুর বাজারে ঢোকার মাথায়ই একটা বেশ বড় জায়গায় নিজেদের অনেক অনেকগুলো কারখানা গড়েছিল। বংশ-পরম্পরায় তারা চালাতো এ-ব্যবসা।
কাশিমপুর বাজার ছিল বর্ণাঢ্যে ভরা। তুরাগ নদের গায়ে গা লাগানো এই বাজারের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং গড়ন সত্যিই মনোমুগ্ধকর। মনে হবে যেন তুরাগ নদেরই একটা পার্ট এ-বাজার। তুরাগের উঁচু পাড়, বিশাল এক ঘাটলা, তার মাথায় কালীমন্দির, পরে অবশ্য একটা মসজিদও স্থাপিত হয়েছে মন্দির থেকে সামান্য দূরে, জায়গায় জায়গায় অশত্থ গাছ, তার পরেই এই কুমোরপাড়া, একটু দূরেই বল খেলার বিশাল মাঠ, স্কুল, শানবাঁধানো ঘাটের পুকুর, জমিদারবাড়ি, বিশাল বিএডিসি (বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন)- সব মিলিয়ে বেশ জাঁকজমকপূর্ণ আবহ।
এই কাশিমপুর বাজার থেকে শুধু কড্ডাতেই প্যাসেঞ্জার নৌকা যেতো না, আরো বিস্তৃত ছিল নেটওয়ার্ক। মালপত্র আনা-নেওয়ার জন্য ছিল গয়নার নৌকা। সেই গয়নার নৌকা দূর-দূরান্তের নানা প্রান্তে পৌঁছে দিতো প্রয়োজনীয় পণ্যসম্ভার। প্রতি মঙ্গলবার কাশিমপুর বাজার থেকে মাল ভরে একদিন একরাত লাগিয়ে পৌঁছাত ঢাকা। আবার ঢাকা থেকে একই সময় লাগিয়ে ফিরে আসতো কাশিমপুর। আব্বা সেই গয়নার নৌকায় নানাবাড়ির জন্য পাঠাতেন আম-কাঁঠাল, লটকান, চম্পাফল। নানাবাড়ির অঞ্চলে কাঁঠাল, লটকান, চম্পাফল এসব ছিলো দুর্লভ। শিল্পায়নের ফলে আজ দাদাবাড়ির অঞ্চলেও সেসব ফলফলাদি তেমন চোখে পড়ে না। তবে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে কাঁঠাল আর লটকানের অস্তিত্ব ঠিকই মেলে। শুধু চম্পাফলই যা বিলুপ্তির শিকার। অথচ চম্পাফল ছিল কাঁঠালের চেয়েও স্মার্ট আর সুস্বাদু। এর কোয়াগুলো কাঁঠালের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট একটু লালচে আর স্বাদটার মধ্যে প্রাধান্য টকের। মিষ্টি স্বাদের মধ্যে টকের আধিক্য থাকায় স্বাদটা দারুণ চপলা-উচ্ছলা মনে হতো। গয়নার নৌকায় পাঠানো এসব ফল ঢাকা থেকে আবার অন্য এক গয়নার নৌকায় রাজাবাড়ি আমার নানাবাড়িতে পৌঁছাত। তখন আমাদের নানাবাড়ি দাদাবাড়ি কোনো অঞ্চলেই ট্রাক বা অন্য কোনো পণ্য-পরিবহন ভেসেলের অস্তিত্ব ছিল না। নৌকাতেই আনা-নেওয়া হতো সব ভারী জিনিসপত্র। বর্ষাকালে নামায় গেলেই চোখে পড়তো মাল পারাপারের দৃশ্য। তুরাগ নদ আর কোপাকান্দি বিল-পারে ইট, খড়ি আর আম-কাঁঠালের স্তূপ হরহামেশাই দেখা যেতো।
বর্ষায় আমাদের নানাবাড়ি যাওয়ার সময় হলেই আব্বা কাশিমপুর থেকে মানুষ দিয়ে নৌকা রিজার্ভ করে আনাতেন। অধিকাংশ সময়ই নৌকা এনে দিতেন উকিলভাই। আব্বার স্কুলের পিয়ন। এখনো চেহারাটা চোখের সামনে ভাসে। ডান চোখের নিচের দিকে বড় একটা আঁচিল ছিল, চুল সবসময়ই খাড়া হয়ে থাকতো মানুষটার। সাইকেল চালাতেন। বাড়িতে যারা রাখাল খাটতেন, তাদের ওপরও পড়তো মাঝে-মধ্যে এ-দায়িত্ব। ছইঅলা নৌকাটি আমাদের জন্য অপেক্ষা করতো গাবতলায়।
আহা রে কোথায় হারিয়ে গেল সেই গাবতলা! ঘন ছায়াভরা সুশীতল সেই গাবতলা! আর কি কখনো তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে? মাথা খুঁড়ে মরলেও ফিরে পাওয়া অসম্ভব! ডিজিটাল যুগ তারে গলা চেপে মেরে দিয়েছে! কী আশ্চর্য যে এক রমণীয় পরিবেশ তৈরি করে রেখেছিল গাবতলা তার চারদিক থেকে। পেছনে জঙ্গল, সামনে সুবিস্তৃত নিম্নভূমির চরাচর। সেই চরাচরের আরো ঢালুতে ছিল কোপাকান্দির বিল। সে বিল দুদিক থেকে- একদিকে কদমতলা আর অন্যদিকে কাশিমপুর বাজারমুখী হয়ে তুরাগের সঙ্গে মিশে যেতে উন্মুখ থাকতো। ভরা বর্ষায় তার সেই সাধ পেতো ঢলো ঢলো পূর্ণতা। তুরাগের সঙ্গে মিলেমিশে তখন একাকার হয়ে যেতো বিল। কিন্তু বর্ষা বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে আবারো তাকে ফিরে যেতে হতো নিজের হতশ্রী শুকনো চিমসে চিপসানো রূপে। শুধু কদমতলাজুড়েই যা একটু তা তা থই থই করতো পানি! জলের সেই টইটুম্বুর আঁধারটুকুর জন্যই পাড়ার ছেলেমেয়েদের ঢল নামতো কদমতলায়। তা সত্ত্বেও গাবতলার কদর সামান্যও কমতো না।
যতদূর চোখ যায় পানি আর পানি। পানির ওপারে ছোট্ট দ্বীপের মতো ভেসে থাকতো জেলেপাড়া। জেলেপাড়ার বাইরের খোলা মাঠ আর প্রান্তর জুড়ে ছিল লম্বা লম্বা সব তালগাছের সারি। দিগন্তের কিনারে দাঁড়ানো সে-তালবৃক্ষের সারি জীবন্ত পেইন্টিং হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো যেন। বর্ষা মিলিয়ে গেলে পানির বদলে জায়গাটা ধান আর বাদামগাছের উপচানো সবুজে ভরে উঠতো।
গাবতলা থেকে আমাদের নিয়ে ছইঅলা নৌকাটি যখন কোপাকান্দির বিল ছাড়িয়ে জেলেপাড়ার পাশ ঘেঁষে তুরাগে পড়তো, অমনি দেখো শুশুকের দল শুরু করে দিতো ডুব ডুব খেলা। অতলান্ত জল থেকে লাফিয়ে উঠে নিজেকে এক ঝলক দেখিয়েই আবার কোথায় হারিয়ে যেত শুশুকটা। বর্ষার নদী নিম্নাঞ্চলের সঙ্গে মিলেমিশে বিশালাকার যেন সমুদ্রের রূপ ধারণ করতো। তা সত্ত্বেও মাঝি নদী দিয়েই চালাতো নৌকা। কোথায় আবার কোন চরায় গিয়ে ঠেকে!
আমাদের এই তুরাগ নদ ছিল চিতল মাছের জন্য বিখ্যাত। বড় বড় সব চিতল পাওয়া যেত উন্নায়! বড় বড় আইড়-বোয়ালও মিলতো বেশ। আরো কত বিচিত্র মাছ যে ছিল! ফেউয়া বলে একটা মাছ ছিল শুধুই ভাজা খাওয়ার জন্য। বাচা মাছ, শিলং মাছ, পোয়া মাছ, কাজলী মাছ, পাবদা- প্রতিটি মাছই স্বাদে-গুণে চেহারায় আলাদা স্বতন্ত্র! গলদা চিংড়ি, পুঁটি-ট্যাংরাতো ছিলই। আরো অনেক মাছই ছিল, নাম মনে করতে পারছি না, চেহারাও ঝাপসা হয়ে গেছে। এভাবেই চিরকালের মতো হয়তো বিস্মৃত হয়ে যাবে কোনো কোনো মাছ। আমাদের নানা গল্প করে বেড়াতেন তুরাগ নদের মাছের আলাদা একটা স্বাদ আছে।
তুরাগ নদ, নদ ছাড়িয়ে বামদিকের আদিগন্ত জলমগ্ন প্রান্তর, ডান পাড়ের কালাকুরসহ গ্রামের দৃশ্যাবলি দেখতে দেখতে কখন যে পৌঁছে যেতাম কড্ডা, বলতে পারব না। মুক্তিযুদ্ধের সময় কড্ডার ব্রিজটা পাকিস্তানিবাহিনীর আগ্রাসন ঠেকাতে মুক্তিযোদ্ধারা উড়িয়ে দিয়েছিল। স্বাধীনতার পর দুতিন বছরের মধ্যেই সে-ব্রিজ অবশ্য পুনর্নির্মাণ করা হয়। ব্রিজ হওয়ার আগ-পর্যন্ত সময়ে চলাচল করতে হতো ফেরিতে।
জরুন গ্রাম থেকে কদমতলা দিয়ে কোপাকান্দির বিল পেরিয়ে তুরাগপার ধরে হেঁটে যেতে যেতে প্রকৃতির নানা পরিবেশের দেখা মিলতো। তুরাগে তো বাহারি নৌকার ছড়াছড়ি ছিলই, মাছমারার দৃশ্য, ওপারে কালাকুর গ্রামের লাজুক বউদের অবেলার গোসল, সবই ছিল কাজল-মায়ার লতায় জড়ানো। সূর্যের ক্রমশ হেলে পড়ার প্রেক্ষাপটে কোপাকান্দির বিল, বিলের পানি, তুরাগের পানি, তুরাগের পার, পারের ওপারের বাড়িগুলো তৈরি করতো মায়াবি সব দৃশ্যপট।
আমি এখনো আমাদের নামার কোপাকান্দি বিল-সংলগ্ন হিজল গাছগুলোর কথা ভুলতে পারি না, হিজল ফুলগুলো এখনো প্রায়ই আমার মনের ওপর অভিঘাত তৈরি করে যায়! ঘন সবুজ পাতার গাবগাছটার গভীর ছায়াতলের ছায়া পেতে মন এখনো উন্মুখ হয়ে থাকে। এই হিজল গাছটা কি নদী না থাকলে হতো ওখানে, হতো?
তুরাগ আর বুড়িগঙ্গার পাশাপাশি আরেকটা নদীর কথা না বললেই নয়। আমাদের নানাবাড়ি থেকে ধলেশ্বরী নদী দেখা যেতো না ঠিক, তবে ধলেশ্বরী নদীতে ছুটে যাওয়া নৌকার পালগুলো চোখে পড়তো। যতোবারই নানাবাড়ি যেতাম গভীর অবাক হয়ে দেখতাম কত বড় বড় যে পাল উড়তো, নানা রঙের! সেসব ছুটে যাওয়া পাল দেখে মনে হতো ধলেশ্বরী নদীতে যেন জীবনের উৎসব লেগেছে! আমি একদিন আমার এক পিঠাপিঠি মামা অরুণকে ধরেছিলাম, চলো যাই নৌকার পালগুলো দেখে আসি। অরুণ আমাকে নিতে পারেনি সেদিন। তবে নিয়েছিল এক জোছনাগলা হালকা হালকা শীত-রাতে। জোছনার আলোছায়ায় কখনো সোজা পথ দিয়ে কখনো বা গ্রামের কোনো বাড়ির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা একসময় পৌঁছে গিয়েছিলাম ধলেশ্বরী নদীপাড়ে। পুরো নদী জোছনায় সাদা হয়ে ছিল। নৌকার পালগুলো রাতে রং হারালেও জোছনা ধারণ করে কী এক অপার্থিব মায়া ছড়িয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছিল দূর থেকে দূরে।
হামিদ কায়সার : কথাসাহিত্যিক।
আরও পড়তে পারেন….
হালদা নদীকে বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণা: যৌক্তিকতা ও বিশ্লেষণ
জলকাটার শব্দ শুনি ।। সত্যজিৎ রায় মজুমদার
শঙ্খ নদ : দ্যা রিগ্রাই খিয়াং ।। মুহাম্মদ মনির হোসেন
এই মৃত নদী আমার তিস্তা না ।। শুভময় পাল