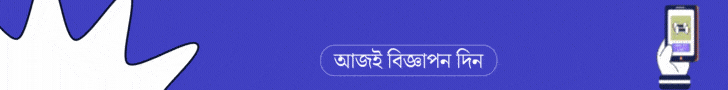ছেলেবেলা থেকেই নদী ও প্রকৃতির সাথে আমার জীবন জড়িয়ে আছে আষ্টেপৃষ্ঠে। নদী ও প্রকৃতির শান্ত-সৌম্য-স্নিগ্ধ রূপ মাধুর্য দেখে যেমন মুগ্ধ ও বিমোহিত হয়েছি তেমনি এর রুদ্র রূপ, ঝঞ্জা-বিক্ষুব্দ ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা দেখে হয়েছি অস্থির, কখনোবা বেদনায় নীল। প্রবল ঢেউ ও ঝরো হাওয়ায় কখনো বা বিপন্নবোধ করেছি মেঘনা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও যমুনার মাঝনদীতে। উত্তাল ঝড়ো হাওয়ায় ডুবে মরার হাত থেকেও দু’একবার প্রাণে বেঁচে ফিরেছি!
আমার বেড়ে ওঠা খাল-বিল-নদী-নালা বিধৌত গ্রামীণ জনপদে। আশৈশব বিচরণ করেছি অনাবিল ও স্নিগ্ধ প্রকৃতির মাঝে। নানা ধরনের দেশীয় নৌকা, লঞ্চ, স্পীডবোট, স্টীমারসহ নানান ধরনের জলযানে চড়ে নদীপথে ভ্রমণ করেছি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, মাইলের পর মাইল। কখনো মনের আনন্দে, কখনো খেয়ালের বশে আবার কখনোবা কারো ভ্রমণসঙ্গী হয়ে দিনভর অবিরাম ঘুরে বেড়িয়েছি এক গন্তব্য থেকে অন্য গন্তব্যে। কাজের সূত্রেও দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়েছি নদীপথে। দেশের প্রধান নদ-নদী, উপনদী, শাখা-প্রশাখায় ভ্রমণ অভিজ্ঞতা এই জীবনে এক বিশালপ্রাপ্তি। এসব ভ্রমণে অনাবিল আনন্দ-সুখ যেমন অনুভব করেছি তেমনি মগ্ন হয়ে দেখেছি নদী ও জীবনের বহুমাত্রিক রূপ।
অনাদিকাল থেকেই এই দেশের বুক চিড়ে নিরন্তর বয়ে চলেছে অসংখ্য নদী। বৈচিত্র্যেভরা অনন্য এক পলিমাটির দেশে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা শাখা-প্রশাখা প্রতিনিয়ত পলি বহন করে সৃষ্টি করে চলেছে অপরূপ এই ভূখণ্ডটিকে। এসব নদী দেশকে করেছে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা। তাই বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। নদীর সাথে গ্রামবাংলার মানুষের রয়েছে নাড়ীর টান। নদীর রূপমাধুর্য নিয়ে লেখা গান, কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস আর সাহিত্যকর্ম আমাদের সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ।
শৈশবে দেখার সেই মুগ্ধতা, পরিণত বয়সে দেখা নদী ও প্রকৃতি নিয়ে কিছু স্মৃতি সহভাগ করার বাসনা থেকেই বক্ষ্যমান লেখা। দূরবীন দিয়ে দেখার মতো দূর অতীতে দৃষ্টিপাত করে নদী আর প্রকৃতির সাথে কীভাবে নিবিড় সখ্য গড়ে উঠেছিল তারই কিছু স্মৃতি তুলে ধরা এই লেখায়। নদী আর শ্যামল প্রকৃতির অনিন্দ্য রূপ মাধুর্য দেখে কেটেছে আমার কিশোরবেলার বড় একটা সময়। তাই তো ভাবি, নদী নিয়ে যে কতো রাশি রাশি স্মৃতির ঝাঁপি, তা স্বল্প পরিসরে কতটুকু তুলে ধরা যাবে? এমন সন্দিগ্ধ মন নিয়েই তাকিয়ে দেখছি পেছনে ফেলা আসা দূর অতীতে।
নদী ও বাংলাদেশ একই সূতোয় গাঁথা দুটি নাম। এ দেশের মাটি এবং মানুষের জীবন ও জীবিকার সাথে নদী জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদী। ছোট বড় অনেক উপনদী এসে এসব নদীতে মিশেছে। এসব নদ-নদী বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে করেছে মহিমান্বিত। অনেকেই বলেন, নদীই বাংলাদেশের প্রাণ যদিও বা নদী ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে এর অস্তিত্ব। পানির অভাবে আজ অনেক নদী মৃতপ্রায়। মারাত্মক দূষণের শিকার অনেক নদী। নদী রক্ষায় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে বিপন্ন ও হারিয়ে যাওয়া মৃতপ্রায় নদীগুলোকে উদ্ধার করা হয়তো সম্ভব। কথায় বলে, নদী বাঁচলে বাঁচবে দেশ, বাঁচবে দেশের মানুষ। কথাটি মোটেই অতিশয়োক্তি নয়।
এদেশের মানুষের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে নদীর রয়েছে ব্যাপক অবদান। নদীপথে কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য পরিবহনে খরচ কম হওয়ায় নদী তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে বড় বড় শিল্প কারখানা। মৎস্য সম্পদেও দেশ সমৃদ্ধশালী। ইলিশ, পাঙাশ, রুই, কাতলা, বোয়াল, পাবদাসহ বিভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়া যায় যা খাদ্য ও পুষ্টির অনন্ত উৎস। বলাবাহুল্য মিঠা পানিতে উৎপাদিত মাছ খুবই সুস্বাদু।
আমাদের মুক্তিযুদ্ধেও ছোট-বড় সব নদীর ছিলো এক বিরাট ভূমিকা। নদীপথে মাইলের পর মাইল পাড়ি দিয়ে হাজারো মানুষ ও দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা এক প্রান্ত থেকে পাড়ি জমিয়েছে অন্য প্রান্তে। বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ নদীপথে অস্ত্র গোলাবারুদ ও অন্যান্য রসদ নিয়ে পরাস্ত করেছে পাকবাহিনীকে। শত্রুসেনাদের হাতে ভারী অস্ত্র-শস্র থাকা সত্ত্বেও সম্মুখসমরে তারা টিকে থাকতে পারেনি।
একেবারে শৈশবের দিনগুলোতে নদীপথে বহুবার সফরসঙ্গী হয়েছি আমার দাদির সাথে যাকে আমি ডাকতাম ‘দাদু’ বলে। নৌকায় চেপে দীর্ঘ নদীভ্রমণ করে তিনি বার কয়েক গিয়েছেন তাঁর নিজের ভিটায়, আমার দাদাবাড়ি। সেই যাত্রায় আমিও থাকতাম তাঁর সাথে। আবার কখনো লঞ্চে চড়ে লতা নদী ও ছোট বড় শাখা নদী পাড়ি দিয়ে প্রথমে যেতাম কীর্তনখোলার পাড়ের বরিশাল নউ বন্দরে। কখনো বরিশালে ২/৩ দিন বেড়িয়ে আবার কখনো বা বন্দরে স্বল্পকালীন যাত্রাবিরতি শেষে বিকেলের ছোট লঞ্চে চেপে কালিজিরা, সুগন্ধা, গাবখান, সন্ধ্যা নদী হয়ে পৌছুতাম কচা নদীর তীরের কাউখালী বন্দর। লঞ্চ থেকে নেমে আবার নৌকায় চেপে দাসেরকাঠি – আমাদের গ্রাম। এককথায় বলা চলে দিনব্যাপী নদীভ্রমণ। আমার পিতার সাথেও লঞ্চে চড়ে নদীপথে ভ্রমণ করেছি অনেকবার।
ছইওয়ালা একমালাই নৌকায় চেপে গেলে দীর্ঘ নদীপথ পাড়ি দিতে অনেক বেশি সময় লেগে যেতো। অতি প্রত্যুষে রওনা করে সন্ধ্যার খানিক পরে পৌঁছে যেতাম দাদু’র বাবার বাড়ি – স্বরূপকাঠি থানার অদূরে আকলম গ্রামে। হঠাৎ করেই যখন সেখানে উপস্থিত হতাম, কাজি বাড়ির মেয়ের আগমনে সেখানে তৈরি হতো আনন্দঘন মুহুর্ত! ২/৩ দিন বেড়ানোর পর নৌকা ছেড়ে যেত মূল গন্তব্য দাদাবাড়ির উদ্দেশে। সকালে রওয়ানা করে দুপুরের খাবার খেতাম দাদুর ছোটো বোনের বাড়ি সেহাঙ্গল গ্রামে। সেকালে তো আর ফোন ছিল না! তাই মেঝো বোনকে আকস্মিকভাবে কাছে পেয়ে ছোটো বোনের যে কী আনন্দ! চোখের পাতা ভিজে ঝরে আনন্দাশ্রু! স্বল্পকালীন যাত্রাবিরতি শেষে একদিন পরেই বিদায়ের পালা। একমালাই নৌকাখানি আবার ছুটে চলে। কচা নদী পাড়ি দিয়ে প্রথমে কাউখালী বন্দর তারপরে আঁকাবাকা খাল পেরিয়ে দুপুরের আগেই পৌঁছে যাই আমাদের বাড়ি। এভাবে দীর্ঘ নদীপথে নৌকা বেয়ে মাঝি হয়ে পড়ে খুব ক্লান্ত। তাঁর যে তখন বিশ্রামের প্রয়োজন!
এভাবেই দিনেরাতে নৌকায় চড়ে দেখেছি দেশের দক্ষিণাঞ্চলের এক অংশের গতিপথ, প্রকৃতির নানা রূপ ও রঙ, নানা অনুষঙ্গ। নদীর ঢেউ গুণে গুণে আর দাদু’র মুখে গল্প শুনে শুনে কখনো শুয়ে কখনো বা বসে থেকে বিভিন্ন এলাকা অতিক্রমের সময় যে জলছবি দেখেছি, তা ছিল এককথায় অনন্য! সেই ভোরে মুলাদি বন্দর পেড়িয়ে আড়িয়াল খাঁ’র শাখা নদী আর ছোট বড় নদী বন্দর (শিকারপুর, টরকি, বানারীপাড়া, স্বরূপকাঠি, জলাবাড়ি ইত্যাদি) পার হতে গিয়ে দেখেছি নদীপথে নানা বরণের নৌকার চলাচল, নানা ধরনের মটর লঞ্চ, মাছ ধরার বিচিত্র সব নৌকা। দেখেছি মাছধরার নানা আয়োজন। আরও দেখেছি নদী পাড়ের মানুষের বাড়িঘর, গেরস্তের প্রাত্যহিক জীবনধারা। দেখেছি ফসলের ক্ষেত, কৃষক-ক্ষেতমজুরের ধানকাটা বা ফসল তোলার দৃশ্য। ফসলের সোদা গন্ধ আজও ঘ্রাণ ছড়ায় যেন। মুগ্ধ হয়ে দেখেছি দিগন্ত বিস্তৃত খোলা আকাশে মেঘেদের ওরাওড়ি। স্বরূপকাঠির নদী পেরোনোর সময় নৌকার উপর বসা ‘হাট’ যেখানে কেনা-বেচা হতো নানাজাতের গাছের চারা, সুস্বাদু পেয়ারা, আমড়াসহ পাকা ও টাটকা ফলফলাদি। ছোটো ছোটো ডিঙি নৌকায় বসা পসরা ও বিচিত্র ‘নৌকার হাট’ দেখার অভিজ্ঞতা মনে হলে আজও অন্যরকম অনুভূতির জন্ম হয়।
এভাবেই একমনে কৌতূহলের ছলে দেখেছি আবহমান বাংলার নদ-নদীর চিরায়ত রূপ, লোকজ সংস্কৃতি ও নদীপাড়ের মানুষের জীবনধারা। দেখেছি বিচিত্রসব লতাগুল্ম, জলজ শ্যাওলা, ঘাটফুল, হোগলাফুল, নারিকেল ও সুপারিসহ নানা ধরনের গাছপালা। নদীর দু’কূলের বাড়ি-ঘর, ফসল তোলার দৃশ্য, নদীর স্বচ্ছ জলে দলবেঁধে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের সাঁতার কাটা বা ডুবডুব খেলার দৃশ্য, উঁচু গাছ কিংবা নদীর কূল থেকে নদীতে ঝাপিয়ে পড়া, কলস কাখে উদাস মনে ঘোমটা মুখে কূলবধূদের সলজ্জ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকার চিরন্তন দৃশ্য! জেলেদের মাছ মারার নানা আয়োজন, সৌখিন মাছ শিকারীদের ভেলজাল বা লম্বা ছিপি নিয়ে বরশী হাতে ছেলে বুড়োদের মাছ ধরার চমৎকার সব আয়োজন। গাঙের জলে ছোট বড় দেখতে মনোহর নানাজাতের পাখিদের উড়াউড়ি। ফুরুত ফুরুত উড়াল দিয়ে পানির ধারায় মিশে গায়ে বা ডানায় পানি মেখে দূরে হারিয়ে যাওয়ার অপার দৃশ্য আজও মনে দোলা দেয়।অপার্থিব এক শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয় মনে।
হঠাৎই চোখে পড়তো বরযাত্রী বহন করা নৌকার বহর। মাইক বাজিয়ে একযোগে ছুটে চলেছে বিচিত্র রঙ ও সাজে সাজানো দুই বা ততোধিক নৌকা। উচ্চস্বরে বাজানো জনপ্রিয় ভাওয়াইয়া, পল্লীগীতি কিংবা সেকালের সিনেমার জনপ্রিয় গানের তালে তালে বিয়ের পসরা সাজিয়ে নববধূ নিয়ে যাওয়ার সে দৃশ্য খানিকের জন্যে হলেও নদী পাড়ের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। এসব দেখে আমার মনের মাঝেও সৃষ্টি হতো এক আনন্দময় মধুর অনুভূতি।
নদীপথে প্রথম দীর্ঘ ভ্রমণটি শুরুর কালে আমার বয়স ছিলো খুব কম- সম্ভবত ৮ বা ৯ বছর। ঠিক ধলপহরে ফজরের আজানের সুর ভেসে ওঠার কিছু আগে চোখ ঘষতে ঘষতে হ্যারিকেনের লালচে ম্লান আলোতে হেটে চলেছি। সামান্য পথ, কিন্তু তা-ও হেটে যেতে কেন জানি খুবই অনীহা! তাই তো হাঁকডাকের মধ্যে ঘুম ভেঙে অগত্যা আর কি করা! আব্বার হাত ধরে দাদু’র সাথে একটু খানি হেটে (কাউরিয়া) বন্দরের ঘাটে বাধা নৌকায় চড়ে বসেছি। যেতে হবে বহুদূরে। নৌকার ছই বরাবর পরদা টানিয়ে আড়াল করা হলো। ওঠার মুহুর্তে নৌকাখানি একটু হেলেদুলে উঠলো। আব্বা বিদায় জানালে নৌকাখানি ছেড়ে দেওয়া হলো। দীর্ঘদেহী ও লম্বা গড়নের শশ্রুমন্ডিত মাঝি লম্বা বাশের লগি ঠেলে খালের মাঝে এসে আস্তে করে সামলে নিয়ে বৈঠা হাতে অভিজ্ঞ হাতের কুশলতায় নৌকাটিকে পুরোপুরি বাগে নিয়ে এলেন। একটুআধটু হেলেদুলে মাঝি এগিয়ে চলেছেন। আবছা আলোয় আর হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় মাঝির মুখ আর দেখা যায় না। মাঝেমধ্যে মুখে আল্লাহ’র নাম। নৌকার মাঝখানের পাটাতনের বিছানায় আমি ততক্ষণে শুয়ে পড়েছি। আঁকাবাঁকা খালের পথে কিছুদূর এগোতেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টেরই পাইনি! ঘুম যখন ভাঙলো, চোখ খুলে দেখি ভোরের নরম ও কোমল আলো পানির উপর ঠিকরে পড়ে চিকচিক করছে। চমৎকার আভা! অতি প্রত্যুষের হালকা মৃদুমন্দ বাতাসে শরীর ও মনে অন্যরকম ভালো লাগার অনুভূতি সৃষ্টি হলো। নদীর গভীরে ছোট ছোট ঢেউ। নৌকাখানি তাই চলছে একটু হেলেদুলে। সবমিলিয়ে নদীর মাঝখানে তৈরি হয়েছে এক নান্দনিক ও মনোমুগ্ধকর আবহ!
ছোট ছোট ঢেউ কেটে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে একমালাই নৌকাখানি এগিয়ে চলেছে। শুয়ে শুয়ে আমি উপভোগ করছি সেই মৃদু নাগরদোলা! একপাশে কাত হয়ে দেখছি গাঙ্গেয় পাখিদের আনাগোনা। খুব ধীর লয়ে ছোট ছোট পাখি ফুরুত করে নদীর জলে গা ভিজিয়ে মুহুর্তেই উধাও। আবার দেখি সাদা বক আর গাঙচিল। এসব পাখিদের আনাগোনা শৈশবের সেই মনে কি দোলা দিয়ে গিয়েছিল? আজ আর শত চেষ্টা করেও তা মনে করা গেল না।
মনে পড়ছে, অন্য একদিনের দাদাবাড়ি যাওয়ার ঘটনা। আমাদের নৌকাখানি মুলাদির নন্দীরবাজার জাহাজ ঘাট পার হয়ে আড়িয়াল খাঁ’র শাখা নদী হয়ে বড় নদী পাড়ি দিতেই শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি, সঙ্গে দমকা হাওয়া। তাকিয়ে দেখি নদীর দু’কূল ছাপিয়ে ঝরছে অবিরাম বারিধারা। নদীর গতি-প্রকৃতিও দ্রুত বদলে যেতে লাগলো। তীরহারা ওই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেয়ার মতো অবস্থা আমাদের। মাঝির শরীর ভিজে টইটম্বুর। ভেতরে বসা আমাদের দু’জনের অবস্থাও নাজুক। নদী এবার ফুসে উঠতে শুরু করেছে। ঢেউয়ের উচ্চতা বাড়তে শুরু করেছে নাটকীয় গতিতে। নৌকার উপর আছড়ে পড়ছে বড়ো বড়ো ঢেউ, আমরা আর এগোতে পারছি না। মাঝনদীর আকস্মিক ঝড়ে নাগরদোলায় নৌকাখানি যেন উল্টে যাওয়ার উপক্রম। এমন বেহাল অবস্থা দেখে দাদুর চোখে মুখে বিষম উৎকন্ঠা! বিপদের আশংকা দেখলেই দাদু উচ্চস্বরে রা তেলওয়াত করতেন! উপায়ন্তর না দেখে মাঝি মরিয়া হয়ে উঠলো কূলের সন্ধানে। শেষমেষ আশ্রয় নিতে হলো ঘন ঝাউবন পরিবেষ্টিত ছোট্ট এক বাজারে। চললো দীর্ঘ যাত্রাবিরতি। বৃষ্টির গতি কমে এলে আমরা আবার ছুটে চললাম গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।
দুই কূলে বৃষ্টিমুখর ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন চর। মাঝি একমনে বেয়ে চলেছে। ঢেউয়ের দোলায় দুলে দুলে একই ছন্দে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। মাঝে মধ্যে মাঝি পাটাতনের নীচে জমে থাকা পানি সেচে ফেলে আবার বৈঠা হাতে বেয়ে চলছে। এভাবেই কিশোর চোখ নিবিষ্ট মনে নৌকার ফাঁক দিয়ে নদীর এ-কূল ও-কূল চেয়ে দেখছে ভাবলেশহীন চোখে। সে দেখায় প্রকৃতি আর বাংলার আবহমান চিরায়ত রূপও ধরা পড়ছে। এভাবেই কিশোর চোখে নদী দেখা, নদীপথে ভ্রমণের সূত্রপাত।
আমার জন্ম হয়েছিল আশি হিজরীর প্রবল এক বৃষ্টিমুখর ঝরো রাতে, বরিশালের হিজলা উপজেলার এক নিভৃত গ্রামে, আমার নানাবাড়িতে। শ্যামল ছায়া আচ্ছাদিত পূর্ব ডাইয়া নামীয় গ্রামের এক মৌলভী পরিবারে। আমার নানা থাকতেন তাঁর নানার বাড়ি, যেটি ছিল তাঁর দাদাবাড়ি থেকে ২ মাইল দূরে। আমার জন্মস্থান সেই নানাবাড়ি মেঘনার অতল গহবরে নিমজ্জিত। আমার প্রিয় নানীর কবরটিও ওই নদীতেই বিলীন!
মনে পড়ছে, নানাবাড়ির চারদিকে ঘন সবুজের বেষ্টনী, নানাজাতের ছোটো বড়ো গাছগাছালি, সারি সারি জারুল-পারুল-হিজল, বন্য ফুলের গন্ধে ভরপুর সেই অনিন্দ্য সুন্দর গ্রামীণ প্রকৃতি জনপদ এখন কেবলই স্বপ্নের মতো, ঝাপসা ও অস্পষ্ট। পাখিদের কলরব শুনে মনোজগতে তৈরি হতো এক অন্যরকম আনন্দময় আবহ। সকালের ঘুম ভাঙে পাখির ডাকে। সন্ধ্যা হয় পাখিদের কূজনে। বাড়িটার এক অংশের ঘন জংগল ছিল পাখিদের অভয়ারণ্য! সেখান থেকে ভেসে আসতো পাখিদের কলরব, কিচিরমিচির ও বিচিত্র শব্দ। সন্ধ্যা নামতেই ডানা ঝাপটে পাখিসব করে রব, ছুটে চলে আপন আপন গন্তব্যে। সন্ধ্যা নামতেই মাগরিবের আজানের ধ্বনি ভেসে আসে। বাড়ির অন্দরমহলে সারি বেধে প্রার্থনায় সমপিত নারী ও পুরুষ। তাঁরা আমার মা, নানা নানি, খালা ও তাঁদের আত্মীয় পরিজন। রক্তের সম্পর্কে যূথবদ্ধ। কোথায় হারিয়ে গেলেন তাঁরা! কোথায় হারালো সেই নানা রঙের দিনগুলি। ভেবে পাই না। অথচ ওখানেই কেটেছে আমার শৈশবের আনন্দময় সময়।
ছেলেবেলায় আমার বড় খালার মেজো ছেলে (মোশারফ হোসেন, ডাকনাম ফিরোজ) ফিরোজ ও আমি একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি। শৈশবের একটা বড় সময় আমাদের কেটেছে নানাবাড়িতে। আমার নানী যাকে ডাকতাম নানু বলে, তিনি আমাদের আদর-যত্নে, ভালবাসায়, তাঁর স্নেহময় পরশে সবসময় ভুলিয়ে রাখতেন। ঘুম থেকে উঠে মজার মজার খাওয়া শেষ করে এক দঙ্গল শিশু কিশোর (খালাতো ভাই-বোনরা) বেরিয়ে পড়তাম বাড়ির আঙিনায়, মেতে উঠতাম অনাবিল আনন্দে। এভাবেই একসঙ্গে খেলে, বাড়ির চারদিকে ঘুরেফিরে আমাদের সেই দিনগুলো কেটেছে। আমরা খেলতাম উঠানে, বড় পুকুর পাড়ে, বাড়ির বাইরের কাচারি বা মক্তবের কাছে। আবার কখনোবা লুকোচুরি খেলতাম গাছ-গাছালি ও ঝোপঝাড়ের আড়ালে। নানা রঙ ও বর্ণের পাখির আনাগোনা দেখে বা পাখির বাসা ও ছোট্ট পাখির ছানা খুঁজে অনেক সময় কাটাতাম। বিভিন্ন মৌসুমে বিশেষত জৈষ্ঠ্যমাসে নানা স্বাদের মৌসুমী দেশী ফলের সমারোহ ও গন্ধ পুরো বাড়িটায় অন্যরকম আবহ তৈরি করতো।
প্রথম দেখা মেঘনা নদীর স্মৃতি আজও ভুলিনি। আমার নানাবাড়ি থেকে মেঘনার দূরত্ব তখন আনুমানিক ৩/৪ মাইল দূরে হবে। আমার বড় খালাম্মা’র বাড়ি থেকে তেমন একটা দূরে নয়। খালাম্মা’র শ্বশুর খুব নামকরা ব্যবসায়ী। স্থানীয় বাজারে বড় পরিসরে পাটের গুদাম ও ব্যবসা রয়েছে তাঁর। তিনি এককথায় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। সবাই এক নামে চেনে। কেউ কেউ সমীহও করে। একদিন আমরা দলেবলে বেড়াতে গেলাম বড় খালাম্মা’র বাড়ি, চর মেমানিয়া গ্রামে। খালাম্মা’র বাড়ি পৌছে দেখি তাঁদের বাড়িটা বেশ বড়সড়। নানাবাড়ি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বিশাল আকারের কয়েকটি টিনের ঘর, সারিবাঁধা। অনেক বড় বাড়ির আঙিনা। লম্বালম্বি উঠানটি বেশ প্রশস্ত। খালাম্মা’র ঘরে ঢুকে মনে হলো, তাঁরা খুব ধনী গেরস্ত। সন্ধ্যা রাতে উঠোনে জোস্নার আলোয় সবাই হৈ-হুল্লোড় করে কাটালাম। পরের দিন সকালে দূরে চোখ যেতেই আবিষ্কার করলাম, নতুন এক ধরনের নৌকা – ‘শুলুক’।
‘শুলুক’ নামটি শুনে মনে হলো, এ আবার কেমন নৌকা! আমার দৌড় তো কেবল ছইওয়ালা একমালাই, দেশী কোষা বা ডিঙ্গি নৌকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমরা ক’জন কিশোর দলবেঁধে নদীর কাছে বাধা বেশ কয়েকটি শুলুক দেখতে গেলাম। শুনলাম শুলুকের ভেতরের গভীরে অনেক মালামাল পরিবহন করা হয়। সাধারণ নৌকা থেকে আদলে ও গড়নে সম্পূর্ণ আলাদা। মালামাল না থাকায় শুলুকগুলোর পেটের ভেতরের গভীর খোড়ল (অংশ) দেখে চক্ষু চড়কগাছ! এই নৌকায় করে লবন বা অন্য জাতীয় পণ্য পরিবহন করা হয়। একেকটি নৌকায় লবন ভরে যখন গন্তব্যে যাত্রা করে তখন বাহির থেকে বোঝাই যায় না এতো পণ্য নিয়ে শুলুক নৌকা ছুটে চলে দূর দিগন্তে। নদীর পারে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। অসংখ্য নৌকা ভেসে চলেছে রং-বেরঙের পাল তুলে। সম্ভবত সেবারই প্রথম দেখলাম গুণ টানা নৌকা। নৌকার উপর মাঝি বড়ো বৈঠা বা পাঙখা হাতে, বাতাসের গতি দেখে বড় কাপড়ের পাল উড়িয়ে ২/৩ জন মাঝি-মাল্লার গলুইয়ের উপর বা ছইয়ের উপর, আর নদীর পাড় দিয়ে ৩/৪ জন মাল্লার কাধের উপর মোটা শক্ত রশি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নৌকাখানি। এসব মাল্লারা কোরাসের সুর তুলে গান গেয়ে এগিয়ে চলেছে সারিবদ্ধ হয়ে। এভাবেই বড়ো মাঝারি ও ছোটো ছোটো অসংখ্য নৌকা পণ্য নিয়ে ভেসে যাচ্ছে দূরের কোনো গঞ্জে বা বন্দরে। খুব কাছ থেকে বা দূর থেকে এইসব দৃশ্য দেখে মন চলে যায় দূরে, বহুদূরে। সেযাত্রায় নৌকার পাশাপাশি কিছু তেলবাহী বিশেষ জাহাজ বা ট্যাংকারও চোখে পড়েছিল। ওগুলো দেখে কী যে ভালো লেগেছিল! সেইসব স্মৃতি স্মরণে এলে এখনো মনে পড়ে অমর সেই গানের পঙতিমালা: “মাঝি বাইয়া যাও রে। অকুল দরিয়ার মাঝে, আমার ভাঙা নাও রে।”
মেঘনার পাড়ে গিয়ে সেবার দেখা হলো জেলেদের সাথে। রাতভর মাছ ধরে কূলে ফিরে এসেছে দলবেঁধে। আবার কেউবা বাড়ি থেকে ৩/৪ দিন আগে বেরিয়ে নদীর গভীর থেকে তাজা মাছ ধরে কূলে ফিরেছে গঞ্জে মাছ বেচার জন্যে। নদীর তীরে সারিবাঁধা জাল বিছিয়ে শুকাচ্ছে আবার কেউ কেউ অলস সময় কাটাচ্ছেন গল্প করে কিংবা গানের সুর তুলে। কেউ কেউ বুঝি জালে রিপুও করছিলেন। খানিকটা জায়গা নিয়ে যেন জালের পসরা বসে গেছে। কিছু নারীও বোধহয় যোগ দিয়েছেন নদী থেকে ফিরে আসা গৃহকর্তা অন্যকথায় বাড়ির পুরুষের সাহায্যের জন্য। নদীর পাড়ে জেলেদের জীবন – এ-এক ভিন্ন সংস্কৃতি! হিজলা থানার মেঘনা নদীর ঘাটে ঘাটে তখন দেখা মিলতো এইসব পেশাদার ও অপেশাদার জেলে সম্প্রদায়ের। এভাবেই আমার পরিচয় হয়েছিল মেঘনা নদীর সাথে।
ভাগ্যের কী পরিহাস, বড় নদী দেখার এতো শখ যা আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল মেঘনার পাড়ে! তার অল্প ক’বছরের ব্যবধানে দেখতে দেখতে আমার খালাবাড়ি’র সেই দূরের মেঘনা চলে এলো নানাবাড়ির খুব কাছে। বিত্ত বৈভবশালী বড়ো খালার বাড়িটি বিলীন হলো নদীর অতল গহ্বরে। আহা, কী সাজানো বাড়িই না ছিল! কী ছিল না তাঁদের! গোলাভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, ক্ষেতে উৎপাদিত ডাল, মরিচ, সরিষা ও তীল তেলের বীজসহ রবিশস্যের সেই বড় গোলা আর কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না! বাড়ির অদূরের গঞ্জে থাকা আমার খালুর বাবার পাট আর মরিচের আড়তও খালি হয়ে গেলো! আমার খালার পরিবারের ঠিকানা হলো নতুন বাড়িতে যেখান থেকে নদী যদিও অনেক দূরে।
হাজারো মানুষ অল্প ক’বছরের মধ্যেই হয়ে পড়লো বিপন্ন, নিঃস্ব। অবিশ্বাস্য! নদীর করাল গ্রাসে গ্রামগুলো বিলীন হতে থাকলো। ভিটেমাটি হারিয়ে দিশেহারা বিপুল জনগোষ্ঠী বাস্তুচ্যুত। এভাবেই ‘রাক্ষুসী’ মেঘনা ধ্বংস করে দিল মানুষের বসতি। আবার কী আশ্চর্য, কয়েক বছরের মধ্যেই অপর পাড়ে জেগে উঠলো এক বিশাল চর। কথায় বলে নদী এ-কূল ভাঙে, ও-কূল গড়ে, এই এক ভাঙা-গড়ার খেলা!
এবার আমার খালাতো ভাই ফিরোজরা চলে এলো আমাদের বাসার খুব কাছে। ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হলো আমার স্কুলে। আমরা একসঙ্গে একই ক্লাসে। কী মজা, ফিরোজ আর আমি একসঙ্গে আবার! মাত্র অল্প ক’দিন ক্লাস করতেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো। রাতারাতি বদলে গেল দৃশ্যপট।
আমাদের স্কুলের ক্লাস চলে, আবার চলেও না। এমন একদিন নানাবাড়ি গিয়ে ঘর থেকে দুই পা ফেলতেই দেখি সবুজের ফাঁকে একচিলতে সাদা ও নীল রঙের আকাশ উঁকি দিচ্ছে। কী কান্ড, আর একটু এগিয়ে পূর্ব দিকে তাকিয়ে অদূরেই দেখি বিপুল জলরাশি! শো শো শব্দে নদীর তুমুল গর্জন! এ কী করে সম্ভব! কিছুতেই মেলাতে পারি না। বুঝতে পারিনি, কোথায় হারালো আমার প্রিয় জনপদ, যেপথে আমরা কতো হেটে বেড়াতাম। ওইপথ ধরেই তো একদিন গিয়েছিলাম বড়ো খালাম্মা’র বাড়ির কাছের সেই মেঘনা পাড়ে। শৈশবের চেনা দৃশ্যপট কোথায় হারিয়ে গেল! মনটা ভেঙে চৌচির! আরও এগিয়ে যেতেই ভেসে এলো ঢেউয়ের প্রবল শব্দ। ধ্বংসের চিহ্ন চারদিকে। পাশের বাড়ির বুড়ী (‘দাই’) নানী, যে কিনা আমার নাড়ী কেটে দিয়েছিলেন অতি যত্নে। তিনিই তো আমার, আমাদের ভাইবোনের, খালাতো ভাইবোনের জন্ম-স্বাক্ষী। আমার, পৃথিবীর প্রথম কান্না তো তিনিই শুনেছিলেন? তাঁর বাড়ির এ কী ছন্নদশা! বুড়ী নানীরা গেলেনই বা কোথায়?
খানিক পরে মনে হয় সম্বিত ফিরে পেলাম। নদী ও নদী পাড়ের ধ্বংসযজ্ঞ দেখে একসময় নানাবাড়ি ফিরে এলাম। সারারাত নদীর পানির গড় খাওয়া আর তীর ভাঙনের শব্দ করুণ সুর হয়েই কেবল কানে বাজলো। পরদিন সকালে আবার নদীর দিকে যাত্রা করতেই দূর থেকে দেখতে পেলাম বড়সড় একটি জাহাজের সম্মুখভাগে তাক করা মেশিনগান। ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জাহাজ যাচ্ছে উত্তর দিক থেকে দক্ষিণে। অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে যাচ্ছে বোধহয়। উরদি পড়া ক’জন সৈন্য ‘টহল’ দিচ্ছে জাহাজের ভেতরে। এমন জাহাজ আগে কখনো দেখি নি। আশপাশের সবাই বলাবলি করছে যুদ্ধ জাহাজ (গানবোট) যাচ্ছে। ভয় ও অজানা এক শংকায় কিশোর মনেও কল্পনার ডালপালা গজিয়েছিল বোধহয়। মনে নেই পুরোটা, শুধু ভয় ও আশংকা যে মনে বাসা বেধেছিল তার কিঞ্চিৎ অনুভূতি মনে আছে।
মনে দুঃখ নিয়ে একাত্তরের আরও একদিন কী খেয়ালে যেন ফিরোজের সঙ্গে সহযাত্রী হলাম, আমাদের জন্মস্থান ‘মুন্সিবাড়ি’ দেখতে। হায়, এ কি! ছবির মতো সাজানো আমার নানাবাড়ি’র অস্তিত্বও প্রায় বিলীন! চারদিকে শুধু নদীর বিস্তৃতি। হালকা বৃষ্টিভেজা এক দুপুরে যখন নানাবাড়ির কাছে পৌছালাম, তখন আর হেটে যাওয়ার উপায় নেই। পরিচিত সেই পথটা ডুবে আছে। চিরচেনা পাশের বিলটিও জলমগ্ন। উত্তর পাশের দৃশ্য অচেনা, নদীর গর্জন আর আছড়ে পড়া ঢেউ। ফিরোজ একটি কলাগাছের ভেলা জোগাড় করলে তাতেই চড়ে আমরা কোনমতে পৌছলাম নানাবাড়ি। সেখানে যা দেখলাম, তা এককথায় ধ্বংসযজ্ঞ!
বলাবাহুল্য আমার নানা-নানী খালাদের নিয়ে আগেই উঠে গেছেন নানার পিতৃভিটায়। ‘পূর্ব ডাইয়া’ থেকে ‘পশ্চিম ডাইয়া’র বাড়িতে স্থানান্তর, যে বাড়িটি কি না ক্ষয়িষ্ণু এক সামন্ত পরিবারের ধংসাবশেষ। এ-বাড়িতে আছে শত বছরের ঐতিহ্য, বড়ো দীঘির শান বাধানো ঘাট, প্রাচীন ইটের বানানো কাচারি ঘর, মুঘলীয় স্থাপত্যে নির্মিত গম্বুজ মসজিদ, বড় বড় পুকুর, গাছ-গাছালি আরও কতো কী! মনে হলো, এ বাড়ির বাসিন্দারা একথা ভেবে অনেকটাই নির্ভর যে মেঘনা নদী এখনো বেশ দূরে! সহসা তাদের আক্রান্ত হওয়ার আশংকা নেই! কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর প্রকৃতি চলে তার নিজস্ব নিয়মে!
এদিকে আমার কিশোর মনে নানাবাড়ির সেই শান্তি নেই, আনন্দ নেই। নতুন পরিবেশে, নানাবাড়ি আর নেই! এই বাড়িকে আর নানাবাড়ি মনে হচ্ছে না। কেননা নানাবাড়ি মানেই মধুময় স্মৃতি, ঘুঘু ডাকা দুপুর, মায়াময় প্রকৃতি আর অনাবিল আনন্দ! এ-বাড়ির মানুষগুলো কেমন যেন। ভালো লাগে না! তাই আত্মীয়দের সঙ্গে আর সেই মায়ার বন্ধন তৈরি হলো না যেটা ছিলো মুন্সিবাড়িতে! মেঘনার টলটলে জলের ধারা আর রং-বেরঙের পাল তোলা নৌকাও আর কেন যেন টানে না!
এখন আর দীর্ঘসময় নিয়ে নানাবাড়ি বেড়ানো হয় না। আমার নানা মাঝেমধ্যে ধরে নিয়ে আসেন, মা’র সঙ্গেও যাই। এভাবেই আসা-যাওয়া চলছিল ক’বছর। এরই মধ্যে বরষায় একবার নানাবাড়ি গিয়ে শুনলাম, ধেয়ে আসছে ‘রাক্ষুসী’ মেঘনা! বড়ো দরজার সামনে খানিক এগিয়ে বুঝতে পারলাম, নদী আর খুব দূরে নেই। আধা মাইলেরও কম দূরত্বে নদী। বড় বড় ঢেউ আর গর্জন! প্রিয় মেঘনার এ কী রুদ্র রূপ!
এভাবেই কাছ থেকে কিশোর চোখ দেখেছে নদী, জীবন ও নদী ভাঙনের তীব্রতা। বেড়ে উঠতে উঠতে এই নদীর বিশালতা, সংকীর্ণতা, ধ্বংসলীলা, পলিমাটির যোগান দেয়া আর ভাঙা-গড়া দেখতে দেখতেই কিশোর একসময় যুবকে উত্তীর্ণ হলো। মেঘনার রূপালি ইলিশ, রাশি রাশি মাছের আড়ং দেখে, ইলিশীয় বিশেষ গন্ধ শুকে এক নব্য যুবক ১৯৭৮ সালের একদিন মেঘনার কালোজল পেরিয়ে রাতের অন্ধকারে চলছে ঢাকা অভিমুখে কলেজে ভর্তির উদ্দেশে।
কলেজে ভর্তির পর থেকে ঢাকায়ই বেশি থাকি। নানাবাড়ি খুব বেশি যাওয়া হয় না। তবে ছুটিতে গেলে থাকি কাউরিয়া, আমাদের বাসায়। ছুটিশেষ হলে নানাবাড়ির কাছের লঞ্চঘাট থেকেই লঞ্চে চড়ে ঢাকায় যাই। তখন নানা ও নানুর সাথে দেখা করতে যাই। তখন মা-ও নানাবাড়িতে। বিদায়ের সেই ক্ষণটি বড়োই বেদনার! হেটে যেতে যেতে যত দূর চোখ যায় মা পেছন থেকে চেয়ে থাকেন ছেলের দিকে। ছেলেও মাঝেমধ্যে একটু করে পেছনে তাকিয়ে দেখে মায়ের দিকে।
একটু একটু করে আমাদের অবচেতনেই মেঘনা এসে হাজির হলো নানাবাড়ির সদর দরজার সীমানায় যেখানে একটি বড়ো খাল আছে, খুব স্রোতস্বিনী। খালের মোহনায় নদী এসে খালের সাথে মিশেছে যাকে বলে গাটছাড়া বাধা। একদিকে ভাঙন কূল – বড় বড় বাড়িগুলো গিলে খেয়ে এখন এসে মিশেছে খালের সাথে। এই খালটি আর সহজে চেনা যায় না। বরষার জোয়ারে ফুলেফেঁপে উঠে এক ভয়ংকর খালে রূপ নিয়েছে। খালটির উপরে বাঁশের খিলানযুক্ত বড় একটা সাকো। এই সাকোর উপর উত্তরমুখী হয়ে বসলে দেখা যায় বিশাল আকাশের নীচে ভরা যৌবনবতী এক সমন্ত নদী। চাদের বুড়ী বুঝি ওই আকাশের উপরে বসেই জাবর কাটে!
জ্যোছনাপ্লাবিত রাতে নদীর রুদ্র রূপও এক অনিন্দ্য সুন্দর আবহ তৈরি করেছে। বড়োবড়ো ঢেউ আছড়ে পড়ার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ আর বিপুল জলরাশির গর্জনে মনের গভীরে ভয়ার্ত এক অনুভূতির সৃষ্টি হলেও কী এক অনিন্দ্য ও মোহনীয় সুরের আবেশ যেন তৈরি হয়! সুরের মূর্ছনায় উদাস করে বাউলের মন! তখন মনে হয়, এমন চাদের আলো মরি যদি সে-ও ভালো!
এমনই এক মায়াবী সন্ধ্যায় আমরা খালের সেই সাঁকোর সামনে কয়েকজন উঠতি যুবকের সাথে একত্রিত হলাম সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ জনা দশেক তরুণ যুবা। জোয়ারের টানে খালের দু’কূল ছাপিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে। আমাদের অদূরে নদী অশান্ত হলেও মোহন বাঁশির আকর্ষণে সবাই উদ্বেলিত। এরই মধ্যে এসে উপস্থিত আরাধ্য শিল্পী- তাজুভাই। তাঁর বাঁশির সুর ইন্দ্রজালিক মোহে আচ্ছন্ন করে।
একদিকে প্রলয়ংকরী মেঘনার গর্জন, অন্যদিকে প্রবহমান পানির উপর ঠিকরে পড়া জ্যোছনার মায়াবী আলো! দূরে দেখছি, প্রায় বিলীয়মান এক বিশাল অশ্বত্থের ছায়া, ডালপালা ছেটে দূরে ভাসে শুধু এর কাণ্ড। আঁকাবাঁকা শিকড়ের কিয়দংশ জোয়ারের পানিতে প্লাবিত। কাণ্ডের চিরিচিরি পাতার হালকা রেখা, পাশ দিয়ে প্রবহমান জলের ধারা যেখানে মেঘনা এসে মিলেছে স্রোতস্বিনী খালের জলে। সাঁকোর পশ্চিম পাড়ে তখনও কিছু বাড়িঘর তখনও ভাঙনের কূলে। বিপন্ন মানুষের ভাঙাচোরা সংসার। তখনও সন্ধ্যাবাতি পুরোপুরি নিভে যায়নি।
আমরা যে যার মতো সাঁকোর উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছি পা ঝুলিয়ে বসে আছি আসরে। ততক্ষণে তাজুভাইয়ের মোহন সুরে সবাই আত্মহারা। একটার পর একটা সুরের মোহজালে সবাই আপ্লুত। ভৈরবী রাগের সুরের মূর্ছনায় যেন চারদিক থমথমে। তাঁর বাঁশির সুর ইন্দ্রজালিক মোহে নদী পাড়ের সেই সুরের মূর্ছনায় আবিষ্ট হয়েছিলাম। সবকিছু মিলে আলো-আঁধারীর মাঝে তৈরি হয়েছে এক নান্দনিক আবহ!
ভাঙনমুখর মেঘনাপাড়ে সেই সন্ধ্যারাতের সেই মধুর স্মৃতি আজও হদয়তন্ত্রীতে গেঁথে আছে। সেই ইন্দ্রজালিক সুরের মূর্ছনা, মোহনীয় বাঁশির সুর! মনের গভীরে ভাসে মোহনীয় সুর,
ও নদীরে একটা কথা সুধাই শুধু তোমারে. .
কোথায় তোমার দেশ, তোমার নাইকি চলার শেষ।
আরও পড়তে পারেন….
চাঁদপুরের নদী, প্রকৃতি ও ইলিশ ।। সৌম্য সালেক
আনন্দাশ্রু ফুলেশ্বরী
আমার শৈশব নদী ।। হামিদ কায়সার